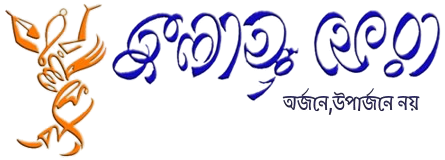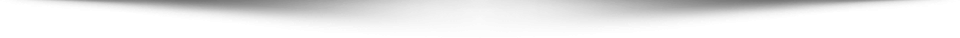বাংলা ভাষায় শিক্ষার সূচনাপর্ব এবং বিদ্যাসাগর
রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
(প্রথম ভাগ)
ত্রয়োদশ শতকে বাংলা মুসলমান সুলতানদের শাসনাধীন হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অবক্ষয় দেখা দেয়। এরপর ঔপনিবেশিক শাসকদের আমলে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ় করতে হলে স্থানীয় মানুষদের আয়ত্বে রাখতে হবে এবং তাদের মনোভাব বুঝতে হবে। এজন্য স্থানীয়দের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার জানা দরকার। এই উদ্দেশ্য তিনি যে সংস্কারমূলক কাজগুলি শুরু করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া। প্রশাসনিক কাজে সহায়তা ছাড়াও এর পিছনে একটি পরোক্ষ কারণ ছিল। খ্রিষ্টান মিশনারীরা বুঝেছিলেন দেশীয় মানুষদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হলে তাদের ভাষা ও ধর্ম
জানা আবশ্যক।
ইংল্যাণ্ড থেকে যেসব কর্মচারীরা প্রশাসনিক কাজের জন্য এদেশে এসেছিল তাদের দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাচ মিশনারী উইলিয়ম কেরী এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হয়েছিলেন। কেরী সাহেবের বাংলা ভাষার প্রতি টান আন্তরিক ছিল বলেই মনে হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ব্যকরণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন – “”The study of Bengali has been much neglected from idea that its use is very confined.” বেশ কয়েক বছর পর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণের সংস্করণে কেরী যা বলেছিলেন সেটা আন্তরিকতারই প্রমাণ – “The Bengali language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.”
উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর মুন্সী রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্যরচনার কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। এর ফলে ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ থেকে বাংলা ব্যাকরণ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বইও লেখা হয়। কেরী সাহেব তাঁর ব্যাকরণ পুস্তকে বাংলা বর্ণলিপি দিয়েছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে কেরী সাহেবের আগে যিনি এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন সেটিই বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। কাজের সুবিধার জন্য হ্যালহেডও বাংলা বর্ণমালার একটি রূপ মুদ্রিত করেছিলেন।
বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম ধাপ হল বর্ণমালা রচনা। উইলিয়ম কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশন ব্যতীত যাঁরা বর্ণমালা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি, রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী সভা। এর মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিশু সেবধি বর্ণমালা কিছুটা হলেও চলেছিল। তবে এগুলির কোনটিকেই তৎকালীন সরকার শিশুশিক্ষার উপযোগী বলে বিবেচনা করেন নি। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় তখন পাঠশালাগুলিতে শিক্ষণের একমাত্র বিষয় ছিল বর্ণমালার অক্ষর লেখা শেখানো ও তার সঙ্গে সামান্য কিছুটা অঙ্কের ধারণা দেওয়া। পাঠদানের কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিই তখন ছিল না।
ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন – “টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব ও মাদ্রাসায় সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি শিক্ষার মধ্যেই উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মমূলক বিষয় ছাড়াও সাহিত্যের সঙ্গে স্মৃতি ও ন্যায় বা আইন পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। কয়েকশো বছর আগে ধর্মীয় নীতি ও আচার যে রক্ষণশীল মনোভাবের ভিত্তিতে প্রচার করা হত, এখনও তাই চলিত ছিল; উনিশ শতকে তার বাস্তব মূল্য যেমন ছিল না, জ্ঞানার্জনের দিক থেকেও তেমনই অর্থহীন ছিল।” মোটের উপর সেই সময় শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ধর্ম ও সামাজিক আচার, বিভিন্ন নীতিমূলক লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী, কিছু নিয়ম ও আইন। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বা মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে এসবের বিশেষ কোনও গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে।
ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা বিরাজ করছিল উইলিয়ম অ্যাডাম তার বিবরণ দিয়েছেন। অ্যাডামের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণী অনুযায়ী তখন নারীশিক্ষার জন্য কোথাও কোনও বিদ্যালয় ছিল না। বস্তুত তখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল না, বরং সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল তার পরিপন্থী। অ্যাডাম তাঁর বিবরণীর উপসংহারে বলেছেন – “. . . . there was nothing in the system of instruction which could awaken and expand the mind of the young scholar and free it from the trammels of mere usage.”
বাংলায় তখনও ছাপা বইয়ের প্রচলন হয় নি। লিখিত গ্রন্থের অভাবে পাঠশালাগুলিতে মূলত শিক্ষকদের মুখ থেকে শুনে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় মনে রাখতে হত। সংস্কৃত টোলে স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র এবং মক্তব ও মাদ্রাসায় ধর্মগ্রন্থ প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বাংলা ছিল লোকের কথ্যভাষা, তাছাড়া বাংলা ভাষায় পদ্য লেখা বা গান বাঁধা হত। কিন্তু সে আমলে বাংলা গদ্যের প্রচলন একেবারেই ছিল না। সরকারী কাজকর্মে বা আদালতের কাজে ফারসি ভাষা ব্যবহৃত হত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা সংস্কৃতে চিঠিপত্র লিখতেন এবং কথাবার্তাতেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন।
সরকারী মহলে যেমন বাংলা ভাষার প্রাধান্য ছিল না, তেমনই বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজেও তা ছিল না। এদেশে কোন্ ভাষায় শিক্ষার প্রসার ঘটবে তা নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছে। কেউ প্রাচ্যের ভাষার (অর্থাৎ সংস্কৃত বা উর্দু) পক্ষে মত দিয়েছেন, আবার কেউ মনে করেছেন ইংরেজ শাসককুলের ভাষা ইংরেজি সেই স্থান নেবে। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গর্ভণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বনে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিতে বলেছিলেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এইচ এইচ উইলসনের মতে সংস্কৃত শব্দ ও ইংরেজি চিন্তার রূপ সমন্বিত করে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতিই ছিল প্রশস্ত। এইসব টানাপোড়েনের মাঝে শিক্ষার নীতি নির্ধারণে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় নি।
গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ – ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচ্যবাদী বনাম পাশ্চাত্যবাদীদের বিতর্কের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে বেন্টিঙ্ক তাঁর পরামর্শদাতা মেকলের অভিমত চেয়েছিলেন। আদ্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন মেকলে সাহেব কোন দেশীয় ভাষাকেই মর্যাদা দিতে চান নি। ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন – “poor and rude”। বেন্টিঙ্ককে তিনি প্রস্তাব দিলেন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতে অর্থের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হোক। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ তারিখে সরকারি রেজোলিউশনে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন – “. . . . all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.” বেন্টিঙ্কের নীতিতে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এশিয়াটিক সোসাইটির কাজের গতি শ্লথ হয়েছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার অবস্থা শোচনীয় হয়েছে।
সরকারী অফিসকাছারিতে এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসে ইংরেজীর প্রাধান্য ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এজন্য সরকারী সাহায্য ছাড়াই একের পর এক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভবানীপুরে এবং ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ও ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার শিক্ষাজগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারও অপ্রতিহত থাকে। কলকাতায় ডাফ স্কুল, চার্চ মিশনারী স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, হিন্দু ফ্রি স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ছাড়াও এই বিদ্যালয়গুলিতে বারোশো’র বেশী ছাত্র ইংরেজী পড়ত। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সরকারী শিক্ষানীতির কারণে সংস্কৃত কলেজের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়।
সরকারি শিক্ষানীতি ইংরেজির অনুকূল হওয়ায় কলকাতায় ২৫টি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সরকারী চাকরিতে লোক নিয়োগের জন্য যে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কেবলমাত্র ইংরেজি জানা লোকেরাই তার মাধ্যমে চাকরি পেতে পারত। তখন উচ্চপদে চাকরি করার একমাত্র শর্ত ছিল ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ল ঠিকই, কিন্তু দেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাংলা বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। বাংলা গদ্য তখনও সুসংবদ্ধ রূপ পায় নি, ফলে বাংলা পাঠ্যবই ছিল না। তাছাড়া বাংলায় ছাপাখানার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এটাও মনে রাখতে হবে জনশিক্ষায় বিদেশী সরকারও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্যে যে কেবলমাত্র মাতৃভাষাতেই শিক্ষার বিস্তার করা সম্ভব তা কেউ চিন্তা করে নি। এই অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক চব্বিশ বছর বয়সী যুবক বিদ্যাসাগর গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে বাংলা বিদ্যালয় খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা নিয়ে কেরী ও মার্শম্যানের রিপোর্ট তিনি যত্নসহকারে পড়েছিলেন। তাছাড়া সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা সম্পর্কে উইলিয়ম অ্যাডামের রিপোর্টও তিনি পড়েছিলেন। এছাড়াও হ্যারিংটন ও হোরেস উইসসনের শিক্ষানীতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
বাস্তব পরিস্তিতি বিবেচনা করে গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করতে প্রয়াসী হন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গ্রামাঞ্চলে ১০১টি বিদ্যালয় খুলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এক বছরের মধ্যেই এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই অভিজ্ঞতাই সেদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তরুণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করতে উৎসাহী করেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতে গিয়ে তিনি নিজেও বাংলা বইয়ের অভাব অনুভব করেছেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দেই টাকা ধার করে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রেস স্থাপন করার মধ্যে ছাত্রপাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই সক্রিয় ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শাল সাহেবের কাছ থেকেও এবিষয়ে তাগিদ এসেছে। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্শালের সহায়তায় বিদ্যাসাগর পুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পুস্তক ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ মুদ্রিত হয়েছিল ডি রোজারিও অ্যাণ্ড কোং থেকে। তার পর থেকেই বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয় ‘অন্নদামঙ্গল’, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, ‘জীবন চরিত’, ‘বোধোদয়’ (শিশুশিক্ষা), ‘ঋজুপাঠ’, ‘উপক্রমণিকা’, ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ ও ‘শকুন্তলা’। এই বইগুলির প্রকাশকাল ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ‘বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি বর্ণপরিচয় প্রকাশ করতে এত দেরী করলেন কেন? আসলে তিনি চেয়েছিলেন বাংলা উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। এর জন্য তাঁকে সতর্কভাবে এগোতে হয়েছে। তাই এত দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বের প্রয়োজন হয়েছিল।
শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াট বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহিত্যের অধ্যাপক করে নিয়ে এলেন এবং তাঁর উপর কলেজ পুনর্গঠন ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করার ভার দিলেন। ১৬ ডিসেম্বর (মাত্র দশ দিনের মধ্যে) তিনি দাখিল করলেন তাঁর সুগভীর চিন্তাপ্রসূত বৈপ্লবিক প্রতিবেদন। শিক্ষাপরিষদ তাঁর শিক্ষানীতি ও কলেজ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা পুরোপুরি মেনে নিয়ে তাঁকেই নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব দিলেন।
সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদনই বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির ভিত্তি। তাঁর সংস্কার প্রস্তাবের প্রথমেই এসেছে ব্যাকরণ বিভাগের কথা। তখন কলেজে ছাত্রদের পাঁচ বছর সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তে হত। বিদ্যাসাগর সুপারিশ করেছিলেন ব্যাকরণের দুরূহ নিয়মগুলি প্রথমেই বাংলা ভাষায় পড়ে নিতে হবে। সংস্কৃত শিক্ষাকে ছাত্রদের কাছে সহজ করে তোলার জন্য এবং অযথা পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যয় বাঁচানোর জন্য তিনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যকরণের উপক্রমণিকা ও ব্যকরণ কৌমুদী লিখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগের আলোচনায় তিনি বলেছিলেন সংস্কৃত রচনা পাঠ করার সঙ্গে ছাত্রদের বাংলা রচনাতেও অভ্যস্ত হতে হবে। তখন সকলকে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হত। তিনি ইংরেজি পদ্ধতি অনুযায়ী আধুনিক গণিতের শিক্ষা চালু করার কথা বললেন এবং হার্সেল প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিভিন্ন রচনাগুলি বাংলায় অনুবাদ করে সংকলিত করার উপর জোর দিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
বিদ্যাসাগরের একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল স্মৃতি বা আইন বিভাগে। তিনি স্মৃতি বিভাগ থেকে হিন্দুধর্মের সামাজিক আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব বাদ দিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে ছাব্বিশটিই ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি এবং তা পুরোহিত শ্রেণীর ব্যবহারের যোগ্য, কাজেই ওই গ্রন্থটি ছাত্রদের পড়ানোর প্রয়োজন নেই। দর্শন শ্রেণীতে রঘুনাথ শিরোমণির অনুমান দিধিতি ও অন্য তিনটি বই বাদ দিয়ে তিনি যুক্ত করলেন সাংখ্য প্রবচন, পতঞ্জলি সূত্র প্রভৃতি বইগুলি। তিনি বললেন সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন হিন্দুজাতির মননশীলতার চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে বলে তা অবশ্য পাঠ্য, কিন্তু তার পাশাপাশি আধুনিক ইউরোপের দর্শনগুলিও পড়ানো হোক যাতে ছাত্ররা নিজের দেশের দর্শন চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নব্য চিন্তার তুলনামূলক বিচার করতে পারে। তাছাড়া তিনি এটাও প্রস্তাব আকারে রাখলেন যে ইংরেজি শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে, কারণ ইউরোপের আধুনিক ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য উপায় নেই।
বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর ও ৫ অক্টোবর তারিখে লেখা দুটি চিঠিতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তার আগে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বসে তিনি ইংরেজিতে যে নোট লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের দক্ষ ও সার্থক স্রষ্টা হতে হলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় ঘটাতে হবে। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। সেইজন্যই তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষার চর্চাই অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন।
১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন – “ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্ত্বৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।” সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগরের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠিতে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চিঠিতে তিনি বলেছেন – “What we require is to extend the benefits of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished.” ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর তারিখে ডঃ মোয়াটকে লেখা আরও একটি চিঠিতে তিনি নিজের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন –“Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English . . . .।” তিনি চেয়েছিলেন এমন একদল যুবক তৈরী করতে, যারা তাদের রচনা ও শিক্ষণের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পৌঁছিয়ে দেবে। তার আগের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন – “That the students of Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt.”
বিদ্যাসাগর মনে করতেন শিক্ষার আলোকে মানুষের মনের মধ্যে জমে থাকা অন্ধকার দূর হয় এবং দৃঢ়প্রোথিত সংস্কারের শিকড়গুলি ক্ষয়ে যায়। কিন্তু সেই শিক্ষা আধুনিক হওয়া চাই এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও উন্নত মানবিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই। তিনি একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষক গড়ার উপর জোর দিতে চেয়েছেন। তাঁর মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার করতে চাওয়ার মূল কারণ শিক্ষাকে গণমুখী করা এবং শিক্ষার সুফলকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষাকে গণমুখী করার উদ্দেশ্যই তিনি পাঠক্রম থেকে ধর্ম সংক্রান্ত অনুশাসন ও বিধিনিয়মগুলি বাদ দিতে চেয়েছেন, যাতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখা যায়। সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে তিনি ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করে নিজেই ছেপে প্রকাশ করেছেন। তদানীন্তন স্কুল পরিদর্শক হেনরী উড্রো বলেছিলেন – “The public owes a deep debt of gratitude to Pundit Iswar Chunder Bidyasagar for his recent publications. He has taken the first place among the educators of his countrymen.”
বিদ্যাসাগর জাতিবৈষম্য মানতেন না। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে জাতিভেদ তুলে দিয়েছিলেন। সমাজসংস্কারে অবতীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তিনি নারীকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। একদিকে তিনি যেমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে সজাগ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শন ও মূল্যবোধকে সমাজে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তাঁর সামনে ছিল দুটি লক্ষ্য – শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। তিনি মনে করতেন এই দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে, যদি শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হয়।
১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এফ. জে. হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নোট তৈরী করেছিলেন তাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন – “সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেননা, সর্বত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের উন্নতি ও শ্রীবর্ধন সম্ভবপর।” এই নোটে তিনি দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায় অন্ততঃ ২৫টি মডেল স্কুল খোলার পরামর্শ দেন, যার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের হাতে। তিনি আরও প্রস্তাব রাখেন এইসব স্কুলের শিক্ষক তৈরী করার জন্য একটি ‘নর্মাল স্কুল’ থাকবে এবং ঐ স্কুল সংস্কৃত কলেজেই বসবে। বাংলার গভর্ণর হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের নোটটি অনুমোদন করে বড়লাটের কাছে পাঠান। ঠিক এই সময়েই (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) লণ্ডন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড্-এর কাছ থেকে ভারত সরকারের কাছে শিক্ষা বিষয়ক একটি নির্দেশনামা এসে পৌঁছেছিল। উডের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা দানের নির্দেশ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সহায়তা দান, শিক্ষাপরিষদের পরিবর্তে শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ।
ছোটলাট হ্যালিডের সুপারিশ ছিল নতুন ব্যবস্থার মধ্যেও বাংলার নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শনের দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের হাতেই থাকা উচিত। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১মে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য তাঁর বেতন দুশো টাকা বৃদ্ধি করে পাঁচশো টাকা করা হয়। নতুন দায়িত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর অনুভব করেন মডেল স্কুলে যে শিক্ষকেরা নিযুক্ত হবেন তাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের ভবনেই একটি ‘নর্মাল স্কুল’ খোলা হয়। বিদ্যাসাগরের মনোনীত ব্যক্তি অক্ষয়কুমার দত্ত এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।
শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের নীতির মূল সূত্রগুলি হল –
ক) আবশ্যিক শিক্ষার পাঠক্রম থেকে ধর্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি বাদ দিতে চেয়েছেন এবং আধুনিক বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তভুক্ত করতে চেয়েছেন।
খ) ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতি ঘটানোকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।
গ) ছাত্রদের মনে যুক্তি ও তুলনামূলক বিচারের বোধ সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে চেয়েছেন।
ঘ) ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয়ের উপরেই জোর দিতে চেয়েছেন এবং মাতৃভাষায় (অর্থাৎ বাংলায়) শিক্ষার প্রসার ঘটানোকে আবশ্যিক বলে মনে করেছেন।
ঙ) শিক্ষাকে গণমুখী করে তার উপযোগীতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিদ্যাসাগর বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘শকুন্তলা’ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে লিখিত হলেও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ এপ্রিল বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ও ১৪ জুন বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রহিত করার আন্দোলনের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের দায়িত্ব (বেথুন স্কুল) পালন করেছেন। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষের মন থেকে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও বিভিন্ন প্রচলিত প্রথায় অন্ধবিশ্বাস দূর করে তাকে আধুনিক মনোভাবাপন্ন করতে হলে শিক্ষাকে গণমুখী করতেই হবে। এই আদর্শ মনে জাগরূক ছিল বলেই তিনি দক্ষিণবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তার কাছে তাঁর পাঠানো রিপোর্ট থেকে জানা যায় সংস্কৃত কলেজে গরমের ছুটি হলে তিনি গ্রীষ্মের রোদে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মডেল স্কুল খোলার ব্যবস্থা করেছেন। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে (২২ আগস্ট, ১৮৫৫ – ১৪ জানুয়ারী, ১৮৫৬) নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে তিনি কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেছেন। এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল নদীয়া জেলার বেলঘোরিয়া, মহেশপুর, ভজনঘাট, কুশদহ ও দেবগ্রাম; বর্ধমান জেলার আমাদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, মানকর ও দাঁইহাট; হুগলী জেলার হারোপ, শিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর ও ক্ষীরপাই; মেদিনীপুর জেলার গোপালনগর, বাসুদেবপুর, মালঞ্চ, প্রতাপপুর ও জকশুরে।
বাংলা সরকারের সচিব রিভার্স টমসনকে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান এতই নীচু যে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য কোন খরচই তারা করতে পারে না। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন সরকার যদি এ ব্যাপারে মনস্থির করেন তাহলে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য তৈরী হতে হবে। শুধু পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে নিজের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে তিনি একটি সান্ধ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়াশুনা করত এবং তাদের বই ও খাতাপত্র দেওয়া হত। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের কার্মাটাড়ে স্টেশনের পাশে তিনি একটি বাংলো বাড়ি তৈরী করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া। সেখানের অধিবাসী সাঁওতাল ও ধাঙড়দের জন্য অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে তিনি আদিবাসী কল্যাণের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত তৈরী করে গেছেন।
————————————————-
বাংলা ভাষায় শিক্ষার সূচনাপর্ব এবং বিদ্যাসাগর
(দ্বিতীয় ভাগ)
রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তারের নীতিতে নারী সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বেথুন ও বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল) স্থাপিত হয়। বাংলায় তখনও স্ত্রীশিক্ষা সমাজের অনুমোদন পায় নি। কিন্তু অভিজাত ও ভদ্রঘরের মেয়েরা বিদ্যালয়ে না এলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভাঙলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের চেষ্টায় ঐ বিদ্যালয়ে মদনমোহনের দুই কন্যা ছাড়াও রামগোপাল ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, নীলকমল বন্দোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কন্যারাও যোগ দিয়েছিল। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বেথুনের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সরকার ঐ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করে। স্কুলকে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন নি। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটি সরকারি পরিচালনায় চলে যাওয়ার পর নতুন কমিটিতে তিনিই অবৈতনিক সম্পাদক হন। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সম্পাদক হিসাবে বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও কাছাকাছি শহরগুলিতে নারী শিক্ষার ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবেন। কিন্তু তাঁর সেই আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নি। সরকারী নীতির সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য ও নীতির মিলন ঘটেনি বলে বেথুন স্কুল থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল।
বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন সমাজকে সংস্কার ও দেশাচার থেকে মুক্ত করতে হলে নারী সমাজকেও সংস্কারমুক্ত করতে হবে। শিক্ষার প্রসার না ঘটালে নারী চেতনাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সম্ভব নয়। একথা বুঝেছিলেন বলেই তিনি নারী সমাজেও শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উড্ সাহেবের শিক্ষাসম্পর্কিত নির্দেশনামায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের নির্দেশ ছিল। একাজে গভর্ণর হ্যালিডে বিদ্যসাগরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মৌখিক অনুমোদন পেয়ে বিদ্যাসাগর কাজ শুরু করেছিলেন এবং হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। অসম্ভব কর্মতৎপরতায় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলার গভর্ণর হ্যালিডে তাঁর ১৯.১১.১৮৫৮ তারিখের নোটে বিদ্যাসাগরের এই অসামান্য সাফল্যকে স্বীকার করেছিলেন।
এতকাল বিদ্যাসাগর সরকারী দপ্তর থেকে শিক্ষানীতির রূপায়ণে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু এবার তিনি সেখান থেকেই বাধা পেলেন। শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং তাঁকে কাজে বিশেষ স্বাধীনতা দিতে চাইলেন না। তাছাড়া প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজের গুরুত্বকেও খর্ব করা হল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংরেজ সৈন্যদলের ভলান্টিয়ার বাহিনীকে থাকতে দেওয়ার জন্য তাঁকে কলেজ ভবন ছেড়ে দিতে হয়। এবিষয়ে তিনি গর্ডন ইয়ংকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ আগষ্ট ও ২ সেপ্টেম্বর তারিখে দুটি পত্র লিখেছিলেন। ঐ বছরের ৩১ আগষ্ট তারিখে তিনি গভর্ণর হ্যালিডেকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এটা স্পষ্ট যে সরকারী দপ্তরের লালফিতের ফাঁস যেমন তাঁর পছন্দ ছিল না তেমনই বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কিত ব্যবস্থাকেও তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। এই চিঠি লেখার এক বছর পরে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি হ্যালিডেকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে কাজ করা তাঁর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠেছে, বিশেষতঃ বহু অর্থব্যয় করে যে প্রণালীতে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল সে পদ্ধতির প্রতি তাঁর কোনো প্রকার সহানুভূতি ছিল না।
বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য যে পথে তিনি এগোতে চাইছেন সরকারী নীতি তার প্রতিবন্ধক। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে স্কুল পরিদর্শক হেনরী উড্রো শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ংকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন – “. . . Pundit Iswar Chunder Bidyasagar opened forty female schools, secured an attendance of more than 1300 girls of good caste, and soon found himself liable for between three and four thousand rupees.” ভারত সরকার তখন ব্যয়সঙ্কোচ নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই যে টাকা খরচ করেছিলেন শুধু সেটুকুই মঞ্জুর হল, কিন্তু তাঁর স্থাপন করা ৪০টি বিদ্যালয়ের খরচ বহন করতে সরকার রাজি হলেন না। শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং-এর নোট থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে –“Special aid solicited to a number of female schools by Pandit Iswar Chander Sarma. Aid refused by Supreme Government . . .”। এর ফলে বিদ্যাসাগরের পক্ষে শিক্ষাবিষয়ক নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আর কিছু করার থাকল না। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি চাকরী থেকে বিদায় নিলেন।
শিক্ষার প্রসারে (বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণে) সরকারী নীতির কার্পণ্য বিদ্যাসাগরকে ব্যথিত করেছিল, কিন্তু তিনি হতোদ্যম হন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা বালিকা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। নারীশিক্ষার জন্য তিনি একটি আলাদা অর্থভাণ্ডার খুলেছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তি মাসিক চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কয়েক মাস পরে সকলেই পিছিয়ে গিয়েছেন। সেসিল বিডন বা রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রমুখ কয়েকজন কিছু কিছু চাঁদা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ব্যয়ভারের বিপুল অংশ তিনি নিজেই বহন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির সাফল্যের জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর তারিখে স্যার বাটল ফ্রিয়ারকে লেখা তাঁর একটি চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করছি –“You will no doubt be glad to hear that Mufussil Female Schools, to the support of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contiguous to Calcutta and schools are being opened from time to time.”
১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে শিক্ষাব্রতী মিস কার্পেন্টার এদেশে এসেছিলেন নারীশিক্ষার অবস্থা দেখতে। তিনি প্রথমেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিনসন বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে এই বিদূষী মহিলার সঙ্গে বেথুন স্কুলে সাক্ষাতের অনুরোধ জানান। সেখানেই মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তিনি ও অ্যাটকিনসন, বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতা ও উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। পরিশেষে মিস কার্পেন্টার এদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতির জন্য একটি ‘ফিমেল নর্মাল স্কুল’ স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। তিনি ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে-র কাছে প্রেরণ করা বক্তব্যে জানালেন এদেশের নারীসমাজ থেকে শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার জন্য মিস কার্পেন্টার যে পরিকল্পনা নিতে চান তা হিন্দুসমাজের তখনকার অবস্থায় ফলপ্রসূ হতে পারে না। গভর্ণর উইলিয়ম গ্রে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে মেনে নিলেও নর্মাল স্কুল স্থাপনের দাবীকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষাদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বেথুন স্কুলেই শিক্ষাদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপিত হবে। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নতুন নিয়ম কার্যকরী হল। তার পরেই বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এখানে জানিয়ে রাখি অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পর পরবর্তী গভর্ণর জর্জ ক্যাম্বেলের আমলে সেই স্কুলটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি ছিলেন প্রখর বাস্তব চেতনাসম্পন্ন পুরুষ। এই প্রসঙ্গে Daniel Lerner-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি – “He assumes a calculating attitude towards a manipulable and open future. He is therefore rational and goal-oriented.” প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় – “বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের ন্যায় practical ব্যক্তি আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ।”
নারীশিক্ষার কাজ থেকে বিদ্যাসাগর কখনই পিছিয়ে যান নি। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বীরসিংহ গ্রামে ভাই শম্ভুচন্দ্রের মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়টি মায়ের নামে উৎসর্গ করে তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘ভগবতী বিদ্যালয়’। বিদ্যাসাগরই আধুনিক ভারতের প্রথম মানুষ যিনি শিক্ষার এই মূলনীতিটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে নারীকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যই নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ করা দরকার। তাছাড়া বহু ব্যক্তিকে তিনি বিদ্যালয় খুলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে বর্ধমানের চকদিঘীর অপুত্রক জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায় তাঁর টাকা ও সম্পত্তি অবৈতনিক এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপনের জন্য দিয়েছিলেন। ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্নকে তিনি টোল করার জন্য টাকা দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শে কান্দিতে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ইংরেজি-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঘাটালে স্কুলবাড়ি তৈরীর জন্য তিনি অর্থসাহায্য করেছেন। বৈঁচিগ্রামের জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়ে তিনি সেখানে কমলেকামিনীদেবী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করান।
শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কাজ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও কলেজের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –“সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুসন। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।” বস্তুত কোনও সরকারী সাহায্য না নিয়ে এবং শুধুমাত্র বাঙালী অধ্যাপক দিয়ে দেশীয় ব্যবস্থাপনায় একটি বেসরকারী কলেজ স্থাপন তাঁর অদম্য পৌরুষেরই প্রমাণ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন – “ইহাই কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বেসরকারী কলেজের পথপ্রদর্শক। এই মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পাদ্রীদের কলেজের উপরেই বহুল পরিমাণে বাঙ্গালীর উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ নির্ভর করিত।”
১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে স্কুল কমিটির সভাপতি রূপে যোগদান করেছিলেন। পরে স্কুলের নাম বদলে হয় ‘হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল’, তিনি হন সম্পাদক। পরিচালকরা স্কুল চালাতে না পারায় পুরো কর্তৃত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে আসে। ১৮৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হিন্দু শব্দটি বাদ দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম দেন ‘মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন’। স্কুল পরিদর্শক হেনরী উড্রো ১৮৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদনে লিখেছিলেন –“The Metropolitan Institution, under the management of Pundit Iswar Chunder Bidyasagar, is the best of these schools and was at the last University Examination one of the most successful schools of India.” বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল ভাল হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে তিনি কলেজ খোলার জন্য সচেষ্ট হন। অনেক চেষ্টার পর ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে উপাচার্য বেলির সহায়তায় সিণ্ডিকেট মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনকে অনুমোদন করলে গভর্ণর তাতে সম্মতি দেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. ক্লাশ খোলার অনুমতি পাওয়া গেলে এটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত হয়। শিক্ষা অধিকর্তা এ. ডব্লিউ. ক্রফট্ ১৮৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ প্রতিবেদনে লিখেছিলেন –“The Metropolitan Institution is the only un-aided college which regularly teaches the full University Course in Arts . . .” এর প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সূর্যকুমারের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে বিদ্যাসাগর আবার নিজের হাতে দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা সি. এইচ. টনি তাঁর ১৮৮৮-৮৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদনে লিখেছিলেন “The Metropolitan Institution continues to be by far the largest of all the colleges in the province and probably in India . . . .”।
বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন দেশজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলবেন যার ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। অত্যন্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন বলেই তিনি একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন, আবার অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন। অথচ শিক্ষণীয়, বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে তিনি পশ্চিমের বিজ্ঞানচেতনা ও মানবিকতার দর্শনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সে যুগের মানুষকে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদর্শন উপহার দেওয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। যুগের প্রয়োজনেই যেন তিনি অসাধারণ ব্যত্তিত্ব ও অসামান্য জীবনচেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যুক্তির সাহায্যে তিনি মানুষের মনের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত সংস্কারকে ছিন্ন করতে চেয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন – “কাজের পথের বাধা ছিন্ন-ভিন্ন করিবার জন্য তাঁহার হাতে ছিল একখানা অসি; চালনা নৈপুণ্যে সেই একখানা অসিকে দশখানা মনে হইয়াছে – সাহিত্য, করুণা, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার, কত না মনে হইয়াছে; কিন্তু অসি দশখানা নয়, একখানা মাত্র, সে খানার নাম লজিক।”
সহায়ক গ্রন্থাবলী :
১. Dr. Amitabha Mukherjee – Reform and Regeneration in Bengal।
২. সবিতা চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক।
৩. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘বিদ্যাসাগর’।
৪. ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় – মুদ্রণ শিল্পে বিদ্যাসাগর (সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর পরিক্রমা)
৫. বিনয়ভূষণ রায় – শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়।
৬. সন্তোষকুমার অধিকারী – বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি।
৭. Dr. Ramesh Chndra Mazumdar – Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century
৮. David Kopf – British Orientalism and Bengal Renaissance।
৯. Santosh Kumar Adhikari – Vidyasagar and the Regeneration of Bengal।
১০. বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত ‘বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী’।
১১. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন – বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (বুকল্যাণ্ড সংস্করণ)।
১২. Arabinda Guha – Unpublished Letters।
১৩. Subal Chandra Mitra – Iswar Chandra Vidyasagar
১৪. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৫. বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর পত্রিকা (দ্বিতীয় সংকলন)।
১৬. সন্তোষ কুমার অধিকারী – বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয় (অনন্য প্রকাশন)।
১৭. বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী।
১৮. সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী – মেট্রোপলিটান কলেজের ইতিহাস (বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা)।
*******************************************

রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর পরিচিতি:
রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১৬ মে ১৯৭৪, কলকাতায়। ১৯৯৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরীরবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে রাজ্য প্রশাসনে আধিকারিক হিসেবে কর্মরত। ছাত্রাবস্থা থেকেই নিয়মিত লেখালিখির শুরু। এ যাবৎ বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরে যাব একদিন নৈঃশব্দ্য হয়ে’ এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘স্বপ্নের মুখ ঢেকে রাখি দর্পণে’ পাঠকমহলে জনপ্রিয় হয়েছে। প্রবন্ধ সংকলন ‘বেদ থেকে পুরাণ’ পাঠক ও সমালোচকদের কাছে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সারস্বত সাহিত্য সম্মান, বিবৃতি সাহিত্য সম্মান, শীতলগড় সাহিত্য সম্মান ইত্যাদি বিবিধ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।