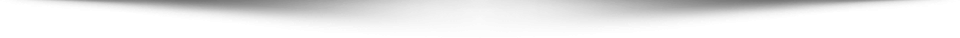মাপ
সুজয় দত্ত
আমি দাঁড়িয়ে আছি অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে। ঘাড়-মাথা-মেরুদন্ড সোজা, হাতদুটো টানটান শরীরের দুপাশে,পাদুটো একসাথে জোড়া। না,স্কুলের পিটি স্যারের ক্লাস নয়,ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পের প্রশিক্ষণ শিবির নয়, নেহাতই একটা দর্জির দোকান। দরজার ওপরের রং চটা সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা “সুরুচি টেলার্স”। ফুলবাগান মোড়ের বাসস্ট্যান্ড থেকে যে রাস্তাটা বাটার জুতোর দোকান হয়ে বাঁয়ে চলে গেছে পুরোনো চটকলের দিকে,তার বাঁকের ঠিক মুখে উল্টো ফুটে কয়েকটা ঘুপচি দোকান। সেগুলোরই একটাতে প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে বাবার হাত ধরে আমার আনাগোনা আর অ্যাটেনশনে দাঁড়ানো। পুজোর নতুন জামা-প্যান্টের মাপ দিতে।
কতটুকুই বা জায়গা? খুব বেশী হলে দশফুট বাই দশফুট। তারই মধ্যে একদিকে ড্রয়ার-ওয়ালা টেবিল পেতে কাপড়ের লম্বা লম্বা থানে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ মারা আর বড় বড় কাঁচি দিয়ে দাগ বরাবর কচকচ করে কাটার কাজ হচ্ছে। অন্যদিকে দেওয়াল ঘেঁষে সাইকেলের মতো বিরাট চাকাওয়ালা আর প্যাডেল লাগানো কয়েকটা সেলাই কল ঘড়ঘড় শব্দে অনবরত সেলাই করেই চলেছে। তাতে বসে থাকা দর্জিদের কপাল-ঘাড়-গলা বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চকচক করছে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা গোটা তিনেক টেবিল-ফ্যান ফুল স্পীডে ক্রমাগত এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়েও সেপ্টেম্বরের ভ্যাপসা গরমকে বাগে আনতে পারছেনা। কোণের অন্ধকার মতো জায়গাটায় লোকচক্ষুর আড়ালে একটা ছোট্ট পর্দা দেওয়া ট্রায়াল রুম। ওর ভেতরে পর্দার আড়ালে ঠিক কী আছে,সে নিয়ে প্রথম প্রথম আমার ভীষণ কৌতূহল ছিল। তখন আমি এতো ছোট যে আমার জামা-প্যাণ্টের ট্রায়ালও লাগতো না। একবারেই হয়ে যেত। পরে একটু বড় হয়ে ওই ছোট্ট কুঠুরিটায় ঢুকলাম যখন,দেখে হতাশ হলাম যে একটা পেল্লায় সাইজের আয়না ছাড়া ওখানে কিছুই নেই।
তবে ওর চেয়েও বড় বিস্ময় লুকিয়ে ছিল সেই খুপরি দোকানের পিছনদিকে। এমনিতে দোকানটায় ঢুকে ছাদের দিকে তাকালে শুধুই নজরে পড়ত একদিক থেকে আরেকদিক অবধি খাটানো সারি সারি চকচকে রড, আর তাতে অগুনতি হ্যাঙ্গারে টাঙানো সদ্য-তৈরী জামা কাপড়। নানা রঙের রামধনু। দেখে অবাক হতাম খদ্দেররা পোশাক নিতে এলে তাদের রসিদের নম্বর মিলিয়ে একটা লম্বা হুক-লাগানো আঁকশি দিয়ে সেই উঁচু রডগুলো থেকে ঠিক হ্যাঙ্গারটা পেড়ে আনতে কী দারুণ পারদর্শী ছোকরা কর্মচারীটা। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি ওই ঝুলন্ত পোশাক আশাকের আড়ালে কিছু থাকতে পারে। একদিন সন্ধ্যের মুখোমুখি বাবার সঙ্গে প্যান্টের ট্রায়াল দিতে যাচ্ছি, এমনসময় হঠাৎ লোডশেডিং। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। আচমকা বিদ্যুৎ চলে যাওয়াকে তখন লোডশেডিংই বলত সবাই—‘পাওয়ার কাট’ কথাটা শিখেছি অনেক পরে। দোকানে পৌঁছে দেখি কাপড়-কাটা টেবিলে একটা মোটা মোমবাতির কাঁপা কাঁপা শিখা,সামনেটায় কেউ নেই,সেলাই কলগুলোও ফাঁকা,শুধু দেয়ালজুড়ে তাদের অদ্ভুত ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। কয়েকমুহূর্ত পরে খেয়াল হল আরেঃ— সেলাইকলে কেউ নেই অথচ ঘড়ঘড় শব্দটা আসছে কোথা থেকে? স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি–মনের ভুল তো নয় ! স্বীকার করতে দ্বিধা নেই,সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। বাবাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই ছোকরা কর্মচারীটা চায়ের ভাঁড় হাতে ফিরে এসে সব রহস্য উন্মোচন করে দিল। আমাদের দেখে হাঁক পাড়লো,”ও মনসুরকাকা, একশো চল্লিশ দুশো পঁচিশের প্যান্টটা হয়েছে?” দেখলাম ভুতুড়ে গল্পে যেমন ছাদের কড়িকাঠ থেকে ভূত নেমে আসে,অনেকটা সেরকমভাবেই ঝুলন্ত সব জামাকাপড়ের আড়াল থেকে কোথাকার কোন ফোকর দিয়ে একটা মই বেয়ে নামছে একজন বেঁটেখাটো চেহারার দাড়িওয়ালা লোক। নেমেই একগাল দেঁতো হাসি,”এজ্ঞে না কত্তা,হেইডা অয় নাই এহনো”। অগত্যা আবার দুদিন বাদে সেই “ভূতের” সেলাই করা প্যান্ট ট্রায়াল দিতে যেতে হল। এবার ভরদুপুরে,তাই স্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম দোকানের পিছনদিকে মই বেয়ে দোতলায় ওঠার ফোকর,আর কানে এল দোতলায় বসা দর্জিদের কথাবার্তা। পূর্ববঙ্গের ভাষায়।
আমি যখন মাপ দেওয়ার জন্য অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম,তখনও ওই ভাষাতেই কথোপকথন চলত রায়জেঠু আর তাঁর ছেলের মধ্যে। দোকানের মালিককে আমি “রায়জ্যেঠু” বলতাম,আর আমার বাবা “রায়দা”। ওঁর নামটা জেনেছিলাম অনেক বছর বাদে। সে-কথায় পরে আসছি। আমি একটু ছটফট করলে আমাকে “নইড়ো না” বলে মৃদু বকুনি দিয়ে আমার গায়ে ফিতে লাগাতেন আর বাবাকে জিজ্ঞেস করতেন, “পগড পিসনে অইবো, না পাশে?”,”সামনের ফুডায় বোতাম দিব,না শেন?”,”জুল কোমর থিক্যা নিব,না প্যাডের উপর থিক্যা?”। বাবা চিরকালই পোশাক আশাকের ব্যাপারে রক্ষণশীল,তাই ছেলেকে এই বয়সেই হিপ্ পকেট দেওয়া চেন-ওয়ালা প্যান্ট পরে উচ্ছন্নে যেতে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। ওঁর পছন্দ শুনে রায়জ্যেঠু যত না হতাশ হতেন,তার চেয়ে অনেক বেশী হত লিটনদা,মানে ওঁর ছেলে। একদিন বলেই ফেলল,”কাকা,খোকারে এহন হইতে এট্টু ফ্যাশন না শিখাইলে চিরডা কাল গাঁইয়া রইয়া যাইব যে। একবার নুতন ডিজাইন পরাইয়া দেহেন,ফাসক্লাস লাগব”। পাছে ছেলের আলপটকা মন্তব্যে খদ্দের অসন্তুষ্ট হয়,তাই ওকে সেদিন ধমক দিয়ে চুপ করিয়েছিলেন রায়জ্যেঠু। পুজোর মুখোমুখি সময়টা ছাড়া বছরের আর যেদিন ওই দোকানে একবার ঢুঁ মারতাম আমি,সেটা অক্ষয় তৃতীয়া। বাংলা নববর্ষের বদলে ওই দিনই দোকানের হালখাতা করতেন রায়জ্যেঠু। পুরোনো, বাঁধা খদ্দেরদের সেদিন আলাদা খাতির। বাবা সকালের বাজারটাজার সেরে ফিরতি পথে দোকানের সামনে “রায়দা” বলে দাঁড়ালেই উনি “আপনের জইন্য রাইখ্যা দিসি” বলে ভেতর থেকে একবান্ডিল ক্যালেন্ডার আর একটা বড়সড় মিষ্টির বাক্স এনে হাতে ধরিয়ে দিতেন। আমি সঙ্গে থাকলে আমার উপরি পাওনা আলাদা একটা মিষ্টি। আমাদের সরকারী আবাসনের ছোট্ট ফ্ল্যাটে তো তখন দুটো মাত্র ঘর,অত ক্যালেন্ডার টাঙাব কোথায়? অতএব আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীকে বিলি করা হত সেগুলো।
এমনিতে খদ্দেরদের খাতির-টাতির করলেও একটা ব্যাপারে কখনো ছাড় দিতে দেখিনি রায়জ্যেঠুকে। জামাকাপড়ের মেকিং চার্জ। ওটার ক্ষেত্রে উনি ছিলেন এককথার মানুষ। অন্য দর্জির তুলনায় বেশী চার্জ করেন বলে পাড়ায় দুর্নামও ছিল খানিক—অনেকেই ওঁর কাছে না গিয়ে বাসরাস্তার ওপারে চারু টেলার্স বা মডার্ন টেলার্সে যেত। কিন্তু বাবা কক্ষণো সে-পথ মাড়াননি। বড়ো জোর দোকানে গিয়ে হাসতে হাসতে বলেছেন, “রায়দা, এভাবে ভাতে মারলে তো মুশকিল। গতবছর প্যান্ট পিছু চোদ্দ টাকা নিলেন,এবার একলাফে কুড়ি?” উত্তরে ওদিক থেকেও বিব্রত হাসি এসেছে,”কী কইরবো বলেন দাদা,মাগ্গি-গন্ডার বাজার—“। ব্যস,ঐটুকুই। আসলে আমাদের সঙ্গে ওঁর এই দীর্ঘদিনের সম্পর্কটা দোকানদার-খদ্দেরের মামুলি ব্যবসায়িক সম্পর্কের গন্ডী ছাড়িয়ে কখন যে আধা-আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে,আমরা খেয়াল করিনি। খেয়াল হয়েছে কয়েকটা ছোট ছোট ঘটনায়,যা কৃতজ্ঞতা বোধকে নিবিড়তর করেছে। একবার যেমন দুর্গাপুজো শুরুর আগের দিন,মানে পঞ্চমীর সন্ধ্যেয়,আমি পুজো প্যান্ডেলের সামনে কচিকাঁচাদের সঙ্গে খেলার সময় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে খোঁচা খোঁচা শিক-ওয়ালা একটা লোহার গেটের ওপর চড়ে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে হাত ফস্কালাম আর নতুন জামাটা গেল এত্তখানি ছিঁড়ে। ওই অবস্থায় বাড়ীতে ঢুকলে বকুনি নয়,মার্ পড়বে পিঠে। তাই ভয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে মামাতো দিদির হাত ধরে রায়জ্যেঠুর দোকানে গেলাম বাঁচবার একটা মরিয়া চেষ্টা করতে—যদি তখনও খোলা থাকে। ভাগ্য ভাল,উনি তখন সবে দোকানের শাটার বন্ধ করছেন,তালা লাগানো হয়নি। লাগিয়ে ফেললে খুলতো সেই একেবারে দশমীর পরে। আমার ওই করুণ দশা দেখে আবার শাটার তুলে জামাটা নিজে হাতে সেলাই করে দিলেন। এ-জিনিস পৃথিবীর কোন্ কাস্টমার সার্ভিস ম্যানুয়ালে পাওয়া যাবে?
“সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়”—এই ‘ক্লিশে’টার মাহাত্ম্য হঠাৎই উপলব্ধি করে মানুষ তার জীবনে,যখন একদিন সকালে উঠে দেখে গলার স্বরটা আর আগের মতো শোনাচ্ছে না বা ঠোঁটের ওপর কচি ঘাসের মতো গোঁফের রেখা। আমিও সেইভাবেই আমার শৈশবকে পুরোনো খেলনার বাক্সে পাকাপাকি ভাবে চাবি দিয়ে রেখে এক সময় বড় হয়ে গেলাম। সেকেন্ডারী,হায়ার সেকেণ্ডারীর চৌকাঠ পেরিয়ে চললাম কলেজে। দেখলাম চারপাশের পৃথিবীটা অবিশ্বাস্য গতিতে বদলে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে মানুষের বাইরেটা শুধু নয়–ভেতরটাও। আমার কলেজে যাওয়ার ঠিক আগেই অবসর নিলেন বাবা,ফুলবাগানের সরকারী আবাসনের পাট চুকল আমাদের। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে একটু একটু করে জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে দেখলাম সুরুচি টেলার্স মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে।
এর পরের কয়েক বছর চলল আমার রেডিমেড পর্ব। তৈরী পোশাকের দোকানে ঢুকে নিজের মাপ ঠিকঠাক বললেই শোকেসে থরে থরে সাজানো নানা রঙের নানা ডিজাইনের জামাকাপড় মেলে ধরা হবে ক্রেতার চোখের সামনে। সেগুলো থেকে বেছে বুছে পছন্দ করে নিলেই হল। ঝঞ্ঝাট কম, সময়েরও সাশ্রয়। তখনও অবশ্য নামী দামী ব্র্যান্ডে ছেয়ে যায়নি বাজার। নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের হাত ধরে দেশবিদেশের রকমারি ব্র্যান্ড মধ্যবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্তের নাগালে আসতেই অগুনতি ছোট ছোট দোকানপাট শুকনো ফুলের মতো ঝরে গেল। পন্ডিতেরা চশমা-নাকে বললেন এমনটাই তো স্বাভাবিক—দুনিয়ায় টিকে থাকতে গেলে লড়ে জিততে হয়। ক্রেতা আর উপভোক্তারা মহানন্দে বিশ্বায়নের জয়গান গাইতে লাগল। আর একদল মানুষ যারা কয়েক প্রজন্মের পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল তাদের পারিবারিক ব্যবসা, হঠাৎ দেখল তাদের হৃদয় নিংড়ানো ঘামরক্তের ফসল আজ অপ্রাসঙ্গিক আর অবাঞ্ছিত।
ফুলবাগান মোড়ের সুরুচি টেলার্সও এই দলে পড়ে কিনা,অনেকদিন অবধি জানার সুযোগ হয়নি আমার। কারণ কলেজের পাট চুকিয়ে ইতিমধ্যে আমি পাড়ি দিয়েছি বিদেশে। উচ্চশিক্ষার জন্য। আমার মতো যারা নিত্যনতুন স্রোতে গা ভাসাতে চায়না,ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতেই বেশী স্বচ্ছন্দ,প্রবাসী জীবনের সামাজিক আর পেশাগত চাহিদা মেটাতে তাদেরও পছন্দ-অপছন্দ আর বেশভূষায় পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়ে একসময়। আমারও পড়েছিল,তবে যতটুকু না হলে নয় ততটুকুই। দেশ ছাড়ার পর বেশ কয়েক বছর কলকাতা যাওয়ার লম্বা ছুটি মেলেনি। মিলল একেবারে শিক্ষাপর্ব শেষে কর্মজীবনে ঢোকার পর। একই সঙ্গে এগিয়ে এল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দিন। হবু জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার যতটুকু সময় পেয়েছিলাম,তার মধ্যে একদিন ওকে নিয়ে গেছিলাম আমার পুরোনো পাড়ায়। আজন্ম শৈশবের স্মৃতিজড়ানো সেই পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ল আরেঃ—বাটার জুতোর দোকানের উল্টোদিকে একপাশে ঝাঁ-চকচকে আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ি আর অন্যপাশে নতুন গজানো একটা পাঁচতলা নার্সিং হোমের মাঝখানে ওটা কী? একটা পুরোনো আমলের বেমানান সাইনবোর্ড টাঙানো একতলা দোকানঘর। তাতে লেখা “সুরুচি ফ্যাশন ডিজাইনার্স অ্যান্ড আউটফিটার্স”। তার মানে—তার মানে কি রায়জ্যেঠু এখনো—? আমার ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে তক্ষুণি দেখা করি,নিজের পরিচয় দিই। এতবছর পর নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু দোকানটা যে এখন বন্ধ। তার মানে আরেকদিন আসতে হবে। ঠিক আছে,কুছ পরওয়া নেহি,আসব। সেদিন বাড়ী ফেরার পথে আমার ভাবী স্ত্রীর কাছে উজাড় করে দিয়েছিলাম ওই দোকানকে ঘিরে মনের মণিকোঠায় জমে থাকা সব স্মৃতি।
আসব ভাবলাম বটে,কিন্তু চট করে আসা হয়ে উঠল না। এমনিতেই বিদেশ থেকে কলকাতায় এলে আত্মীয়স্বজনদের নেমন্তন্ন রাখতে রাখতে হিমশিম খেতে হয়,তার ওপর এবার তো বিয়ে,শিরে সংক্রান্তি। শেষ অবধি সপ্তাহ দুয়েক বাদে আবার ওমুখো হওয়ার ফুরসৎ মিলল। ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখলাম দোকানটা খোলা। ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে বড় অচেনা লাগল। আয়তনে বাড়েনি,কিন্তু দেওয়াল জুড়ে কাচের শোকেস,সামনে একদিকে ছোট্ট ক্যাশ কাউন্টার আর আরেকদিকে একটা আধুনিক কাটিং মেশিন। পিছনদিকে সেই সাইকেলের চাকা-ওয়ালা মান্ধাতা আমলের ঘরঘরে সেলাইকল গুলোর বদলে কয়েকটা স্টিচিং-নিটিং কম্বো মেশিন। দু-তিনজন মহিলা সেখানে বসে কাজ করছেন। থাকার মধ্যে রয়েছে পুরোনো দিনের সেই ছাদ জোড়া রডগুলো আর তাদের গা থেকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে বিশাল বিশাল প্লাস্টিক শীটে মোড়া জামাকাপড়। মেয়েদের ফ্যাশন দুরস্ত পোশাকই বেশী। আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক ভদ্রমহিলা “ও কাকু,বাইরে আসুন” বলে হাঁক পাড়তেই লাগোয়া একটা চেম্বার থেকে মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল-ওয়ালা মধ্যচল্লিশের এক ভদ্রলোক গেঞ্জি আর পাজামা পরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন,”বলেন দাদা,কী করাইবেন?”
চুল পেকেছে,মধ্যপ্রদেশে চর্বিও জমেছে একটু,চোখে উঠেছে চশমা—কিন্তু এই মুখ চিনতে আমার ভুল হবে? সেই পান-খাওয়া লাল ঠোঁট,সেই সরু গোঁফ,সেই বাচনভঙ্গী। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছি দেখে ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল,”কাপড় আইনাসেন সাথে? দ্যান। আপনেরি অইব তো?”
“আমাকে চিনতে পারছ না—তাই না লিটনদা?”
“ন্-না তো। ঠিক খেয়াল পড়সে না। এহেনে কাম করাইসেন আগে?”
“একশোবার। তোমাদের হাতের জামাকাপড় পরেই তো বড় হয়েছি” বলে আমি সহাস্যে নিজের পরিচয় দিলাম। একটু একটু করে ওর মনে পড়ল। তারপর “খোকা !!!” বলে এমন একখানা হাঁক পাড়লো যে দোকানের সবাই দেখলাম কাজ থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোথায় থাকি,কী করি,বিয়ে করেছি কিনা,মা-বাবা কেমন আছে—ওর এক নিঃশ্বাসে করা এতগুলো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তারপর আমার প্রশ্ন করার পালা। জানতে চাইলাম,”রায়জ্যেঠু এখন আর তাহলে দোকানে আসেন না? তোমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন? আছেন কেমন উনি?”
মুহূর্তকাল নীরব থেকে বাঁ দিকের দেওয়ালে ঝোলানো গণেশ মূর্তির পাশে একটা ছবির দিকে আঙুল দেখায় ও। রজনীগন্ধার শুকনো মালা ঝুলছে তাতে। এক বিরলকেশ,লোলচর্ম বৃদ্ধ। নীচে লেখা শ্রী হরিহর রায়। শ্রী-এর ওপর চন্দ্রবিন্দু। মনে পড়ল,ঠিক এইখানে দাঁড়িয়েই আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে শেষবার মাপ দিয়েছিলাম ওঁর কাছে।
“তুমি এখন থাকো কোথায় লিটনদা? সেই কাদাপাড়ার পুরোনো বাড়ীতে?”
“না রে ভাই। আমি তো বিয়ার পর রাসমণি বাজারে ফেলাট ভাড়া লইয়া উইঠ্যা আইলাম। বাবুরে বইল্যা বইল্যাও সেইহানে আইনতে পারি নাই। মইরলোও হেই কাদাপাড়াতেই।”
“ও। তা সে বাড়ী কি এখন ফাঁকা পড়ে আছে?”
“না না। হেই বাসা উইল কইররা দিয়া গেসে যোগমায়া বৃদ্ধাশ্রমেরে। অহন বুড়া বুড়ীরা থাইক্যে। আর টাহাপয়সা যা জমাইসিল,তার চাইর আনা দিয়া গেসে মহাকালী পাঠশালারে।”
বুঝলাম। সারাজীবন সবাইকে ফিতে দিয়ে মেপেছেন যে মানুষটা,তাঁর চওড়া হৃদয়কে মাপার মতো ফিতে এ-দুনিয়ায় মিলবে না। হঠাৎ আমার মাথায় কী খেলে গেল,দুম করে বলে বসলাম,”লিটনদা,আমাকে এবার অনেকেই জামাপ্যাণ্টের কাটপিস দিয়েছে তো,কলকাতা থেকে তৈরী করিয়ে না নিয়ে গেলে ওগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হবে। তোমাকে যদি দিয়ে যাই,তুমি করে দিতে পারবে? দু-সপ্তাহের মধ্যেই চাই কিন্তু। মাপ আজকেই নিয়ে নাও।”
দেখলাম ওর চোখে বিস্ময় আর দ্বিধা। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না আমি এই অনুরোধ করছি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,”ঠিক আসে। তুমি বইল্লে যহন —। খাড়াও,ফিতাডা লইয়া আসি।”
অনেক,অনেক বছর পর আবার এখানে আমি অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে। ভাবার চেষ্টা করছিলাম,হঠাৎ এই খেয়াল চাপল কেন মাথায়? কোনো দরকার ছিলনা। বিয়ের জন্য এসেছি বলে এবার এমনিতেই এতো পোশাক আশাক হয়েছে,প্লেনে অত নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আর আমার গুটিকয় প্যাণ্ট না বানালে লিটনদার দোকানও নিশ্চয়ই লাটে উঠবে না। তাহলে? আসলে আর কিছুই না—ছোটবেলার সেই হারানো সোনালী দিনগুলোকে অপ্রত্যাশিতভাবে চোখের সামনে পেয়ে বড্ড ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।
মাপতে মাপতে লিটনদা মজা করে বলল,”তাইলে তুমি অহন নুতন ডিজাইনই পর দেখতাসি।” আমি হাসলাম। বললাম “আর গাঁইয়া নই বলছ?”
সেদিন মাপ দিয়ে চলে আসার পর কলকাতার মাটি ছাড়ার আগে আরও দুদিন গেছিলাম সেই দোকানে। একদিন কাটপিস গুলো দিতে, আরেকদিন প্যান্টের ডেলিভারী নিতে। ট্রায়াল দেওয়ার আর সময় ছিলনা। কোনোবারই অবশ্য লিটনদার দেখা পাইনি। কাটপিস দেওয়ার দিন শুনলাম কোথায় জরুরী কাজে গেছে,আর ডেলিভারীর দিন শুনলাম অসুস্থ—ফ্ল্যাটেই শুয়ে আছে।
এ-কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু না,আরেকটু আছে। কলকাতায় আসার এরকম লম্বা ছুটি আমি আবার পেলাম বছর চারেক বাদে। আগেরবার এসেছিলাম একা,ফিরে গেছিলাম দুজনে। এবার সংখ্যাটা তিন। এই তৃতীয়জনের টলোমলো পায়ে হাঁটা আর আধো আধো বুলিতে মজে সবাই যখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত,আমি ফাঁক পেয়ে টুক করে একদিন পুরোনো পাড়ায় ঢুঁ মারলাম। দেখলাম বাটার জুতোর দোকানের উল্টো ফুটে সেই আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ী আর পাঁচতলা নার্সিং হোমের মাঝখানে ঝলমল করছে মনজিনিজ-এর কেক-পেস্ট্রির দোকান। খদ্দের উপচে পড়ছে। আর তার তিনশো মিটার দূরেই হয়েছে ‘প্যান্টালুনস’-এর নতুন শোরুম। বিশাল তিনতলা বস্ত্রবিপণী,ভেতরে লিফ্ট আর এস্ক্যালেটর। সেই দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে উর্দিপরা দারোয়ান সেলাম করে আর মেটাল ডিটেক্টর দেহ সার্চ করে। কেউ অক্ষয় তৃতীয়ার মিষ্টির বাক্স আর ক্যালেন্ডার বাড়িয়ে ধরে না। সেই দোকানে কোনো জ্যেঠু বা দাদা থাকেনা—থাকে শুধু বায়ার্স আর সেলার্স।
হ্যাঁ,সারা পৃথিবী জুড়েই আজ শুধু বায়ার্স আর সেলার্স।
*********************************************