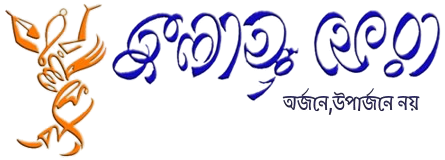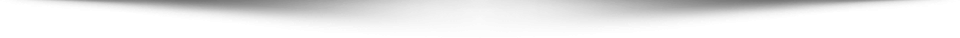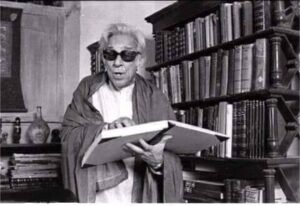
সিধুজ্যাঠার সঙ্গে সিনসিন্যাটিতে
সুজয় দত্ত
“তুমি কি মুকুল ধর নামক ছেলেটির বিষয়ে প্রশ্নটি করছ?”
প্রশ্নটি শুনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে তাকালেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে, সেটি তিনি পরিচালক মানিকদা–র নির্দেশে করে থাকতে পারেন,কিন্তু আমরা দর্শকরা হারীন্দ্রনাথের ওই কথাটি এবং পরবর্তী সংলাপগুলো শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একধরণের বিস্ময়মিশ্রিত সমীহ অনুভব করতে শুরু করি তাঁর অভিনীত চরিত্রটির প্রতি। তিনি গোয়েন্দাগিরিতে নামলে ওই পেশার অনেকেরই যে আর পসার থাকত না, ফেলুদারূপী সৌমিত্রের মুখে একথা শোনার পর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি যা বললেন তা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মনে তাঁর চরিত্রটিকে এক বইমুখো সবজান্তা জ্যাঠা থেকে একজন নিরাসক্ত প্রাজ্ঞ দার্শনিকে রূপান্তরিত করল।
তিনি অনেক কিছু করলেই অনেকের পসার থাকত না—সেকথা তিনি জানেন। জেনেও কিছুই করেননি তিনি জীবনে,শুধু মনের জানলা খুলে বসে আছেন যাতে বাইরের আলোবাতাস এসে মনটাকে তাজা রাখে। উচ্চাকাঙ্খা অর্থলিপ্সা যশলোভ এমন মানুষের কাছে লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পায় না,তাদের মেকি অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রদোষ মিত্রকে তিনি উপদেশ দেন, একজন গোয়েন্দা হিসেবে যদিও মানুষের মনের অন্ধকার দিকগুলো নিয়েই তার নিত্য কারবার,সে যেন নিজের মনকে কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে না দেয়। গোয়েন্দাপ্রবরকে সে–যাত্রা রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় সেই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির কাছে যে তার মনও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত।
এই বিশেষ চরিত্রটির নাম যে সিধু জ্যাঠা,তা ফেলুদা-প্রেমীদের অন্ততঃ না বলে দিলেও চলবে। সত্যজিত রায়ের প্রায় তিন ডজন ফেলুদা-কাহিনীর মধ্যে এই গল্পটিতে,অর্থাৎ ‘সোনার কেল্লা’-তেই চরিত্রটির প্রথম আবির্ভাব। ফেলুদার তারা রোডের (পরে রজনী সেন রোডের) আস্তানা থেকে অল্প কয়েক মিনিটের হাঁটা দূরত্বে সর্দার শংকর রোডের
এক সাদামাটা বাড়ীতে মগ্ন সাধকের মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁর। অকৃতদার। ঘরসংসার বলতে একরাশ বই–আলমারিতে,টেবিলে,তক্তপোশে। ভোরের নিয়মবাঁধা প্রাতঃভ্রমণ আর দুপুরের নাওয়া-খাওয়া ছাড়া দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে তাদের সঙ্গেই। বিভিন্ন পত্রিকা আর খবরের কাগজ পড়েন,নানারকম উল্লেখযোগ্য-অনুল্লেখযোগ্য খবরের পেপার-কাটিং সযত্নে রেখে দেন মোটা মোটা ফাইলে। সারাজীবনই কি তাঁর তাহলে এভাবেই কেটেছে? না,জানা যায় তিনি একসময় নানারকম ব্যবসাপাতি করেছেন, আর্থিক লাভলোকসানের মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্যের মোহে জড়িয়ে ওই জগতেই পাকাপাকিভাবে বাঁধা পড়ে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। কোনোরকম কাজেই নিজেকে বেঁধে ফেলতে চান না তিনি,সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমতো নিজের সময় খরচ করতে পারাটা তাঁর কাছে আর্থিক সচ্ছলতা বা পেশাগত নামযশের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। মৌলিক চিন্তাভাবনা করা, প্রথাগত পেশার গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে অন্য সকলের থেকে একটু আলাদা কিছু করা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও পরিসর দেওয়া–এগুলোই সবসময় তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় ওপরের দিকে। জীবিকানির্বাহ নয়।
এই সিধু জ্যাঠার কাছে কিন্তু ফেলুদা শুধু পুরোনো খবরের খুঁটিনাটি বা গোয়েন্দাগিরির জন্য দরকারি নানারকম তথ্যই পায় না। তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব আর বিবেকের উৎকর্ষবর্ধক নানা উপদেশও তিনি দিয়ে থাকেন,অর্থাৎ একধরণের ‘moral compass’-এর ভূমিকায়ও দেখা যায় তাঁকে। তিনি ফেলুদাকে স্মরণ করিয়ে দেন,গোয়েন্দাগিরির পেশায় বেশ কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে যেগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায়না। আর অপরাধ মানে শুধু মানুষ খুন নয়,দেশের নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের গা থেকে দুষ্প্রাপ্য মূর্তি খুবলে মোটা টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাচার করাও একইরকম ঘৃণ্য অপরাধ। গোয়েন্দাগিরি শুরু করার আগে পেশাটির ইতিহাস ভাল করে পড়ে নিলে কাজে আনন্দ আর আত্মবিশ্বাস–দুটোই যে বাড়বে,এমন পরামর্শ ফেলুদা সিধুজ্যাঠা ছাড়া আর কার কাছে পাবে? তপেশের পৈতৃক ভিটে যে গ্রামে,সেখানে তার বাবা-জ্যাঠাদের প্রতিবেশী ছিলেন এই ভদ্রলোক একসময়। তপেশের বাবারা তিন ভাই,যার মধ্যে মেজভাইয়ের ছেলে ফেলু আর তার ছোটকাকার ছেলে তপেশ। বয়সে ফেলুদার বাবার চেয়ে বড় হওয়ার দরুণই তিনি গ্রাম-সম্পর্কে ওর জ্যাঠা, ওকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। একটি গল্পে ফেলুদার ছোটবেলার এক প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন,সে একবার এয়ারগান দিয়ে একটা শালিক পাখী মেরে ওঁকে দেখাতে এনেছিল আর উনি তাকে স্নেহের বকুনি দিয়ে বলেছিলেন নিরীহ পশুপাখীর প্রতি আর কোনোদিন যেন সে এরকম নিষ্ঠুরতা না দেখায়। দুজনের সম্পর্কের বাঁধুনিটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পেশাগত ব্যস্ততার কারণে ফেলুদা অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ করতে না এলে প্রবীণ মানুষটির গলায় অভিমান ঝরে পড়ে,আর তার উত্তরে ফেলুদার মতো দৃঢ়চেতা, ঋজু চরিত্রের মানুষও ছাত্রসুলভ শ্রদ্ধাবনতঃ ভঙ্গীতে কৈফিয়ত দেয়। অবশ্য সেই অভিমান অন্যদের ওপরেও অল্পবিস্তর আছে তাঁর–বুড়ো মানুষটার কেউ তেমন খোঁজখবর রাখে না বলে। তবে তিনি কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য কারুর ওপর নির্ভরশীল নন। ফেলুদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মূলতঃ স্নেহ-ভালবাসার,প্রশ্রয়ের আর বন্ধুত্বের। অভিভাবকসুলভ শাসন বা বয়োজ্যেষ্ঠতার আনুগত্য দাবী নেই তার মধ্যে। নেই প্রজ্ঞার অহংকারও। তিনি যখন তাঁর দুই স্নেহের ভাইপোর সাধারণ জ্ঞানের বা পর্যবেক্ষণ-প্রখরতার পরীক্ষা নেন (যেমন সোনার কেল্লায় ফেলুদার কিংবা বাক্স রহস্যে তোপসের),তা-থেকে একধরণের ছেলেমানুষী মজাই ফুটে বেরোয়, কোনো উচ্চম্মন্যতা নয়।
গোয়েন্দাগিরিতে বাজিমাত করার সবরকম গুণই যে আছে সিধুজ্যাঠার মধ্যে, তার ঝলক মাঝেমাঝেই দেখা যায়। যেমন কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে রাস্তার পাশে চায়ের খুপরিতে চা খেতে খেতে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো সাংবাদিককে দেখেই বুঝে যান সে সিদ্দিকপুরের বিমান দুর্ঘনাস্থল থেকেই আসছে (সে নিজে সেকথা অস্বীকার করলেও), কারণ তার জুতোয় লেগে থাকা ছাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রখর স্মৃতিশক্তি আর অসাধারণ বিশ্লেষণক্ষমতার অধিকারী তিনি, জ্ঞানের বিশ্বকোষ তো বটেই। পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতেই পারে — ফেলুদার মতো একজন তুখোড় গোয়েন্দা হিরো থাকা সত্ত্বেও সত্যজিৎ তাঁর গল্পে এরকম একটি চরিত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছেন কেন? লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রটি নাহয় বৈপরীত্য আর হাল্কা বিনোদন (contrast and comic relief) সৃষ্টিতে কাজে লেগেছে, কিন্তু সিধু জ্যাঠা? ফেলুদা-কাহিনী যদি গত শতাব্দীতে লেখা না হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে লেখা হত,ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ঐরকম একটা চরিত্র আদৌ দরকার হতো কি লেখকের? এই দুটো প্রশ্ন পরস্পরসংযুক্ত, তাই উত্তরও একসঙ্গে খুঁজতে হবে। আসলে,ফেলুদার কাছে এই প্রবীণ ব্যক্তিটি শুধু অভিধান বা বিশ্বকোষ নন, তার চেয়েও বেশী কিছু। পুরোনো দিনের সহজ-সরল, নির্লোভ আর সত্যনিষ্ঠ জীবনদর্শনের প্রতীক,সাবেক মূল্যবোধের প্রতীক। আজকাল মুঠিফোনের দু-চারটে বোতাম টিপলেই সারা পৃথিবীর সমস্ত তথ্য হয়তো তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়,পুরোনো পেপারকাটিং-এর ফাইল রাখার বা গাদা গাদা বই পড়ার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু নতুন শতাব্দীতে মানুষের দ্রুত-বদলাতে-থাকা জীবনদর্শন যখন অন্ধভাবে ভোগবাদ আর সংকীর্ণ স্বার্থপরতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ও যখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে,সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর দৌরাত্ম্যে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক বন্ধনের সুতোগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে–তখন একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে সিধুজ্যাঠাকে আমাদের বড্ড দরকার। আরও অনেক বেশী করে দরকার।
সোনার কেল্লায় প্রথম আবির্ভাবে সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে কানাডা–ফেরত নামকরা প্যারাসাইকোলোজিস্ট ডঃ হেমাঙ্গ হাজরার পূর্বজীবনের একটা ঘটনার হদিশ দিয়েছিলেন,যাতে এলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ) প্রতারক ভবানন্দ আর তার চ্যালার কুকীর্তির কথা এবং ডঃ হাজরার সেখানে গিয়ে মুখোশ খুলে দেওয়ার কথা বলেন তিনি, যদিও পাঠক বা দর্শক তখনও জানেন না এই জুটিই গল্পের খলনায়ক হতে চলেছে। এলাহাবাদে তাদের ঠগবাজীর ব্যবসাকে তিনি তুলনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীতে ফ্রাঞ্জ আন্তন মেসমার–এর (যিনি জৈব চৌম্বকশক্তি আর মেসমেরিজম এর প্রবক্তা—মেসমেরিজমই পরবর্তীকালের হিপ্নোটিজম বা সম্মোহনবিদ্যা) বুজরুকির কারবারের সঙ্গে। সেই প্রথম আমরা পরিচয় পাই সিধুজ্যাঠার জ্ঞানের পরিধির। এরপর বাক্স রহস্য গল্পে জানা গেল তিনি পৃথিবীবিখ্যাত সংবাদপত্র লন্ডন টাইমসের নিয়মিত পাঠক। কারণ সেখানে শম্ভূচরণ বসু নামক এক বাঙালী ডাক্তারের (যিনি একইসঙ্গে একজন শিকারী ও পর্যটক) লেখা এবং এক বিলেতি প্রকাশকের ছাপা “Terrors of Terai” বইটির ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছিল,যা তিনি পড়েছিলেন। সেই শম্ভূচরণেরই তিব্বত নিয়ে লেখা আরেকটি অপ্রকাশিত ভ্রমণকাহিনীর পান্ডুলিপি চুরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্প। পাণ্ডুলিপিটি হাতে পাওয়ার ও পড়ে দেখার জন্য সিধুজ্যাঠা এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে বেশ ভালোরকম দাম দিয়ে সেটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেন। উদ্দেশ্য সেটাকে বই হিসেবে ছাপিয়ে অর্থলাভ বা যশোলাভ নয়, নিজের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে বঢ়াই করাও নয়—স্রেফ লেখকের নিজের হাতের লেখা থেকে তাঁর স্বভাবপ্রকৃতি আর চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাবে জানা।
গোরস্থানে সাবধান গল্পটিতে দেখা যায় ফেলুদা তার প্রিয় জ্যাঠার শরণাপন্ন হয়েছে পুরোনো যুগের কলকাতার এক অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ খবরাখবর নিতে। সেই ইতিহাস বলতে গিয়ে লখনৌ–এর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের হেঁশেল অবধি পৌঁছে গেলেন জ্যাঠা। ব্রিটিশ ভারতের ইতিবৃত্তে তাঁর এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে আমরা আর নতুন করে অবাক হই না। কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে ব্যাপারটা একটু উল্টে গেল। এবারে আর ফেলুদা–তোপসে সিধুজ্যাঠার কাছে নয়,তিনি নিজেই প্রবল বৃষ্টিবাদলা উপেক্ষা করে হাজির ফেলুদার বাড়ী। কারণ আর কিছুই নয়,আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রের অমূল্য ভাস্কর্য চোরাচালানকারীদের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হওয়া–সংক্রান্ত একটি খবরে মনের উদ্বেগ আর আবেগ চেপে রাখতে না পেরে ছুটে এসেছেন সেই বিষয়ে কথা বলতে। শুধু কথা নয়,ফেলুদার সঙ্গে সশরীরে গিয়েই হাজির হলেন একটি বিমান–দুর্ঘটনাস্থলে, যার নিহত যাত্রীদের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতীয় ভাস্কর্যের আগ্রহী ক্রেতা এক বিদেশীর। এই গল্পে দেশের প্রাচীন শিল্পকলা চোরাপথে রফতানির ব্যবসা নিয়ে তাঁর তীব্র ঘৃণা ছাড়াও যেটা প্রথমবারের জন্য সামনে এল, তা হল তাঁর সুগভীর শিল্পবোধ। তাঁর মতে,মানুষ শিক্ষিত হলেই যে শিল্পকলার মূল্য বুঝবে—এমন নয়। শিল্পের প্রতি অনুরাগের জন্য চাই শিল্পবোধ।
এরপর গোলোকধাম রহস্য গল্পটিতে আমেরিকা–ফেরত জৈবরসায়ন গবেষক নীহার দত্তের বাড়ীর একটি ঘটনায় তদন্তের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ফেলুদা তাঁর অতীত সম্বন্ধে জানতে সিধুজ্যাঠার কাছে গিয়েই প্রথম জানতে পারে ভদ্রলোক একা গবেষণা করতেন না, তাঁর এক বাঙালী সহকারী ছিল। এই সহকারীটিকে ঘিরেই পরে গল্পের রহস্যজাল ঘনীভূত হয়। সিধুজ্যাঠা পরে কাগজপত্র ঘেঁটে ফেলুদাকে হদিশ দেন নীহারবাবু দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দেশে ফিরে আসার পর সেই সহকারীটি অন্য এক দেশে কী অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। গোলাপী মুক্তো রহস্যে ফেলুদাকে তার জ্যাঠা সাবধান করে দেন মূল্যবান রত্নের এক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে অসাধারণ কথাটি বলেন,তা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,মানুষকে ভাল বা খারাপ বলে মোটা দাগে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বৃথা, কারণ মানুষের মন তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও আলো–আঁধারিতে ধূসর। তাই গোয়েন্দাগিরিতে কারো সম্বন্ধে কোনো বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে না এগিয়ে খোলামনে নমনীয় বিচারবুদ্ধি নিয়ে এগোনোই ভাল। এই গল্পগুলি ছাড়া হত্যাপুরী নামক কাহিনীটিতে সিধুজ্যাঠার উপস্থিতি না থাকলেও উল্লেখ আছে তাঁর সংগ্রহে থাকা কিছু অতি পুরোনো পুঁথি প্রসঙ্গে।
ফেলুদার গল্প সব বয়সের পাঠক বা দর্শকের কাছে সমান জনপ্রিয় হলেও সত্যজিৎ ওগুলি লিখেছিলেন মূলতঃ কিশোর সাহিত্য হিসেবে। ফেলুদা আর সিধুজ্যাঠা—দুজনকেই কিশোর–কিশোরীদের কাছে দুই আদর্শ চরিত্রের রোল–মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন লেখক। আর তা করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের এবং রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যদের বেশ কিছু চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন এই দুজনের ওপর। পরে এই গল্পগুলির চলচ্চিত্রায়ণের সময় ফেলুদার চরিত্রটি যেমন সৌমিত্র,সব্যসাচী,আবির,টোটা, ইন্দ্রনীল প্রমুখ প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় অভিনেতারা করেছেন বিভিন্ন সময়ে,তেমনি সিধুজ্যাঠার চরিত্রটিও অনেক হাত ঘুরেছে। সোনার কেল্লায় হারীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু। তারপর মনোজ মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্য ভট্টাচার্য্য,অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চরিত্রটিকে স্মরণীয় ও উজ্জ্বল করে রেখেছেন। প্রতিটা ছবিতেই এই স্থিতধী,নিমগ্ন,প্রজ্ঞালোকিত প্রবীণকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় আমাদের মন বলে ওঠে,”দেখি আপনার পায়ের আঙুলগুলো”।
এহেন সিধুজ্যাঠার সঙ্গে হঠাৎই কয়েক বছর আগে দেখা সিনসিন্যাটি-তে। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। সিনসিন্যাটি হল আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চহ্রদের চতুর্থটির (লেক এরি) তীরবর্তী রাজ্য ওহায়ো-র তৃতীয় বৃহত্তম শহর। তেরো বছর আগে এই ওহায়ো রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসার পর একবার সিনসিন্যাটি গেছিলাম একটা পেশাগত কাজে। ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিন্যাটির ঝাঁ-চকচকে ক্যাম্পাসে কয়েকজন পরিচিত ভারতীয়র সঙ্গে একটা বেশ বড়সড় ক্যাফেটেরিয়ায় খেতে গেছি দুপুরে, খেতে খেতে জমিয়ে আড্ডা মারছি,কথাপ্রসঙ্গে ভারতের নানা বিষয় উঠে আসছে। আমার ভোজনসঙ্গীরা অর্থনীতিবিদ,তারা নব্বইয়ের দশকে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর তার সাড়ে তিন দশক পর আজকের নতুন ভারত–কী হতে পারতো,কী হল না–ইত্যাদি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে তুলতে হঠাৎ একটা প্রশ্নে আটকে গেল। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যখন উদারনীতি ঘোষণা করছেন, তখন দেশের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? আমারও ঠিক মনে পড়ছিল না–আন্দাজে বললাম,বোধহয় শংকর দয়াল শর্মা। বন্ধুরা “রাইট রাইট” করে উঠতেই কোথা থেকে একটা গম্ভীর গলা ভেসে এল–“রং। রামা সোয়ামি ভেঙ্কটা রামান”। আমরা চমকে তাকিয়ে দেখি পিছনের টেবিলে একা বসে থাকা এক লোলচর্ম আমেরিকান বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লম্বা সাদা দাড়ি, চোখে মোটা চশমা, সামনে কফি-স্যান্ডউইচের পাশে একটা আধখোলা বই। অমর্ত্য সেনের “দ্য আইডিয়া অফ জাস্টিস”। আমেরিকানরা সাধারণতঃ অন্যের কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে না। আমরা “ওহ, থ্যাংক ইউ” গোছের কিছু একটা বলার আগেই ওঁর ঠোঁটদুটো (এবং সেই সঙ্গে দাড়ি) আবার নড়ে উঠল,”অ্যান্ড ইন কেস ইউ আর ইন্টারেস্টেড,দ্য স্পীকার অফ ইয়োর পার্লামেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ শিভা রাজা প্যাটিল”। আমেরিকানরা একটা বিস্ময়সূচক শব্দ খুব ব্যবহার করে–“ওয়াও”। আমার মুখ থেকেও নিজের অজান্তে বেরিয়ে এল ওটা। ইনি তো যে-সে আমেরিকান নন ! চারজন উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়কে ক্যাবলা বানিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদেরই দেশের রাষ্ট্রপতি আর লোকসভার স্পীকারের নাম? লালমোহন গাঙ্গুলির ভাষায় মনে মনে বললাম, এঁকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে। ঝুলে পড়ব নাকি এঁর সঙ্গে?
এবং পড়লামও। ডঃ সিডনি স্পেনসার জেটসন-এর সঙ্গে সেই আচমকা প্রথম আলাপের পর অনেক বছর ধরে বহুবার ফোনাফুনি, ইমেল চালাচালি আর সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। সিনসিন্যাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন,এখন (অর্থাৎ সেই প্রথম আলাপের কয়েক বছর পর) অবসর নিয়ে এমেরিটাস প্রফেসর। একসময় গবেষণার বিষয় ছিল ওরিয়েন্টাল ডেভেলপিং ইকোনমিজ মানে প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি। ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। কিন্তু ওই জন্য নয়, আমি ওঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেলাম অন্য একটা কারণে–সারা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে এরকম অবিশ্বাস্য লেভেলে খুঁটিনাটি খবর রাখাটা আমি কোনো দেশে আমার চেনাশোনা কারো মধ্যে কখনও দেখিনি। ইথিওপিয়া বা আইভরি কোস্ট-এর কফির সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান কফির তফাৎ কি, বেহালার ছড় কেন পের্নাম্বুকো কাঠ দিয়ে তৈরী হয়,সুমেরু অঞ্চলের বল্গাহরিণ-দের মূল খাদ্য লাইকেনের পুষ্টিগুণ কিরকম, উষ্ণ সাগরজলের দুই বিশালকায় স্তন্যপায়ী প্রাণী ম্যানাটি আর ডুগং আজ লোপাট হয়ে যেতে বসেছে কেন–ইত্যাদি অজস্র প্রশ্নের (যেগুলো কিনা প্রশ্ন হিসেবে আমার মাথাতেই আসেনি কখনো) তাৎক্ষণিক উত্তর তাঁর নখের ডগায়। ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে বের করতে হতো না। যখন সারা পৃথিবী করোনা অতিমারীর কবলে গৃহবন্দী,কয়েকবার ভিডিও চ্যাট হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। আমাকে উনি বেশ পছন্দ করতেন–তার কারণ হিসেবে একবার বলেছিলেন যে আমি নাকি খুব ভাল “লিসনার”,আর কেউ নাকি এত ধৈর্য্য ধরে ওঁর কথা মন দিয়ে শুনতে চাইত না। তাই আমাকে নিজের জীবনের প্রায় আট দশকের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন, তার মধ্যে অধ্যাপনা বা গবেষণা-সংক্রান্ত পরামর্শও থাকত। ওই ভিডিও চ্যাটগুলোর সময় দেখতাম একটা ছোট দু-কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন এই অকৃতদার প্রফেসর–শুধু রাশি রাশি বই পরিবৃত হয়ে। কম্পিউটার একটা ছিল,কিন্তু তাতে দিনের খুব বেশী সময় কাটাতেন বলে কখনওই মনে হয়নি।
আচ্ছা, আমি তখন থেকে অতীতকাল ব্যবহার করে যাচ্ছি কেন তাঁর কথা বলার সময়? কারণটা বড় বেদনার আমার কাছে। ২০২১ এর ফেব্রুয়ারীতে কোভিড-এর মারণ-সংক্রমণ ছিনিয়ে নিল তাঁকে আমাদের সকলের থেকে। শেষ দিনকটা কেটেছিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে একাকী,নিঃসঙ্গভাবে। এরপর একবার সিনসিন্যাটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে গেলাম যখন একটা সেমিনার দিতে, একা গিয়ে বসেছিলাম সেই ক্যাফেটেরিয়ায়। জানলার পাশের সেই টেবিলটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল,সিডনি জেটসন আর সিধুজ্যাঠা–এই নামদুটোয় কী মিল,তাই না?
************************************

সুজয় দত্ত বর্তমানে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (statistics) অধ্যাপক। তিনি কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্য তাঁর সৃজনশীলতার মূল প্রকাশমাধ্যম,সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। ছোটগল্প,বড় গল্প,প্রবন্ধ ও রম্যরচনার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতাও লেখেন তিনি। এছাড়া করেছেন বহু অনুবাদ–হিন্দি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে। তিনি হিউস্টনের “প্রবাস বন্ধু” ও সিনসিনাটির “দুকুল” পত্রিকার সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত ‘বাতায়ন’ পত্রিকাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই পত্রিকাগুলি ছাড়াও ‘অপার বাংলা’ ও ‘গল্পপাঠ’ নামক ওয়েব ম্যাগাজিন দুটিতে,নিউজার্সির ‘আনন্দলিপি’ ও ‘অভিব্যক্তি’ পত্রিকা দুটিতে,কানাডা থেকে প্রকাশিত ‘ধাবমান’ পত্রিকায়,ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পূজাসংকলন ‘মা তোর মুখের বাণী’ তে,ভারতের মুম্বাই থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতা পরবাসে’ রয়েছে তাঁর লেখা। কলকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজসেবী সংস্থা ‘পোয়েট্স ফাউন্ডেশন’-এর তিনি অন্যতম সদস্য। সম্প্রতি নিউ জার্সির “আনন্দ মন্দির” তাঁকে “গায়ত্রী গামার্স স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারে” সম্মানিত করেছে। সাহিত্যরচনা ছাড়া অন্যান্য নেশা বই পড়া, দেশবিদেশের যন্ত্রসঙ্গীত শোনা এবং কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো।