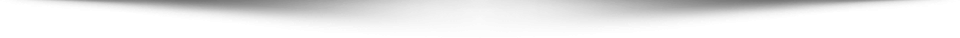ভারত-বাংলাদেশের মাছ ধরার উৎসব ও মৎস্যমেলাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য
সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথা মেনে বছরের একটি দিনে মাছ ধরা বা মৎস্যমেলা (Fish Fair) – র উৎসব উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার বলেই মনে হয়। ভারত ও বাংলাদেশের নানা স্থানে এই ধরনের উৎসব হয়। সর্বত্রই এই উৎসব কোথাও ফসলের বীজ বপনের পর, কোথাও বা নতুন ফসল গোলাজাত করার সময়ে কোনো একটি দিন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। যেহেতু জল নিজেই উর্বরতার প্রতীক, তাই মাছ-ও জলজ প্রাণী বলে জীবন ও উর্বরতার প্রতীক। মাছের ডিমে থাকে জন্মলাভের সম্ভাবনাময় অসংখ্য পোনা। তাই সন্তানবতী নারীর প্রতীক রূপেও মাছকে উর্বরতার প্রতীক ও ‘শুভদ্যোতক’ গণ্য করা হয়। সেই কারণে বিভিন্ন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে মাছ ব্যবহৃত হয়। আলপনায় মাছ আঁকা হয়। কাঁথায় মাছের নকশা করা হয়। আবার অনেকের মতে মাছ লৈঙ্গিক প্রতীক (phallic symbol) হিসাবেও উর্বরতা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এ প্রসঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে প্রথম পদার্পনের দিন বাংলার নববধূদের হাতে ল্যাটা মাছ ধরানোর তাৎপর্য সহজবোধ্য। একইরকমভাবে ‘মৎস্য মারিব খাইব সুখে’ নিছক এই প্রবৃত্তি থেকেই নয়, আহার্য হিসেবে মাছ গ্রহণ করলে শস্য-সন্তান-সম্পদ-সমৃদ্ধি – সবই মিলবে এমন কল্পনা থেকেই বাৎসরিক একটা মাছ ধরার উৎসব বা মাছ মেলার আয়োজন করা হয়। বহু জায়গায় মাছ ধরার পর রান্নাশেষে নিজেরা খাওয়ার আগে মন্দিরের দেবতা বা পিতৃপুরুষের ‘আত্মা’-র উদ্দেশে তার কিয়দংশ ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। এক্ষেত্রে জাদুবিশ্বাসমূলক কৃত্যানুষ্ঠান কালক্রমে ধর্মানুষ্ঠানে পরিণতি লাভ করেছে বলা যায়।
গ্রাম বাংলার আবহমান লোক ঐতিহ্যের অন্যতম ‘পলো বাওয়া’। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও এই উৎসব পালন করেন। শীতের শুরুতে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোর অর্থাৎ ছোটো ছোটো কম গভীরতার নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়ের জল শুকিয়ে হাঁটু বা কোমর পর্যন্ত নেমে গেলে সেগুলোর মিষ্টি জলে প্রচুর দেশীয় প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সেই সময়েই ‘পলো বাওয়া’ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার গ্রামীন জনপদগুলোতে কিশোর, যুবক ও বয়স্ক পুরুষেরা তখন ‘ঝপ ঝপাঝপ পলো বাও / মজার মজার মাছ খাও’ স্লোগান দিতে দিতে সদলবলে মাছ ধরার জন্য জলে নেমে পড়েন। প্রতিটি গ্রামেই উৎসবের দিন-ক্ষণ আগে থেকেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়। সেই নির্ধারিত দিনে ও বিশেষ সময়ে শয়ে শয়ে মাছ শিকারী নিজের নিজের ‘পলো’ নিয়ে নির্দিষ্ট জলাশয়ে হাজির হন। পলো হল বাঁশের কাঠিকে সরু তার বা নাইলনের সুতো দিয়ে বিশেষ কায়দায় বেঁধে গোলাকৃতি পাখির খাঁচার আদলে তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম। এর ওপরের দিকে একটা ছোটো খোলা মুখ থাকে। নিচের দিকও খোলা। এই ফাঁদে মাছ একবার ঢুকে পড়লে আর বেরোতে পারেনা। যাদের কাছে পলো বা মাছ ধরার অন্য কোনো সরঞ্জাম থাকেনা, তাঁরা হাত দিয়েও মাছ ধরেন। এই উৎসবে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই। মাছ ধরার জন্য কারো কাছে কোনো ‘ফি’ নেওয়া হয়না। কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং কোথাও কোথাও পেশাদার জেলেরাও এতে সামিল হন। সারিবদ্ধভাবে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে জলে নেমে পলো ফেলতে ফেলতে তাঁরা এগোতে থাকেন। মাছ শিকার দেখতে পাড়ে ভিড় জমানো হাজার হাজার জনতা হাততালি দিয়ে ও জোরে জোরে চিৎকার করে তাঁদের উৎসাহিত করতে থাকেন। পলো ফেলার শব্দ ও তুমুল হট্টগোলে মাছগুলো ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে। অনেক মানুষ একসঙ্গে মাছ ধরতে নামায় জল ঘোলা হয়ে যাওয়ার কারণে মাছ ভেসেও ওঠে। তখন সেগুলোর কোনো-না-কোনোটিকে পলো দিয়ে আটকে ফেলা হয়। তারপর পলোর ওপর দিকের খোলা অংশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাছটি ধরে সেটিকে জালের থলি বা দড়িতে বেঁধে নেওয়া হয়। কে কত বেশি আর কত বড় মাছ ধরতে পারে তা নিয়ে শখের মাছ শিকারীদের মধ্যে চলে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা। সকালে সূর্য ওঠার সময় থেকে শুরু হয়ে যায় মাছ ধরা। চলে প্রায় বিকেল পর্যন্ত। জল থেকে তাঁরা উঠে আসার পর সমবেত দর্শনার্থীদের মধ্যে মাছ দেখার হিড়িক পড়ে যায়। মাছ দেখে আনন্দে মাতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা। ধরা পড়া মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, কালবোস, আড়, বাঘা আড়, বোয়াল, শোল, টাকি, গজার, কই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিজেদের পরিবারে খাওয়ার চাহিদা মিটিয়ে বাকি মাছ স্থানীয় হাটবাজারে বেচে দেন মাছ শিকারীরা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ শুঁটকি করেও সংরক্ষণ ও বিক্রি করা হয়। অনেক জায়গায় পাইকারি মৎস্য ব্যবসায়ীরা চলে আসেন তাঁদের কাছ থেকে মাছ কিনতে। সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় চালান হয়।বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল ‘চলনবিল’। যা নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। অনেক বড় বড় বিলের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে চলনবিল। বহু নদী চলনবিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিলে ‘পলো বাওয়া’ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। স্থানীয় ভাষায় মাছ শিকারীদের বলা হয় ‘বাউৎ’। তাই এই অঞ্চলে এটি ‘বাউৎ উৎসব’ নামেও পরিচিত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চলনবিল অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জের তাড়াশ ও রায়গঞ্জ উপজেলা; নাটোরের নলডাঙা, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম ও লালপুর উপজেলা এবং পাবনার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার নদনদী ও খালবিলগুলোয় এই উৎসবের ধুম পড়ে যায়। চলনবিলের গুমানি নদীতে পলো সহ বিভিন্ন দেশীয় উপকরণ দিয়ে দল বেঁধে মাছ ধরার দৃশ্য দেখার মতো হয়। নলডাঙার হরিদাখলসি গ্রামের কুড়িল বিলে, বড়াইগ্রামের চিনাডাঙার বিলে, লালপুরে বিলমাড়িয়া এলাকায় নওসারা সুলতানপুরে পদ্মার বুকে, চাটমোহরের খলিশাগাড়ি ও ডিকশি বিলে এবং চাটমোহর-ভাঙ্গুড়ার রুহুল বিলেও উৎসব জমে ওঠে।
বাংলাদেশের আর যেসব জেলা-উপজেলায় এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব উদ্যাপিত হয়, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখনীয়। নওগাঁর নিয়ামতপুরে শিব নদী ও হরিপুর বিল এবং বদলগাছীর ছোটো যমুনা নদী; চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের নানা জলাশয়; রাজশাহীর বাঘার আড়পাড়া বিল; মাগুরার সদর উপজেলা সহ শ্রীপুর, মহম্মদপুর ও শালিখার বিভিন্ন এলাকার জলাশয়; নড়াইলে ইছামতী বিল, চাচুড়ির বিল, কাড়ার বিল, নলামারা বিল সহ অসংখ্য বিল; পটুয়াখালীর দশমিনার খাল-বিল; ফরিদপুরে চরভদ্রাসনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ভুবনেশ্বর নদী; টাঙ্গাইলের সখীপুরে শাইল-সুন্দর খাল ও বাসাইলের আতিলা বিল সহ কয়েকটি বিল; গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মেদী আশুলাই এলাকার আলেয়া বিল; নরসিংদীর রায়পুরার খলিলাবাদ গ্রামের বিল ও শিবপুরের আড়িয়াল খাঁ নদী; কিশোরগঞ্জের নিকলির নদনদী, খালবিল ও হাওড়; নেত্রকোণার মদনে মগড়া নদী; সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ডাহুকা নদী; সিলেটের বিশ্বনাথের মাদাই বিল ও গোয়াহরি বিল এবং জৈন্তাপুরের ভাড়ার ডুয়ার বিল; মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ধলাই নদী, জুড়ীতে কন্টিনালা নদী ও শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওড় পলো উৎসবের সুপরিচিত ক্ষেত্র।
কিন্তু দিন দিন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে জলাশয়গুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র কমে যাওয়া, চাষের জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এবং কলকারখানার বর্জ্য জলে মেশা, নিষিদ্ধ ঘোষিত জালের অবাধ ব্যবহার, বর্ষাকালে প্রজনন মরশুমে ডিমওয়ালা মা-মাছ সহ ছোটো ছোটো মাছ সব ছেঁকে তুলে ফেলা ইত্যাদি নানা কারণে দেশীয় প্রজাতির অনেক মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ফলে পলোতে এখন মাছ আগের চেয়ে অনেক কম ওঠে। শোনা যায় আগে এই উৎসবে এক একজন এত মাছ ধরতেন যে সেগুলো দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে ঘরে ফিরতেন। মাছ কমে যাওয়ায় এবং সেইসাথে অধিকাংশ জলাশয় ইজারা দেওয়ায় পলো বাওয়া উৎসবে এখন অনেকটা ভাটা পড়েছে।
তবে পলো বাওয়ায় মেলা মাছ মিলুক আর না মিলুক, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’ পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে এখনও প্রতি বছর ‘মাছ মেলা’-র আয়োজন করে থাকে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দূর-দূরান্ত থেকে আসা লাখো মানুষের ঢল নামে শতাব্দী প্রাচীন মেলাগুলোতে। বিভিন্ন প্রজাতির বৃহদাকৃতির মাছ মেলার আকর্ষণ। দেশি বিলুপ্তপ্রায় মাছ-ও থাকে। স্থানীয় বিভিন্ন খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, নদ-নদীর মাছ নিয়ে আসেন মৎস্যজীবী ও মৎস্যব্যবসায়ীরা। মৎস্য খামার থেকেও মাছ আসে। লাখ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হয়। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সবাই মেলা থেকে মাছ কেনার চেষ্টা করেন। মেলাকে কেন্দ্র করে কৃষিজাত পণ্য, গৃহস্থালীর সামগ্রী, কাঠ বা স্টিলের আসবাবপত্র, শিশুদের খেলনা, ফল-সবজি, মিষ্টি সহ বিভিন্ন পসরার কয়েকশো দোকানপাট বসে। নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস, পালা গান, বাউল গান ইত্যাদি বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকে। মেলার সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীরা দেশে এসে থাকেন। ঘরে ঘরে মেয়ে-জামাই সহ আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। শ্বশুরেরা মেলায় আসেন জামাইদের জন্য মাছ কিনতে। জামাইরাও মেলা থেকে মাছ কিনে শ্বশুরবাড়ি যান। কে সবচেয়ে বড় মাছ কিনে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে জামাইদের মধ্যে চলে এক নীরব প্রতিযোগিতা। নতুন ধানের চালের ভাতের সাথে মেলায় কেনা হরেক রকমের মাছের পদ দিয়ে জামাই আপ্যায়ন করা হয় বলে এই মেলাকে কোথাও কোথাও ‘জামাই মেলা’-ও বলে। সেখানে মূল মেলার পরের দিন একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় ‘বউ মেলা’। আগের দিন মাছ কাটা, ধোয়া, রান্না,পরিবেশন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাড়ির মেয়ে-বউরা মেলায় যাওয়ার সময় পাননা। তাঁদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। ‘বউ মেলা’-র দিন তাঁরা মেলায় গিয়ে নিজেদের খুশিমতো কেনাকাটা করেন।
নবান্ন উপলক্ষ্যে অগ্রহায়ণের প্রথম দিন বাংলাদেশের জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার পাঁচশিরা বাজারে, বগুড়ার নন্দীগ্রাম ও দুপচাঁচিয়া উপজেলার বিভিন্ন বাজারে এবং শিবগঞ্জ উপজেলার উথলী বাজারে মাছের মেলা বসে। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মাছের মেলা হয় মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় কুশিয়ারা নদীর তীরে শেরপুর নামক স্থানে এবং শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন মাছবাজারে। শেরপুরের মেলাটি আগে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ‘মনুমুখ’ নামক স্থানের একটি বাজারে হত। আনুমানিক দেড়শো বছর আগে পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে এই মেলা শুরু করেন স্থানীয় জমিদার মথুর বাবু। কুশিয়ারার ভাঙনে সেই বাজার নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় মেলাটি শেরপুরে স্থানান্তরিত হয়। নরসিংদীর মনোহরদীর দরগাহ বাজারের মাছ মেলা, গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বিনিরাইলের মাছ মেলা, হবিগঞ্জের পইলের মাছ মেলাও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে হয়। নতুন ফসল ওঠার আনন্দে বাংলাদেশে আরো অনেক স্থানেই মাছের মেলা হয়। শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বগুড়ার ধুনট উপজেলার ‘বকচর মাছের মেলা’-রও নাম আছে। মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের বুধবার আয়োজিত এই মেলাকে ‘মাছ-মিষ্টির মেলা’-ও বলা হয়। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত মাছের মেলা সম্ভবত বগুড়ার ‘পোড়াদহ মাছের মেলা’। বগুড়ার গাবতলী উপজেলার মহিষাবান ইউনিয়নের গোলাবাড়ী বাজার সংলগ্ন ইছামতী নদীর তীরবর্তী পোড়াদহে মাঘ মাসের শেষ বুধবার মাছ মেলা বসে। ‘সন্ন্যাসী পূজা’ উপলক্ষ্যে প্রায় চারশো বছর ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিশালাকায় মাছ ছাড়াও এ মেলায় দর্শনার্থীদের কাছে আরেক আকর্ষণ বিশাল আকৃতির ‘মাছ-মিষ্টি’।
এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক ভারতের দিকে। ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম ও মফস্বলের মানুষেরা হঠাৎ শখ করে দলবদ্ধভাবে পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়ে মাছ ধরতে গেলেও সেখানে বছরে নিয়ম করে একদিন মাছ ধরা উৎসব পালনের খবর আমার অন্তত জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি মাছের মেলা হয় যা পাঁচশো বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। কলকাতার কাছেই হুগলি জেলায় দেবানন্দপুরের কৃষ্ণপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটে পৌষ সংক্রান্তির পরদিন (১ লা মাঘ) এই মেলা হয়। এটি ‘উত্তরায়ণ মেলা’ নামে পরিচিত। এখানে সেদিন শুধু হরেক প্রজাতির মাছ কেনাবেচাই হয়না। মাছ কিনে মেলার মাঠের পাশের আমবাগানে তা রান্না করে বনভোজনে বসে পড়েন অনেকে। মেলায় বসা কিছু দোকানেও ক্রেতাদের ফরমায়েস মেনে তৈরি হয় বিভিন্ন মাছের নানা সুস্বাদু পদ। মেলায় মিষ্টি, ফলমূল, শাকসবজি সহ অন্যান্য পসরার দোকানও থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেলায় বিকিকিনি চলে। মেলা সংলগ্ন শ্রীপাটের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে দিনভর চলে পুজো-আর্চা ও নামসংকীর্তন। নিরামিষভোজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীপাটে মাছের মেলার প্রচলন কীভাবে হল তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সে সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তা হল – ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে এখানকার ‘মজুমদার’ উপাধিপ্রাপ্ত জমিদার বংশের সন্তান রঘুনাথ দাস মাত্র সতেরো বছর বয়সে ঘরসংসার ছেড়ে নীলাচলে (পুরী) গিয়ে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন ‘ষড় গোস্বামী’-র অন্যতম। ষোলো বছর নীলাচলে থাকার পর তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। একমাত্র সন্তান ঘরে ফিরে আসার খুশিতে তাঁর বাবা গোবর্ধন দাস মজুমদার গ্রামের সব লোককে মাছ-ভাত খাওয়ান। সেই থেকেই প্রতি বছর ১ লা মাঘ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রামে ফিরে আসার দিনটিকে স্মরণ করে এই মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে জনশ্রুতি যাই থাকুক, এটি কৃষিকেন্দ্রিক পৌষালি উৎসবেরই অঙ্গ। ভারতের অন্যত্র অনেক স্থানে সম্প্রতি সরকারি উদ্যোগে বার্ষিক মাছের মেলা হয়ে থাকে। যেমন, মণিপুরে মেইতি জনগোষ্ঠীর ‘নিঙ্গল চকৌবা’ উৎসব উপলক্ষে এ ধরনের মেলা হয়। কিন্তু ভারতের আর কোথাও কৃষ্ণপুরের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মাছের মেলার হদিশ এখনও পাইনি।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ( যে-যে রাজ্যে প্রধান খাদ্যই হল ভাত) কৃষি উৎসবের অনুষঙ্গ হিসাবে বছরে একবার মাছ ধরার উৎসব পালনের প্রথা প্রচলিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে আসামে ‘মাঘ বিহু’ বা ‘ভোগালি বিহু’-র প্রথম দিনে (উরুকার দিনে) নির্দিষ্ট পুকুর, খাল বা অন্য কোনো জলাশয় থেকে সবাই একত্রে মাছ ধরেন। রাতে সেই মাছ রান্না করে খাওয়া হয়। আসামের পানবাড়ির গোরোইমারী লেক-এ ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে মাছ ধরার বড় উৎসব হয়। অরুণাচল প্রদেশের লেপারাদা জেলায় বসবাসকারী গালো জনজাতিদের প্রধান কৃষি উৎসব ‘মপিন’ মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় একদিন দলবদ্ধভাবে তাঁরা ইগো নদীতে মাছ ধরতে যান। মণিপুরের কামজং ও উখরুল জেলায় কৃষিজীবী তাংখুল নাগা জনজাতির লোকেরা এপ্রিল-মে মাসে ফসলের বীজ বপনের পর ভালো ফসলের কামনায় তাঁদের বৃষ্টির দেবীকে আবাহন করতে ‘খৈরি কাসাও’ বা ‘ইয়েই থাবা’ উৎসব করেন। মূলত এটি মাছ ধরারই উৎসব। নাগাল্যান্ডের ফেক জেলার বিভিন্ন গ্রামের চাখেসাং নাগারা প্রতি বছর ফসল কাটার পর ভালো ফসল প্রাপ্তির জন্য তাঁদের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশীর্বাদ পেতে মাছ ধরার উৎসব ‘খিলিনিয়ে’ পালন করেন। চাষের জমিতে জমে থাকা জলের মধ্যে থেকে মাছ ধরা হয়। সেই মাছ তাঁরা ঘরে আনেন না। চাষের জমিতে বসেই তা রান্না করে নতুন ধানের চালের ভাত দিয়ে খান। নাগাল্যান্ডের ওখা জেলার সুঙ্গিকি গ্রামের লোথা এবং জুনহেবোতো জেলার ফিলিমি গ্রামের সুমি নাগারা প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে দোয়াং নদীতে মাছ ধরতে যান। তাঁদের সঙ্গী হন চুকিতং, কইও, রোতোমি, আকুহাইতো ও খ্রিমিতো গ্রামের লোথা ও সুমি নাগারা। মাছ ধরার তিন দিন আগে থেকে ভালো ফসলের প্রত্যাশায় তাঁরা তাঁদের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানানোর পাশাপাশি দু’একটি নিয়ম মেনে চলেন। সেই কদিন তাঁরা কোনো প্রাণীকে বলি দেন না এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস করেন না। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ জনজাতিই বংশানুক্রমে প্রচলিত এক প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে নদীর মাছ ধরেন। প্রথমে তাঁরা বাঁশ, বোল্ডার, মাটি, গাছের পাতা ও ডালপালা দিয়ে একটা অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করেন। তারপর আটকে রাখা জলে বড় বড় পাথর বা গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পেতে তার ওপর আঁটি বেঁধে রাখা এক বিশেষ প্রজাতির (derris elliptica) গাছের শিকড়-বাকড় লাঠি দিয়ে সমানে পেটাতে থাকেন। তাতে সেগুলোর রস জলে মেশার ফলে মাছগুলো অচৈতন্য হয়ে যায়। তখন তাঁরা হাত জাল বা শুধু হাত দিয়েও মাছ ধরতে নেমে পড়েন। উত্তরাখন্ডের টেহরি গাড়োয়ালের জৌনপুরে প্রতি বছর ২৯ শে জুন আয়োজিত মাছ ধরার উৎসব ‘মৌন মেলা’ (Maund Fair)-তেও সেখানকার লোকেরা মাছেদের অচৈতন্য করতে অগলাড় নদীর জলে জড়িবুটি মেশান। তবে তাঁরা এ কাজে টিমরু (zanthoxylum armatum) গাছের শেকড়,পাতা ও বীজের গুঁড়ো ব্যবহার করেন।
কৃষির সমৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত বার্ষিক মাছ ধরার উৎসব উত্তর ভারতের কাশ্মীরেও প্রচলিত। যেমন, মে মাসে অনন্তনাগের কাজিগুন্ডের পানজাথ নাগ ঝরনায় স্থানীয় অধিবাসীরা ট্রাউট মাছ ধরতে যান। তবে দক্ষিণ ভারতে এই উৎসবের রমরমা বেশি। এপ্রিল মাসে কেরালার কান্নুর জেলার পায়ানুরে সালিয়া জাতির লোকেরা পায়ানুর মীনামরুথু উৎসব উপলক্ষ্যে কাব্যায়ি কয়াল (backwater) – এ মাছ ধরতে যান। সেই মাছ পায়ানুরের অষ্টমাচল ভগবতী মন্দিরের দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। অতীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে জলযাত্রা নিরাপদ করতে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল বলেও মনে করা হয়। কর্ণাটকের সুরথকলের কাছে চেলাইরু খান্দিগে ধর্মারাসু শ্রী উল্লায়া মন্দিরে মে মাসে বৃষভ সংক্রান্তির দিন মাছ ধরার উৎসব পালিত হয়। নন্দিনী নদী থেকে মাছ ধরে রান্না করে মন্দিরের দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অর্পণ করার পর সবাই তা প্রসাদ হিসাবে খান। ‘মীনু হাব্বা’ কর্ণাটকের আরেক ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার উৎসব। উত্তর কন্নড় জেলার কারোয়ার তালুকের কিন্নর গ্রামে এই উৎসব দেখতে মুম্বাই, গোয়া থেকেও বহু মানুষ আসেন। মে মাসের একটি দিন উৎসবের জন্য স্থির করা হয়। সেদিন এলাকার লোকজন গিন্দিদেবীর মন্দিরে পূজো দিয়ে কালী নদীর কয়ালে মাছ ধরতে যান। মাছ ধরার পর প্রত্যেককে তাঁদের প্রাপ্ত মাছের অর্ধেক ভাগ মন্দিরে দিতে হয়। মন্দিরে দেওয়া মাছ নিলামে বিক্রি করে সেই অর্থ মন্দিরের কাজে লাগান হয়। হাভেরি জেলার হানাগুল তালুকের কিসানুর গ্রামেও ‘মীনু হাব্বা’ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার থিরুভাথাভুর, মেয়াপ্পানপট্টি, সারুগুভালায়াপট্টি ইত্যাদি গ্রামে বিভিন্ন জলাশয় থেকে মাছ ধরেন স্থানীয় মানুষজন। এছাড়াও চৈত্র মাসে কাল্লানধিরি মুথান স্বামী থিরুকোভিল মন্দিরের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক উৎসবের শেষ দিনে একটি বিশাল জলাশয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেখানকার পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দারা মাছ ধরেন। সেই মাছকে তাঁরা ‘পবিত্র’ মনে করেন বলে বিক্রির পরিবর্তে বাড়িতে নিয়ে যান। তামিল ভাষায় এই মাছ ধরার উৎসবকে ‘কানমোই আঝিথাল’ বলা হয়। রবি শস্য বা চৈতালি ফসলের বীজ বপনের সময়কালে ওই জলাশয়ে মাছের পোনা ছাড়া হয়। ফসল কাটার পর বড় হয়ে যাওয়া সেই মাছগুলোকেই উৎসবের সময় ধরা হয়। কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ উৎসবে যোগ দেন।
এত কথার শেষে নটেগাছ মুড়োনোর আগে মনে পড়ল কবি ঈশ্বর গুপ্ত-র লেখা দুটি পংক্তি-“ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙ্গালি সকল/ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল”। কামনা করি শুধু বাঙালিরা নন, ভাত-মাছ যাঁদের স্বাভাবিক আহার্য, তাঁদের সকলের সন্তান মাছে-ভাতে থাকুক। অবশ্যই সেই মাছ-ভাতকে ভেজাল ও বিষ মুক্ত হতে হবে। তবেই তারা বাঁচবে। আর তারা বাঁচলেই বেঁচে থাকবে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কালজয়ী সাক্ষী এই গ্রামীন মাছ ধরার উৎসব ও মেলাগুলো।
সহায়ক গ্রন্থঃ
(১) পূজা পার্বণের উৎসকথা – পল্লব সেনগুপ্ত
(২) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতি – সুধাংশু কুমার সরকার
এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্যাপিত মাছ ধরার উৎসব ও মৎস্যমেলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি ইন্টারনেট, বিশেষত ‘ইউ টিউব’ থেকে।
ছবি সৌজন্যঃ গুগল
***************************************
সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিতিঃ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘দর্শন’-এ স্নাতকোত্তর সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত একজন লেখিকা,সংগীতশিল্পী এবং বিজ্ঞান ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। ‘কালান্তর’,‘সুস্বাস্থ্য’ ‘উৎস মানুষ’,‘টপ কোয়ার্ক’,‘যুক্তিবাদী’, ‘এখন বিসংবাদ’,‘মানব জমিন’,‘আবাদভূমি’,‘সাহিত্য সমাজ’,‘সারথি’,‘অভিক্ষেপ’ ইত্যাদি বেশ কিছু পত্রিকা ও সংবাদপত্রে তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একসময় তিনি ছিলেন ‘আজকাল’ পত্রিকার নিয়মিত পত্রলেখিকা। ২০০৩-এ ‘ভারতের মানবতাবাদী সমিতি’-র উদ্যোগে তাঁর সম্পাদনায় ‘র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন’ প্রকাশন থেকে ড. পবিত্র সরকারের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়েছে ‘ছোটোদের কুসংস্কার বিরোধী গল্প’-র দুটি খন্ড। তাঁর লেখা ‘ইতিহাসের আলোকে মরণোত্তর দেহদান–আন্দোলন ও উত্তরণ’ বইটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। দূরদর্শনে ‘মরণোত্তর দেহদান’ নিয়ে সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্যও রেখেছেন। সম্প্রতি চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী কানন দেবীর জীবন নিয়ে তাঁর একটি গবেষণামূলক কাজ ‘ফেসবুক’-এ তাঁর টাইমলাইনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে তিনি ‘সংগীত প্রভাকর’ ও ‘সংগীত বিভাকর’। দীর্ঘদিন শাস্ত্রীয় সংগীতেও তালিম নিয়েছেন। শৈশব ও কৈশোরে বেতারে ‘শিশুমহল’,‘গল্পদাদুর আসর’ ও ‘কিশলয়’-এর অনুষ্ঠানে বহুবার গান গেয়েছেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় ও এই রাজ্যের বাইরেও মঞ্চানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত,পল্লীগীতি ও গণসংগীত ছাড়াও তাঁর ভাই রাজেশ দত্তর কথায়-সুরে ‘মানবতার গান’ পরিবেশন করেছেন। ২০০৬-এ রাজেশের কথায়-সুরে তাঁর গাওয়া ‘পাল্টা স্রোতের গান’ অডিও ক্যাসেট ও সিডি আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রজীবনে বেশ কয়েকটি নাটক ও শ্রুতিনাটকে অভিনয় করেছেন। পরবর্তীতে চন্দননগরের ‘কোরক’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাট্যাভিনয় করেছেন। আবৃত্তি,সংগীত ও কয়েকটি ‘রিয়্যালিটি শো’-এ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কৈশোরে খেলাধূলার জগতেও তিনি বিচরণ করেছেন। স্কুলে ইন্টারক্লাস ‘কবাডি’ খেলায় নিজের ক্লাসের টীমে তিনি ‘ক্যাপ্টেন’-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। চন্দননগরের ‘চিত্তরঞ্জন ব্যায়ামাগার’-এ তিনি ‘জিমনাস্টিকস্’,বিশেষত ‘তারের খেলা’-র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ব্রতচারী নাচের প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র-ও অর্জন করেছেন। এখন গৃহকর্মের ফাঁকে ও অবসরে লেখালেখি ও গানের চর্চা ছাড়াও আঁকতে ও ছবি তুলতে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর নিজের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ’ভ্রমণ’।