 রাঢ়ের ‘গাজন’ ও দত্তবরুটিয়াঃ একটি মূল্যায়ন
রাঢ়ের ‘গাজন’ ও দত্তবরুটিয়াঃ একটি মূল্যায়ন
অনুপ মুখার্জি
সুপ্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী প্রতিটি লোক সমাজের নিজস্ব চেতনা সম্পন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। অনেকে একে প্রান্তিক, প্রতিবর্গ বা গ্রামীন সমাজ বলে অভিহিত করেন। সার্বজনীন প্রতিনিধিত্ব এই সমাজে শুধু মুখ্যই নয়,ব্যক্তি বিশেষের প্রজ্ঞা সমাজের সবার অভিজ্ঞতার নির্যাস হয়ে ওঠে। তাতে আত্মগোপন করে থাকে তাদের বেঁচে থাকার রসদটি অর্থাৎ জীবন জীবিকা। যার প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক উৎকর্ষতার রূপটি ফুটে ওঠে। নেই ব্যক্তি পুজো। সমাজ স্রষ্টা হওয়ায় সৃষ্টিকর্তার চোখ রাঙানি নেই। প্রাচীন মানুষের এই সম্মিলিত কালোত্তীর্ণ দর্শন-ই লোকায়ত দর্শন বা সংস্কৃতি। বলা বাহুল্য প্রাচীন মানুষের এই সংস্কৃতির আবরণ অবশ্যই ধর্মীয়, যেমন ‘গাজন’। কিন্তু তাতেই লেগে রয়েছে বহু যুগ অতিক্রমণের ফল স্বরূপ একাধিক ধর্মীয় সংঘাত ও সমন্বয়ের নানাবিধ প্রলেপ। অনুসন্ধিৎসু মন এবং বিশ্লেষণী চেতনা সূত্র ধরে পৌঁছে যেতেই পারেন আদিম রূপটির দোর গোড়ায়। প্রাজ্ঞ লোকসংস্কৃতিবিদগণ এবিষয়ে মামুলি দু-চার কথা ব্যতীত কেন গভীরে গেলেন না, তা নিয়ে আমার ধন্দ রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমি নগণ্য, ক্ষমাপ্রার্থী।
(লেখনীধৃত বর্ণনার গ্রাম সমাজ চিত্রের মৌলিক সময় কাল একটানা ১৯৮০ সাল অবধি। আলোচ্য কালপর্বের স্মৃতি, পরবর্তীতে এর প্রবহমান ধারা, আর বর্তমানের অনুধ্যান আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। স্বতই কোন গভীর সুচিন্তিত মনে দাগ কাটার মতো রসদ হয়তো এ রচনায় মিলবে না।)
গ্রাম জীবনঃ মুর্শিদাবাদের সালার ও শিমুলিয়ার মধ্যিখানের গ্রাম-দত্তবরুটিয়া।মুখ্য প্রবেশ পথ – দক্ষিণ মুখী। সেই সময় প্রবেশ পথের দেড় কিমি.বছরের প্রথম ছয় মাস গভীর চ্যাটালো কাদায় ভরতি থাকত। উত্তর মুখী পথটি তৎকালে অপ্রচলিত ছিল। বিদ্যুৎ আসে এতদঅঞ্চলের গ্রামগুলিতে ১৯৭৬ সালের পর। যাতায়াত মাধ্যম-পা,পাল্কি, ডুলি, সাইকেল, গরু-মোষের গাড়ী। কিছুটা দূর থেকেও গাঁ দেখা যায় না। ছোটবড় পুকুর, নানান গাছ গাছালি ঢেকে রাখত মাটির খরুটি করা একচালা, দোচালা, চারচালাজুড়ে শান্ত অথচ জঙ্গম জড় ও জীবের প্রবহমান ধারাটিকে।
নগুরে লোকেরা তেমন একটা আসত না, ভোটের প্রচার ছাড়া। একমাত্র বছর শেষে চৈত্র মাসে, ভিটে ছাড়ারা ঘরে ফিরত গাজন উপলক্ষে, সঙ্গে দু এক জন শহুরে বন্ধু বান্ধব।
অনুষ্ঠানঃ এই গ্রামের গাজন বহুলাংশে অন্য ধারার। প্রধানত পাঁচ দিন ব্যাপী। প্রথম দিন, শিব ওঠা। বারবেলার পূর্বে প্রধান পুরোহিত সর্বসমক্ষে গ্রাম দেবতাকে কক্ষে নিয়ে – তারই (আরাধ্যের) শুধুমাত্র এক নিশি যাপনকারী একটি অতি সাধারন ছোট্ট মাটির চালা ঘরের সামনে হাজির হন। মুখোমুখি দন্ডায়মান শিখী পালক গুচ্ছধারী দেয়াসিনি। এর একুশ দিন পূর্বে দেয়াসিনির ক্ষৌর কর্ম হয়।তাদের ঘিরে উচ্চ বর্ণের ছত্রধারী মানুষ। তখনই ঢাক ও নানান প্রাচীন বাদ্য ভান্ডির বাদনে বসন্তের শেষ কয়টি প্রখর দিন মুখর হতে শুরু করে।আর শুরু হয় হত দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেনীর মানুষ গুলির আকাশ বাতাস বিদীর্ন করে শূন্য হাত, রিক্ত বসনে এক পৃথিবী জয় করার আনন্দ, আর নাচানাচি। এক রাতের গৃহ থেকে বেরিয়ে অপর স্থায়ী আটচালা গৃহের প্রায়-তিনশ গজ দূরত্ব পার হতে তখন ঘন্টা তিনেক লাগে। আদি ও অন্তের প্রায় ষাট সত্তর গজ রাস্তা এই মানুষগুলি পরম আরাধ্যের জন্য বুক পেতে দেয়। সেদিন এবং পরের দুই দিন বিকাল থেকে রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে শুদ্ধ ভক্তদের নাচ। তৃতীয় রজনী ‘জাগরণ’ রাত নামে চিহ্নিত। চতুর্থ দিন ‘জল সন্ন্যাস’ এবং পঞ্চম দিন হোম।
অন্ত্যজ সংস্কৃতিঃ গাজনে উঁচু জাতের বোলবোলা কম। প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের সে কি আবেগ! ঘর গেরস্থালি দেহ মন জুড়ে আবহমানের যে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা তা কর্পূরের মতো উবে যেত এই কয়েকটি দিন। হয়ত লবার বাবা তাদেরই মতো নিরাভরণ, নিরলঙ্কার বলে। রাঢ়ের ইতিহাসে অবশ্য বহু কালের ধর্ম সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারার যে ঐতিহ্য তারই এটি একটি রূপ-যে দিন গুলিতে ঘুমিয়ে থাকা গ্রাম গুলি জেগে ওঠে, প্রাণ পায়। এই জাগরণের উৎস কোথায় ,আজও কেন কেউ তলিয়ে ভাবে না, অন্তত যাদের ভাবার কথা, কে জানে! এই উন্নাসিকতা প্রান্তিক মানুষদের লৌকিক উৎসব বলেই কী?
ধরনঃ চৈত্রের শুরুতেই সাঁঝ পেরোলেই কানে ভেসে আসত একদিক থেকে গোলা ঢোল, অপরদিকে ঢাকের দূরাগত ধ্বনি। পাড়ায় পাড়ায় বোলানের মহলা। বোলান দুই ধরনের- এক) ডাক বোলান, দুই) পোড়ো বোলান।
গাজনের ভক্ত দু ধরনের- এক) শুদ্ধ ভক্ত ও দুই) পাতা ভক্ত (পোড়ো বোলানের অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় পাতা ভক্ত)। প্রথমটিতে, অব্রাহ্মণ্য আধিক্য লক্ষ্যনীয়। ভক্তদের ক্ষৌর কর্ম হয় দেয়াসিনির বাড়িতে। সাধারণ মানুষ একে ‘বত্’ করা বলে। শব্দটি ‘ব্রত’ (‘বৃ’ধাতুর সঙ্গে অতচ্ প্রত্যয়, অর্থ বরণ করা)-র অপভ্রংশ। এটি অবশ্যই বাঙলায় কম প্রচলিত ব্যাতিক্রমী পুরুষ দেবতার ব্রত। পৌরোহিত্যকারীদের অর্থ ও সম্মান বর্জিত থাকায় বৈদিক ধর্মে ব্রত পালনকারীদের ‘ব্রাত্য’ অর্থাৎ হীন চোখে দেখা হতো। এবং রীতিটি দ্রাবিড়ীয়। (ধারণাটি পায় পল্লব সেনগুপ্তের পূজা পার্বনের উৎস কথা গ্রন্থে এবং সুহৃদ ভৌমিকের লোকশ্রুতি ১২ সংখ্যায়)। যাই হোক রীতি নীতিতে খনিকটা বৈষ্ণবীয় ধারা। এদের পায়ে নূপুর, হাতে বেতের লাঠি, গলায় আকন্দের মালা ও উতুরে, কপালে গুলঞ্চের মালিকা, পরনে ধুতি ও নতুন গামছা। দিনে ছোলা গুড়, জল, বাখারি, কলা সহযোগে ফলাহার। রাত্তিরে বদ্ধঘরে আড়াই নুড়ির পাকে হবিষান্ন। হবিষান্নকালে চামড়া জাত কোনো শব্দ তাদের কানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। শরীর ঠিক রাখতে বিশেষ বৈকালিক নৃত্য ঢাকের বাদ্যির তালে। মধ্যাহ্নের সূর্য একটু পশ্চিমে ঢললেই ব্রতকারীরা তাদের জন্য কালগত নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর জলে স্নান সেরে প্রায় সিক্ত বসনে উড়ন্ত বলাকার সারির ন্যায় কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হয়ে ডান হাত সঙ্গীর কাঁধে ও বাম হাত নিজ কোমরে দিয়ে পা আগু-পিছু করে নৃত্যের ভঙ্গীতে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করেন। আবার বিশেষ বিশেষ স্থানে উত্তর-পশ্চিম কোনে হাতির শুঁড়ের ন্যায় শির ঝুঁকিয়ে মুখে ইষ্ট দেবতার স্মরণ নেয় অর্থাৎ জাগ দেয়। একে বলে মাথা খাটানো। আর এদের সম্মুখভাগে থকেন মালসাধৃত দেয়াসিনি। এই মালসাকে ঘট রূপে বিবেচনা করলে, পল্লব বাবুর ধারণা মোতাবেক-এটি একটি আদিম সংস্কার এবং মাতৃতান্ত্রিকতার রূপক হিসেবে অন্তর্বর্তী নারীর সঙ্কেতবাহী। উন্মুক্ত ধূলিধূসর প্রান্তরে নির্দিষ্ট তিন-চারটি মন্ডপ চত্তরে তাদের যে ঘণ্টা খানেকের করে নৃত্যশৈলী তা নয়নাভিরাম ও অদৃষ্টপূর্ব। এটি ‘শাস্ত্রীয় নৃত্য’ কি না তার বিচার আপনাদের। “লোকনৃত্য হতে উদ্ভূত শাস্ত্রসম্মত ও নিয়মনিষ্ঠ নৃত্য পদ্ধতি”-কেই শাস্ত্রীয় নৃত্য বলেছেন ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় (লোকশ্রুতি ১২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬)। একমাত্র আলোচ্য গ্রামটিতেই এই পরম্পরাগত ঐতিহ্য আজ ও প্রবহমান। বাদ্যির এই তাল ঢাকিদের বংশগত প্রাপ্তি। সে সময় কানু কাকা, শিবরাম কাকা দক্ষ বাজিয়ে ছিলেন। এঁনাদের বাড়ী বর্ধমানের দখিনদি গ্রাম।
পাতা ভক্তঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,’পাতা’ শব্দের অর্থে বলেছেন,পালন কর্তা বা রক্ষাকর্তা (পা-রক্ষা করা+তৃ)। কিন্তু সমাজ ইতিহাসের ধারায় একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, মনুর বিধানে, ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে, একেবারে জল অচল অন্ত্যজ শ্রেনীর মানুষেরা পাতক হিসাবে পরিগণিত হতো। এবং এরাই এই আলোচ্য অনার্য দেবতার আদি উপাসক। তাই হয়ত এদের পাতা ভক্ত নাম। কথাটা এই কারণেই বললাম,গাজনের পঞ্চম তথা শেষ দিনে, এই অন্ত্যজ উপাস্য দেবতার ধূমধাম করে হোম-যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে, এর শুদ্ধিকরণ ঘটে। আমার ধারণায় শুদ্ধ ভক্ত ও হোম যজ্ঞ গাজনের প্রাচীন অঙ্গ নয়, এটি আর্যীকরণ এর ফল।
পাতা ভক্তদের পরম্পরাগত পরিধেয় বস্ত্রাদি, সঙ্গিন ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী খুবই পবিত্রতার সঙ্গে সংরক্ষিত। গলা থেকে কোমর ও কোমর থেকে পা দুভাগে গাঢ় লাল, কমলা কাপড়ের উপর নানান টোটেম যুক্ত সেলাই। মুখ ভয়ংকর চিত্রিত। মাথায় বিশাল পরচুলা,হাতে সরু লম্বা অসি ও নরমুণ্ড, কোমরে ঘন্টা। গান মৃদু স্বরে। কথা করুণ। বাজনা নৃত্যানুসারী চিরায়ত বোল যুক্ত। কখনো খাতে তো খানিক পরে সপ্তমে। অসিটি মাটিতে নিম্নমুখী ঠেকিয়ে, দেহের উর্দ্ধাংশ অর্ধ নমিত করে বৃত্তাকারে অন্তত ৬-১০ জনের দল এই নাচে অংশ নেয়। সারারাত ব্যাপী গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওরা এই নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। তাদের চলার পথের ঘণ্টা ধ্বনির শব্দ কালো রাতের বুক চিরে দূর বহুদূর পর্যন্ত এক মায়াবী স্বপ্নলোক রচনা করত। আজও কোন চৈত্র রজনীতে কল্প জগতে বিচরণ করতে করতে চোখ বন্ধ করলে ভেসে ওঠে- গ্রাম ছাড়িয়ে ধূ ধূ ধানের জমি,মাঝে মধ্যে শ্যাওড়া, শিরিষ, আম, জাম, তাল, বেলের জঙ্গলে ঘেরা ছোট বড়ো পুকুর, সেখানে আঁচলা ভরে জল খেয়ে, হাতে লন্ঠনের টিমটিমে আলোয় জোনাকির মতো ভাসতে ভাসতে তাল বেতালের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বিকারহীন ভাবে এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ ! এদের ঐ নিশীথের চলার পথের কাল নিরূপণ কেউ করেনি। সে ইতিহাস জানে একমাত্র নিরবধি কাল, আঁধার রাতের তারা !
লোক গবেষকরা কী বলবেন জানি না, আমার মতে , পোড়ো বোলান বাঙলার অন্যতম প্রাচীন ‘লোকনৃত্য’। সমাজের বিশেষ স্তরের সরল সাধারণ জনগোষ্ঠীতে উদ্ভূত ও নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানেই এর স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শৈলী,পরম্পরা ও ঐতিহ্য সেই সাক্ষ্যই বহন করে। যদিও সংরক্ষণের অভাবে ক্রম বিলীয়মান। আলোচ্য সময়ে উক্তস্থানে এই বিশেষ ধরনের লোক নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন সিপাই বায়েন, শিবু বায়েন, শান্তি বায়েন, রতন বায়েন প্রমুখরা। এনারা সাধারণত সুরাপায়ী হয়েই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। তবে উক্ত দিবসে সূর্যোদয়ের পর থেকে এনারা উপোসী থাকেন। মধ্যাহ্নের পর মৃৎশিল্পীদের কাছে মুখাঙ্কন করিয়ে এসে দেয়াসিনির কাছ থেকে পবিত্র ক্ষীর জল (যা,একটি ছোট মৃৎপাত্রে থাকে) গ্রহণের পর তাদের পূত ঐতিহ্যবাহী পোষাক অঙ্গে গলিয়ে, অন্তত তিন পুরুষের অসিটি ধারণ করে, যে গাছে সংগৃহীত নর করোটি এ কয়দিন ঝুলিয়ে রাখা ছিল, সেটি শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে পেড়ে আনেন ও ক্ষীর জল পান করান এবং নিজেরাও গ্রহণ করেন। বিগত কয়েকদিন তাদের পরিবার আজকের এই বিশেষ আরাধ্যটিকে নিয়মিত ধূপ সন্ধ্যা দেখিয়ে এসেছেন। পোড়ো বোলানের দল জল সন্ন্যাসের দিন তাদের এই মূল উপাচারটি নিয়ে, আরাধ্য দেবতার সামনে নাচতে নাচতে গঙ্গায় গিয়ে একসঙ্গে অবগাহন করে নর করোটি ভাসিয়ে দেন। তখন ঢাকের বোল একটাই – “লবার বাবার জল সন্ন্যাস।” উনি দোলায় চড়ে শুধু চাঁদ মালা সজ্জিত হয়ে চললেন, সঙ্গে বাণেশ্বর। লোকপ্রবাদে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের তাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই মিলিত হবেন উদ্ধারণপুরের ঘাটে। অন্য ভাইয়ের ভক্তরা রাঘবেশ্বরকে নিয়ে স্নান করবেন। ভায়ে ভায়ে মিলনের এই বার্তা কী অসীম মৌলিক! ঢাক সহ অন্যান্য বাদ্যভান্ড রইলেও শিঙার ধ্বনি এ যাত্রায় মুখ্য। ও… বলে দিই লবা কে? লবা অর্থাৎ লম্বোদর- গণেশ। তারই বাবাকে নিয়ে নাচ গান আনন্দ উৎসব। বুঝছেন নিশ্চয় লৌকিক দেবতার সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের কী সম্পর্ক!প্রবহমান ধারাঃ আসলে বাঙলায় লিঙ্গ পুজোর প্রচলন বহু প্রাচীন – প্রাক আর্য যুগের। পরবর্তীতে দ্রাবিড়ীয় ভাবধারা যুক্ত হয়ে সম্ভবত শুদ্ধাচারী ভক্তদের উদ্ভব।
এই দু ধরণের ভক্তদের প্রধান দেয়াসিনি। এক্ষেত্রে নাপিত। তিনি কী ইতিহাসের কোন কাল পর্বে রাঢ়ে বর্ণ বিভাজিত সমাজের মধ্যস্থতাকারী বা সমন্বয়কারীর ভূমিকায় ছিলেন? এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখলাম। বলাবাহুল্য এই কয়দিন তারই প্রাধান্য। সারা চৈত্র মাস জুড়ে চলে তার শুদ্ধাচারী কৃচ্ছ্রসাধন। তার মালসা ধৃত জল (যা ক্ষীর জল নামে পরিচিত) ও হস্ত ধৃত শিখি পালক গুচ্ছই ভক্তদের এ কদিনের সকল পীড়ার দাওয়াই।
জাগরণের রাত্রিঃ গাজনের মুখ্য প্রাণসত্তা নিহিত এই রজনীতে। এ সময় আমরা মনে দুর্মর আগ্রহ চেপে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতাম। কবে আসবে ‘জাগরণের রাত’। দেখব পাতা ভক্তদের পোড়ো বোলান, লুকিয়ে শুনব ডাক বোলান। ‘ডাক’ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সাধক। ‘ডাকার্ণব’ এ বারাহী ও শ্রী হেরুক বলেছেন, অবধূতপন্থী এই সাধকরা দেহকে আশ্রয় করে ‘হরগৌরীসমাক্রান্ত’ যুগলের সাধনা করতেন। মূর্তি অপেক্ষা গান ও সাধনা তাদের বড় প্রিয়। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত নানা গ্রন্থে এদের উল্লেখ মেলে। অতঃপর হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রাধান্যের প্রাবল্যে কিছুকাল সংঘাতের পর শৈব ও শাক্তের মিলিত ধারার সঙ্গে নিজেদের সর্মপিত করেন। কিন্তু গোপনে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায়, ইঙ্গিত মূলক বক্তব্যে নিজেদের গান ও সাধনা করতেন। বাঙালি চর্যার কাল থেকে আউল-বাউল, বৈষ্ণব (গৌড়ীয়), নাথ, যোগী সবার কথাই জানে। কিন্তু কতটা জানে সেই ধারারই বোলান বা ‘ডাক বোলানের’ কথা? স্মর্তব্য, বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের অবনতির সময় থেকে, অর্থাৎ ষোড়শ শতক থেকে এপর্যন্ত সামাজিক উচ্চবর্ণের কাছে এই সংস্কৃতি যথেষ্ট হেয়র পাত্র। আর সময়ের ধারায় নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে পূর্বের ঠাট ধরে রাখলেও ভাষার ধার পরবর্তী যুগ ও রীতির ক্রমানুসারী হয়েছে এবং এটিই স্বভাবিক। (সূত্রঃ শ্রী রমেশ বসু মহাশয়ের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৩২ তম বর্ষে,৮ ম মাসে পঠিত প্রবন্ধ)।
আলোচ্যমান সময়ে, ডাক বোলানের একমুখো, দুমুখো, তিন মুখো পাঁচালি শুনতে রাশভারী পিতৃদেব বা গুরুজনেদের চোখ এড়িয়ে রাত জাগা ছিল আমার মতো অনেকেরই প্রায় অসাধ্য। বোলান, পাঁচালি দুটিতেই থাকত সমস্যা জর্জরিত মানুষের অসহায়তার কথা। তবে পাঁচালিতে অগ্রসর বা পরাবর্গ সমাজের প্রতি কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আদি রসের প্রাবল্য থাকত বলে নাক উঁচুরা এড়িয়ে চলত। ভূমিহীন কৃষিজীবী এই মানুষেরা সারাদিন উদায়াস্ত পরিশ্রমের পর, লন্ঠনের বা কুপির আলোতে বোলানের মহলা দিতেন। বন্দনা ও গানে ‘ভক্তিভাব’ এবং পাঁচালিতে ‘নাগরভাব’ প্রাধান্য পেত। রাঢ়ে ভক্তিবাদের প্রভাব অতি প্রাচীন। পরবর্তীতে শ্রী চৈতন্যদেবের সমুন্নত ভাবাদর্শের প্রভাবের পাশাপাশি সম্ভবত তাঁরই মৃত্যু পরবর্তী একশ্রেণির রাঢ়ী অনুগামীদের অসামাজিক ভাবধারার প্রকোপও পড়ে। বন্দনায় জোড়হাত করে গাইতেন- “চরণ ছাড়া করো না, মোরা ভজন তো জানিনা।“ চরাচর জুড়ে বিরাজমান আঁধারে জোনাকির ভেসে বেড়ানোর মতো এর রেশ আজও কানে বাজে। পালা শেষে হলে শুরু হতো পাঁচালি গাওয়া। বিষয়ঃ বাবু মানুষ, সমাজপতি, নেতাদের ঢলুনি ও চালবাজি, দুই সতীনের ঝগড়া, মনিবের ছেলের পরকীয়া, ঘরের বউকে মেলা দেখানোয় ফাঁকি দেওয়া- কত কী। “আর কবে কিনে দিবি খোঁপার ফুল, আজ দিবি কাল দিবি করে পেকে গেল মাথার চুল”। “নিচের দিকটা আমি লেব, উপর দিকটা তোকে দেব….. “, সতীনদের এই ঝগড়ায় স্বামী বাবাজির প্রাণ যায় আর কি! এসব শুনে গাঁয়ের বৌঝিরা ঘোমটার আড়াল থেকে হাসি ঠাট্টায় ঢলে পড়ত। কিশোর, কিশোরীদের মনও যে ছুঁয়ে যেত তা তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পেত। পালায় ‘মেয়েলি’রা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কী সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশ করত। সামাজিক শিক্ষার এ হেন জ্ঞান মাধ্যম আজ কোথায়?আসর ফাঁকা যায় না। বোলানের পরই কোনো না কোনো দল পোড়ো বোলান শুরু করে। ডাকিনী যোগিনী সেজে নর করোটি নিয়ে দুঃখ ভরা চাপা স্বরে ঢাকের তালে নাচ-গান, আর ভাগাড়ের শকুনির দল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে ভাবে ভয়ঙ্কর মুখাঙ্কন ও আলখাল্লা পরিহিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যেন সামগ্রিকভাবে এঁকে চলা চিরায়ত জীবনের অলিখিত পট। আমার মতো সমবয়সীদের তখন উৎসুক্য ও ভয়ে, দ্বিবিধ অন্তর। উভয়বিধ বোলানের গীতিকার রূপে কালকেপুর (বামুন্দি) গণপতি এবং তাঁর শিষ্য চন্দ্রশেখরের এবং বালুটিয়ার ষষ্টীচরণ দাসের নাম উল্লেখের দাবি রাখে।
প্রাসঙ্গিকতাঃ শ্রী নরোত্তম হালদারের, “গঙ্গারিডিঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা” নামক গ্রন্থানুযায়ী, প্রাকৃত ‘পুড’ থেকে ‘পোদ’ জাতিবাচক শব্দের উৎপত্তি,যার সংস্কৃত অর্থ পুন্ড্র বা পৌন্ড্র। আবার এই সংস্কৃত ‘পুন্ড্র’ থেকে জাতিবাচক ‘পুঁড়ো’ শব্দের উৎপত্তি। এবং এরাই প্রাকার্য যুগের বাঙলার অধিবাসী। যাদের বিস্তার ছিল, রাঢ় ও বরেন্দ্রর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল কৌম। সমাজ বিবর্তনের ধারায় এরা বার বার ধর্মান্তরিত হয়েছে। যে সকল জল চল বা অচল সম্প্রদায়ের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে, আমার ধারণা তারা প্রায় সকলেই এদেরই উত্তরপুরুষ। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহাস্থানগড় লিপিতে পুন্ড্রনগর ও এর অধীন জনগোষ্ঠীগুলির উপর বৌদ্ধ প্রভাব এবং সামাজিক, আর্থিক ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যহীন অব্রাহ্মণ্য চরিত্রের সন্ধান পায়। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এই ‘পুঁড়ো’ জাতির কোন উপাসনা সংগীত থেকে কী আজকের পোড়ো বোলান?
যাই হোক,এই অচ্ছুৎ সম্প্রদায় উক্ত রজনীতে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বছরে একটি বারের জন্য অবাধে আরাধ্যের ঘরে সর্বাগ্রে প্রবেশাধিকার ও নিজস্ব ধারায় আরাধনার অধিকার পান। রাত গভীর হলে মশাল প্রজ্জ্বলিত করে উভয় ভক্তবৃন্দ আরাধ্যের উদ্দেশ্যে ‘জাগ’ বা জয়ধ্বনি দিতে দিতে মূল মন্দির থেকে অদূরে কালী মন্দিরের দিকে যান। উদ্দেশ্য উভয়ের ‘জাগরণ’ পালন। জীব জগতের সৃষ্টি চেতনার রহস্যঘন এক দর্শনের যেন উন্মোচন মুহূর্ত হয়ে ওঠে সেইক্ষণ।
সেই রাত্রে তারাই প্রধান উপাসক। তাদের এটুকু ভূমিকা না থাকলে যে রাঘবেশ্বর (উল্লিখিত গ্রামের শিবের নাম) রাত প্রভাত হলে গঙ্গা নাইতে যাবেন না। বুঝুন ঠেলা!! ইনিই গ্রাম দেবতা। এনার একশ গজ মতো দূরত্বে গ্রামদেবী কালিকার অবস্থান। ইনিও রাঘবেশ্বরের ন্যায় নিরাবয়ব প্রস্তরময় হলেও, আকারে বেশ বৃহৎ এবং পূর্বপুরুষদের বক্তব্যানুযায়ী ক্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। হয়তো জীবাশ্মগত কারণে। কথাটা উল্লিখিত হওয়ার কারণ, পোড়ো বোলানের দলের এই স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ! নিকট অতীতে রাঘবেশ্বরের মন্দির ছিল মাটির আট চালা গড়নের। আর কালীমন্দির রেখ দেউল গড়নের বাংলা ইঁটের তৈরি। আমার অনুমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ত্যজ মানুষদের কাছে টানার উদ্দেশে উচ্চবর্ণের লোকেরা গ্রাম দেবতার স্থানান্তর ঘটিয়ে, তার মর্যাদা দিয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। তবুও বলাবাহুল্য যারা সব মন্দিরে ব্রাত্য, তারাই আজ লবার বাবার উপাসক, সঙ্গী।
বৌদ্ধ প্রভাবঃ বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কোন শাখার প্রতিফলন কী এইটি? সুদিনে বৌদ্ধধর্ম এতদ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল, তা সুধী জনেরা জানেন। শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া তাঁর “প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ ” নামক গ্রন্থে, হিউয়েন সাং এর বিবরণী উল্লেখ করে জানিয়েছেন, সে সময় কর্ণসুবর্ণে দশ বা ততোধিক সঙ্ঘারামে দুই হাজারের মতো আচার্য্য ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের অন্য তিন স্থানে ‘দেব দত্ত সম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধ’-রা আরো তিনটি সঙ্ঘারামে বাস করতেন। আলোচ্য গ্রাম নাম এবং বিবৃত বিষয়ের সঙ্গে এই সূত্র কী একেবারেই অপাংক্তেয়?
সূত্র সন্ধানঃ লোক গবেষক নির্মলেন্দু ভৌমিক এই জাগরণের গান কে বলেছেন কাম জাগানোর গান। শুধুই কী তাই? না আর ও অনেক কিছু? স্মরণীয় যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, বোধায়ন ধর্মসূত্র, মনুসংহিতায় বঙ্গ ও বাঙালিরা হেয়র পাত্র। আবার খ্রিস্টের জন্মের আগেই বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ও বিস্তার। জৈনরা দুর্বল হয়ে পড়লেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে বাঙলা। কিন্তু কালক্রমে বাঙলার ব্যয়বহুল বিহার নিবাসী ভিক্ষুরা জনসংযোগ হারায়। ফলে পাল, খড়গ, চন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার না করে ভগবান বুদ্ধের নামেই তাদের ভূমিদান করতেন। অথচ গুপ্ত যুগের আগেই বাঙলায় বৈদিক পৌরাণিক ধর্মের ভিত্তি ছিল। পাঁচ থেকে তেরো শতক পর্যন্ত তাই ভূমিদানে বৌদ্ধদের সংখ্যা কম। এই সময়কালে মঠবাসী ভিক্ষুদের তুলনায় ব্রাহ্মণরা সহজেই পৌরাণিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে স্মার্ত ধর্ম প্রচার করে সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য এলাকায় এই ভূমিদান কম। সম্ভবত একটিঃ নৈহাটি (রমাকান্ত চক্রবর্তী। বাঙালির ধর্ম,সমাজ ও সংস্কৃতি)। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় এতদঅঞ্চলে বৌদ্ধদের শক্ত ভিত্তির কথা। এমনকি যে গ্রাম নাম এই আলোচনার ভিত্তি তার পাশের গ্রাম শিমুলিয়া (প্রাচীন নাম সোমালি) নাম সহ অন্যান্য যে দুয়েকটি গ্রাম নাম মেলে নৈহাটি ফলকে সে গ্রামগুলিতে গাজন নামমাত্র।
আর আলোচ্য গ্রামটিতে আজও পৌরাণিক দেব দেবীর মূর্তি পুজোর চলন নেই। (একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের দুটি জগদ্ধাত্রী পুজো ও সার্বজনীন দূর্গাপুজো হাল আমলের।)
এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বাঙলার ধর্মীয় সংস্কৃতি দেখব। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙলার তন্ত্র” নামক গ্রন্থানুসরণে বলি, প্রাচীন বৌদ্ধ শূন্যবাদে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। মহাযানী একটি তন্ত্রধারা জীবদেহ বিচ্ছিন্ন আত্মাকেই উপাস্য করে তোলে। এখানে নেই শক্তির অন্বেষণ, যা জীবদেহ সঞ্জীবিত করে অথবা ভাবের বিকাশ ঘটায়। একটি পর্বে এসে, এই মহাযানী বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শাক্ত উপাসকদের আপোস ঘটে। স্মর্তব্য যে, শক্তিধর্ম মহাযানী তন্ত্র অপেক্ষা বহু প্রাচীন, অনার্য সভ্যতাভুক্ত এবং সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক। বলাবাহুল্য, তন্ত্র ধর্মই যেহেতু বাঙালী ও বাঙলার প্রাচীন ধর্ম (অতুল সুরঃ বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন), তাই আমাদের পূর্ব পরিচয়ের সূত্র অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় গাজনের উপর আলোকপাত। এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ না তুললেই নয়, তা হলো, বৌদ্ধ মহাযানী তন্ত্রের ‘কামবজ্রযান’ নামে পরবর্তীতে একটি শাখার উদ্ভব ঘটে। এই মতবাদ অনুযায়ী জগত ও জীবের সৃষ্টি রহস্যের মূলে কাম এবং এই সৃষ্টির শক্তি সমন্বিত রূপ শিবলিঙ্গ। বাংলায় এই সম্প্রদায়ের এক সময় প্রবল প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধদের পতনের যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারী মনুবাদী হিন্দু ধর্ম এদের এই কাম কলার সর্বাত্মক বিরোধিতা শুরু করে। আমরা বিরুপাক্ষ নামক এক হিন্দু তান্ত্রিকের কাহিনী জানি, যিনি এই কামবজ্রযান উপাসক সম্প্রদায়কে বাঙলা থেকে নির্মূল করেন। অর্থাৎ আক্রমণ স্মৃতি, সংহিতা শাসিত সমাজের উচ্চবর্ণের। নৃতাত্ত্বিক অতুল সুরের মতে, গাজন প্রাক আর্য উৎসব। আর লিঙ্গ পুজো তো সর্বাধিক প্রচলিত ছিল তৎকালীন বাঙলায়। বিবর্তনের ধারায় এতে প্রথমে দ্রাবিড়ীয়, পরে আলপীয় সভ্যতার ছোঁয়া লাগে। অতঃপর গ্রাম নামটি লক্ষ্য করুন – প্রথমে ‘দত্ত’ অব্রাহ্মন উপাধি, মধ্যে বরু সংস্কৃত বড়ু জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শেষে টিয়া। অভিমত, শুক পাখি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দ্যোতক। তাই?!!! পর পর দুটি বর্ণে র উল্লেখ থাকলেও শেষেরটি উধাও! যারা উপরোক্ত দুই বর্ণে র থেকে তফাত রেখে বাস করতে বাধ্য হতো। কোথায় যেন চর্যার ছায়া নিহিত!
শূদ্রের অবস্থানঃ ধর্মশাস্ত্রের যুগ থেকেই বিশেষত মনু সংহিতায় শূদ্রদের চূড়ান্ত অধঃপতিত অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বদরায়নের ‘বেদান্ত সূত্রে’ ‘শূদ্র’ শব্দার্থে ‘শুক’ অর্থাৎ শোক, ‘দ্রু’ ধাতুজ অর্থ ধাবন করা। পুরানেও ‘শুক্’ বা ‘শুচ্’ ধাতুজ অর্থে সন্তপ্ত বোঝানো হয়েছে। মনু সংহিতায় মনুষ্যেতর প্রানী রূপে বর্নিত, একপ্রকার ঊনমানব – এই অন্ত্যজদের সামাজিক আচার আচরণে অংশ নেওয়া তো দূরে থাক, শ্রাদ্ধ দর্শন ও উচ্ছিষ্ট ভোজন ও নিষিদ্ধ ছিল। এদের কোন ধর্ম নেই, থাকতে পারে না। ব্রাহ্মণের উপদেশ পাওয়া, এক বৃক্ষের ছায়া তলে থাকার যোগ্যতা যাদের নেই, তারা ‘পতিত’ – “ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চন্ডালৈর্ন পুক্কুসৈঃ। ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ।।” (মনুসংহিতা এবং শূদ্র-কঙ্কর সিংহ)। আলোচ্য সময়ে জন বিন্যাস ও পরিবেশ এই রকমই দেখেছি। মধ্যে ব্রাহ্মণ তাদের ঘিরে সদগোপরা। এদের ঘিরে গ্রামের উপকন্ঠে বাগদি, হাড়ি, মুচি, বায়েন অন্যান্য জল অচল সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্রাত্য জনেদের অবস্থিতি। বসত নেই কামার, কুমোর, ধোপা। আলোচ্য গ্রামটি সহ বহু ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত গ্রামগুলিতে এই গাজনের আসর পরিচর্যার মুখ্য দায়িত্ব এখনো হাড়িরাই পালন করে চলেছেন। সিদ্ধাচার্য হাড়িপার কথা সতত মনে জাগে। এরাই ‘পতিত’ ‘শুক’বা ‘টিয়া’ যা বলবেন।
মন্তব্যঃ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের সূচনা। বাঙালির প্রিয় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের অবদান – একথা সকলেই জানি। কিন্তু আর যে সকল বৌদ্ধ ধর্মানুসারী সংস্কৃতি লড়াই করে আজও টিঁকে আছে, তাদের সর্ম্পকে কতটুকুই বা আগ্রহ আমাদের সুধী মহলে ঝরে পড়েছে? চর্যাপদ এর ক্ষেত্র বিচরণকারী সহজিয়াদের একাংশই গাজনের ঐতিহ্য পালনকারী। কথাপ্রসঙ্গে বলি, গবেষিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর, ‘চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্বে এই সহজিয়া বা সিদ্ধদের আর্বিভাব। এরা অধিকাংশই হীনবৃত্তির তথাকথিত নিচুতলার মানুষ। অতীশ দাশগুপ্তের মতে, সময়টা হিন্দু ধর্মে শ্রৌত পর্যায় সমাপ্ত হয়ে স্মার্ত পর্যায়ের সূচনা, বাঙলার কৃষক সমাজকে জাতপাতের বিভাজনে ভাগ করার আয়োজনকাল।’ সহজিয়া দর্শনের মূল কথা হলো উজান- সাধন।… ভোগবাদী ইন্দ্রিয়নির্ভর গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ নিমজ্জিত, সেই পথের বিপরীতে উজান বেয়ে সাধককে ফিরতে হবে ‘সহজ’ অর্থাৎ সহজাত সত্য স্বরূপে, রূপ থেকে অরূপে।’ এই যে ‘সহজিয়া’ সাধনা, এর উন্মেষ বহু পূর্বে বাঙলার প্রাকার্য লোকায়ত দর্শনে গ্রামীন সমাজের নাথগুরু ও আচার্যদের কায়সাধনার সূত্রে। (বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির জননীঃ সম্প্রীতি)। সহজে সবাই সমান- নেই শূদ্র, নেই ব্রাহ্মণ। রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে, ‘নৃতত্ত্বের বিচারে বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও নমশূদ্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় নি’ (বাঙালির ধর্ম,সমাজ ও সংস্কৃতি)। এই পথের পথিক যারা, তারা মঠ, মন্দির বা সংঘারামে আশ্রয় খোঁজেন নি।
আপন কর্ম বা বৃত্তিতে গভীর অনুরাগে আত্মনিয়োগকারী এই মহাত্মাগণ বৃত্তির উৎকর্ষের মধ্যেই সিদ্ধি অর্জন করতেন। স্বীয়বৃত্তি বা জীবিকাকে হীন না ভাবা – এই যে দর্শন, যাকে সমাজের উপরতলার মানুষের ঘেন্না ও তাচ্ছিল্য জ্ঞান করত -তাকে উচ্চাসন দান, এক পাল্টা মতাদর্শ! এখানে উল্লেখ্য, এই উৎসবে সর্বাধিক স্বতঃফূর্ততা চোখে পড়ে বাগদি, হাড়ি, মুচি, বায়েন, ডোম ও বাউড়িদের মধ্যে। অধিকাংশ সিদ্ধাচার্যগণ এদের বৃত্তিধারী।
ইতিকথাঃ প্রাচীন মায়া সভ্যতার ন্যায় বাঙালির ধর্মীয় জীবন জ্যোতিষ কেন্দ্রিক পঞ্জিকা নির্ভর বৈষয়িক ও ধর্ম জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। রাঢ়ের গাজনের ক্ষেত্রে সেটির বালাই নেই! এর একটিই নিয়ম বিধি – চৈত্র মাস ৩১ দিনে হলে জাগরণ ২৮ তারিখে, অন্যথায় ২৭শে চৈত্র। উত্তর রাঢ়ের বীরভূমের কোল ঘেঁষে, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের একাংশ জুড়ে বৃত্তাকারে বোলান ও পোড়ো বোলানের যে অনুষ্ঠান গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই বিষয়টিতে আজও নাগরিক সমাজ উন্নাসিক। অথচ আমদের সংস্কৃতির শিকড় সন্ধান করতে গেলে যেতেই হবে প্রান্তিক এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে। এবং সেই সংস্কৃতির লোকায়ত ধারা যুগ যুগ ধরে নিজেকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি শত অবহেলাতেও ঐতিহ্যানুসারী। এর কারন এই সংস্কৃতি প্রতিবাদের নীরব উচ্চারণে ঋদ্ধ। অর্থ নয়, প্রচার নয়, ভালোবাসার একটু ছোঁয়া পেলে জাগরণের এই রাত আরো জাগরিত হয়ে উঠবে, বেঁচে উঠবে একটি সুপ্রাচীন ধারা। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর বিখ্যাত “সংস্কৃতির ভাঙা সেতু” প্রবন্ধ গ্রন্থের ভাষ্য তুলে ধরলাম, “ইতিহাসের যতদূর দেখা যায়, বাংলার নিম্নবিত্তের সচ্ছল ছবি পায় না।…. কিন্তু এই দারিদ্র দিয়েই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না। তার জীবনযাপনে মানবিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ আছে এবং হাজার হাজার বছরের শোষন তাঁর সুকুমার বৃত্তিকে উপরে ফেলতে পারেনি। তাই তাঁর যথার্থ পরিচয়লাভের জন্য তাঁর সংস্কৃতিকে জানা একেবারে প্রথম ও প্রধান শর্ত।”
আমরাই তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও যাই, বিভিন্ন লোকায়ত জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান দেখতে। চলুন না, এই শিশির বিন্দুটিকে দর্শন করতে? কে বলতে পারে, এর মধ্যে লুকিয়ে নেই কোন অতীত। আর আমাদের মধ্যেই তো রয়েছে স্বভাব অতিক্রমনের তীব্র আকুতি।
বিশেষ সহায়তাঃ
১) পল্লব সেনগুপ্ত -পূজা পার্বনের উৎস কথা;
২) রমেশ বসু-প্রবন্ধ;
৩) নরোত্তম হালদার-গঙ্গারিডিঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা;
৪) শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া-প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ;
৫) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় – বাঙলার তন্ত্র;
৬) অলকা চট্টোপাধ্যায় – চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী।
*****************************************************

লেখক পরিচিতি – শ্রী অনুপ মুখার্জি
শিক্ষক পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, সাতান্ন বর্ষীয় চিরতরুণ অনুপ বাবুর বিদ্যালয় শিক্ষা দক্ষিণখন্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্নাতক স্তরের পঠন পাঠন বহরমপুর শহরে কৃষ্ণনাথ কলেজে। লোক সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জনজাতির আচার, সংস্কার, জীবনযাত্রার ওপর বিস্তর পড়াশুনো রয়েছে অনুপ বাবুর। সম্পূর্ণ শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার সীমানায় দত্তবরুটিয়া গ্রামে। লেখালেখির পাশাপাশি ভ্রমণ ও ফটোগ্রাফি তাঁর নেশা।

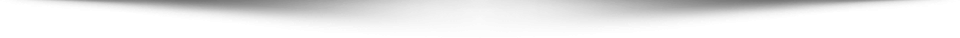
গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির ওপরে দীর্ঘ, সুচিন্তিত, সুলিখিত, বহুলগবেষনামুলক প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগলো। তবে সুরটি বড় ক্ষীণ হয়ে কানে এল, কারণ, বৃহত্তর বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের সুদূর অতীতের সাহিত্য, লোকজীবন তথা লোকসংস্কৃতি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের সংঘাত ও জাতপাতের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং বিস্তির্ণ পড়াশোনা না থাকলে এ ধরনের লেখার মূল সুরটি অনুধাবন করা কঠিন !
কৌতুহল হচ্ছে জানতে, প্রায় চার যুগ আগের, লেখকের কৈশোরের, ওই গাজনের উৎসব কি এখনও তার সেই রূপটিকে ধরে রাখতে পেরেছে ? না কি, আধুনিকতার জোয়ারে, বৈদ্যুতিক সংযোগের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে, রেডিও-টিভি-চলচ্চিত্রের দৌলতে সে হারিয়ে গেছে? থেকে থাকলে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে ! … তবে, আমার মত শহুরে, শৌখিন পর্যটক অবশ্য প্রথমেই শুধাবেন, চত্তিরের শেষে যা গরম, ওখানে থাকার জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত “রিসর্ট” পাব তো ( হাঃ, হাঃ, হাঃ!) !!!!
শেষের বাক্যটিকে গুরুত্ব না দিয়ে, শুধু কৌতূহলটুকু মেটালে, লেখকের কাছে বাধিত হ’ব।
প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই পাঠ প্রতিক্রিয়াজাত নাড়ির টানের আবেগ প্রতি শ্রদ্ধাসহ।হ্যাঁ,এখনো এই অনুষ্ঠান এতদ অঞ্চলজুড়ে হয়ে চলেছে।শুধু বলার জাগরণের রাতটি সর্বত্র একদিনে।অপরাপর অনুষ্ঠানগুলি সেভাবে সব গ্রামে হয়না।খুব ভালো হয় কাটোয়াকে তিনদিন ভিত্তি করে জাগরণের দিন বিকাল ৪টের মধ্যে গাড়ী নিয়ে দত্তবরুটিয়া চলে আসা ভক্তনাচ দেখার জন্য। তারপর সাঁঝ গড়িয়ে পাড়ি দিন বনওয়ারিবাদ /সোনারুন্দি।এভাবে স্থানীয়দের সাহায্য নিয়ে একে একে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বোলান ও পোড়ো বোলান দেখুন। অথবা ভক্তনাচ বাদ দিলে সন্ধ্যার পর কাটোয়া থেকে একইভাবে বেড়িয়ে কেতুগ্রাম, পাচুন্দি, সোনারুন্দি, জলসৌতি, জামলে হয়ে পরদিন দুপুরে উদ্ধারণপুরে পৌঁছান সেখানেই গঙ্গার ঘাটগুলিতে আপন আপন গ্রামের আরাধ্য শিবলিঙ্গ নিয়ে উভয় ভক্তবৃন্দ স্নান করে সন্ধ্যার মুখে পাখিদের সনে কুলায় ফেরে।আধুনিকতারর ছোঁয়ায় বোলানের দল হেঁটে নয়,চারচাকায় গেয়ে বেড়ায় গাঁয়ে,গাঁয়ে।সঙ্গে একালের বাজনাও থাকে।তবে পোড়ো বোলান রীতিতে মোটামুটি একই আছে।
এই গ্রামগুলিতে থাকার সমস্যা সত্যই আছে।আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখিত গ্রাম বা তৎসন্নিহিত এলাকার কাছাকাছি থাকতে গেলে সেরা স্থান সালার।এখন ওখানে দু তিনটি লজ হয়েছে।স্টেশনে সব এক্সপ্রেস দাঁড়ায়। গাড়ীর ও ব্যবস্থা আছে।
ভুলে গেছি বলতে, আবহমানকালের মধ্যে এই প্রথম করোনার প্রকোপে গতবছর রাঢ়ের গাজন বন্ধ ছিল।
আমার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুন্দর প্রতিমন্তব্যের জন্য লেখক শ্রী অনুপ মুখার্জ্জীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।… বয়েস থেমে থাকছে না। আগামী ৬/৭ মাসেও করোনা দেবী লীলা সাঙ্গ করবেন কিনা বলা দুষ্কর! তারও পরের বছর যাবার অবস্থায় থাকবো কি না, তাও জানি না। দেখা যাক। চমৎকার রচনাটির জন্য আবারও ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই শ্রী মুখার্জ্জীকে !!
লেখকের পদবির বানান নিয়ে আমি একটু বিভ্রান্ত। নিবন্ধের সঙ্গে রয়েছে “মুখার্জি” । লেখক পরিচিতি তে লেখা ” মুখার্জ্জী ” ! আমি দ্বিতীয়টিই লিখেছি । দুটিই অবশ্য মুখোপাধ্যায় থেকে নেওয়া।