
“সলিলের গানে দুঃখ-বিরহ”
পল্লব চট্টোপাধ্যায়
সলিল চৌধুরি এ দেশের সংগীতজগতে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর গানের বিশেষত্ব নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন বহু গুণীজন। আমার আজকের আলোচনা সলিলের গানের গতিময়তা নিয়ে। গতিময়তা বলতে এক্ষেত্রে ভাষা, সুর বা লয়ের লঘুতার কথা বলছি না, সলিল গীত-সংগীতের প্রতিটা বিভাগে রেখেছেন নিজস্বতার স্বাক্ষর। জীবন যে চলার নাম, তা কখনও থেমে থাকে না, দুঃখ-মৃত্যু-বিরহ আসে দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই এই জিনিষ কথায় আর সুরে বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুল, দ্বিজেন, রজনীকান্ত আর নজরুল। এবার সুর-ছন্দ-লয়ের বৈচিত্র্য আর যন্ত্রানুষঙ্গের দ্বারা এক নতুন সুষম আঙ্গিক যোগ করলেন সলিল চৌধুরি। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য সলিলের একটি জনপ্রিয় গান। প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে আরো নানান কথা,‘সলিল-সমাধি’ ঘটেছে এমন কিছু গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার সংযোজন।
ভূমিকা
আমাদের দেশের সংগীতে গানের কথা বা বিষয় অনুসারে গানের স্বভাব, গতি আর মেজাজ নির্ভর করে, তার হিসেবমত রাগ, তাল আর লয় নির্ধারিত হয়। প্রাক্-রবীন্দ্র বা রবীন্দ্রোত্তর যুগেও এর খুব একটা অন্যথা হয় নি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এ ব্যাপারে, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন, কখনও বা নজরুল চমক সৃষ্টি করেছেন মাঝে-সাঝে ব্যতিক্রমী সৃষ্টি দিয়ে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে প্রচলিত ধারণা বা প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিই।
হিন্দুস্থানী মার্গসংগীতের এক স্বনামধন্য পণ্ডিত তাঁর কিছু বিদেশী শিষ্যদের নিয়ে ভারতীয় রাগসংগীতের বৈচিত্র্য নিয়ে চর্চা করছেন। তিনি বাদ্যযন্ত্রে ভৈরবীর সুর বাজিয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের কী মনে হল। উত্তর এল- কারো জন্যে সারারাত প্রতীক্ষা করলাম, সে এল না। আশ্চর্য! সুরটা ছিল বিখ্যাত বন্দিশ ‘কা করুঁ সজনি, আয়ে না বালমা’র। তার পরের সুর ভীমপলশ্রী- বিদেশী শিষ্যেরা একবাক্যে বললেন কে যেন দুঃখে-অভিমানে গুমরে কাঁদছে। সুর ছিল-‘যা যারে অপনে মন্দিরবা’। তানসেনের দীপক রাগ গেয়ে আগুন জ্বালানো বা বৈজুর মেঘরাগে বৃষ্টি নামিয়ে নেভানো হয়ত গল্পকথা। তবে শ্রী-রাগে নিবদ্ধ দত্তাত্রেয় পলুস্করের ‘হরি কে চরণ-কমল নিশাদিন সুমরো’ শুনে মনে হত যেন শেষ দিনের ডাক শুনতে পেয়েছেন তিনি, কেমন যেন একটা বিদায়ব্যথা-জড়িত ক্লান্তি তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে। সত্যি অসম্ভব গুণী মানুষটি বড় তাড়াতাড়ি যেন চলে গেলেন সংসারের মায়া ছেড়ে।
সংগীতে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার নিয়ে এরকমই নানা গল্পকথা ছড়িয়ে আছে এ দেশের পথে প্রান্তরে। ওস্তাদ-পণ্ডিতদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা ছিল না সেযুগের সঙ্গীতজ্ঞদের। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পণ্ডিত-ওস্তাদদের হাতে এমনভাবে কুক্ষিগত ছিল যে খেয়াল-ঠুমরি-ধ্রুপদের বন্দিশ বাংলায় লেখার কথাও ভাবা যেত না। চর্যাগীতির আলোচনায় যাচ্ছি না, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শোরী মিঞার দলবলের অনেক বিরোধিতা সহ্য আর উপেক্ষা করে নিধুবাবু লিখলেন বাংলা টপ্পা, রাজা রামমোহন লিখলেন ধ্রুপদ। তারপর কিছুটা হলেও খুলে গেল বাংলা গানে রাগরাগিনীর সার্থক প্রয়োগ, রামপ্রসাদ-মদন-দাশুরায় ভক্তিগীতিতে যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ করলেন বাংলার লোকগীতি, বিদেশী সুর, ভাঙলেন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের যাবতীয় বেড়াজাল।
‘সংগীতচিন্তা’য় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন “আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা থেকে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসৃষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁদ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে। সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে।” আরো বলেছেন, “ক্লাসিক্যাল আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কী গেয়েছেন, জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন? আমরা তো তানসেনের সময়ের লোক নই, আমরা কি জড়পদার্থ? আমাদের কি কিছুমাত্র নূতনত্ব থাকবে না?” এর অর্থ কী? “আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।” আসলে সংগীত বা শিল্পসাহিত্য-ললিতকলা ততদিনই বেঁচে থাকে, যতদিন সে নিজেকে ঘষে মেজে নতুন করে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে পালটে নিতে পারছে। গোলমাল তখনই বাধে যখন এই ঘষামাজার কর্তব্যে নতুন সৃষ্টির আনন্দের চাইতে সে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ব্যাকরণের লঙ্ঘন হল কিনা, সেই তর্কে প্রাজ্ঞ পিতামহ শ্বেত শ্মশ্রু দোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিহাস সাক্ষী, যতবার শিল্পীর প্রতিভার খামতি দেখা দেয়, ততবারই ধ্বংসের ভয়ে ব্যাকরণ টিকিয়ে রাখার ব্রতে মগ্ন হয়ে পড়েন তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা।
একটি জনপ্রিয় গান
কিছু তো বাকি ছিল! রবীন্দ্রোত্তর যুগে নজরুল এনেছিলেন আরবী সুর, বাংলায় লিখেছিলেন গজল, কাওয়ালি, কাজরি, ঠুমরি, দাদরা, শ্যামাসংগীত ইসলামি গান। ভাবের সঙ্গে সুর আর লয়ের সামঞ্জস্য নিয়ে নজরুল কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও চিরাচরিত প্রথা যেন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেললেন সলিল। সুরের বৈচিত্র্য তো বটেই, রাগাশ্রিত গানে বিবাদী সুরের মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার, স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের প্রচলিত শৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে আসা, পলিফোনি, হারমনাইজেশন, পিয়ানোর কর্ডের সাথে সেতারের গতের মেলবন্ধন, এক গানের ইন্টারল্যুডে অন্য গানের সুরের প্রয়োগ- পূর্বসূরীরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও এ সবকিছুর প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন সলিল চৌধুরি। কথা-সুর-লয়-ছন্দের সামঞ্জস্য আর বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেল সলিলের একটি জনপ্রিয় গানের কথা-
“দূর নয় বেশী দূর ওই সাজানো সাজানো বকুল বনের ধারে
ওই বাঁধানো ঘাটের পারে।
যেথা অবহেলা সয়ে সয়ে কিছু ফুল শুকানো শুকানো হয়ে
পড়ে পড়ে আছে তার কিছু দূরে ঘাটের চাতাল ছাড়িয়ে-
সেখানে আমার মাতাল হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে।।
(যাক্, যা গেছে তা যাক্, যাক্, যা গেছে তা যাক্)”
বহুশ্রুত গান, গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। একে হৃদয়, তায় আবার মাতাল- যাক না হারিয়ে, ক্ষতি কী! হৃদয় যথাস্থানে হারানোর চেয়ে আনন্দের ঘটনা আর কী হতে পারে? তবে গীতিকার এখানেই থামেন না, অতএব গায়ককে ঠিক কী হারিয়েছে তার বর্ণনা দিতে হয়।
“শুক-সারীরা সেখানে কূজনে কূজনে দুজনে গাহিয়া যেত
ওই নদীটি বহিয়া যেত।
বনহরিণী চকিত চপল চরণে চমক লাগায়ে দিয়ে
তার চেয়ে ভাল চোখ দুটি দেখে যেখানে যেত সে দাঁড়িয়ে-
সেখানে আমার করুণ হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে।।
(যাক্, যা গেছে তা যাক্…)”
প্রথম চরণের মধ্যমিল আর তার পরে ‘চ’এর অনুপ্রাস চোখে পড়ার মত। কিন্তু তারও চেয়ে ভাল সেই চোখের বিবরণ যেখানে কবির চোখ পড়েছে, কিন্তু আমাদের এখনও পড়েনি। হৃদয় এখানে করুণ, তবু অনায়াসে বলে উঠি, ‘যাক্, যা গেছে তা যাক্’ পরের স্তবকের আশায়।
“মোর মানসী কলস কাঁখেতে লইয়া ওখানে দাঁড়াত এসে,
মুখে মধুর মধুর হেসে।
তার তনুর তীরথে ডুবিয়া মরিতে নদীও উতলা হত
তার ঢেউএ ঢেউয়ে আরো দুটি ঢেউ যেখানে দিত সে বাড়িয়ে-
সেখানে আমার উতল হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে।।
(যাক্, যা গেছে তা যাক্…)”
এতক্ষণে অনঙ্গ যেন অঙ্গধারণ করলেন। ‘তনুর তীরথ’ কথাটা অবশ্য নতুন নয়, নজরুল আগেই লিখে ফেলেছেন- “বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে”। তবে নারীর বক্ষসৌন্দর্য বর্ণনার জন্যে কোনও কুরুচিকর শব্দ বা বিতর্কে না গিয়ে কবি তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আরো দুটি ঢেউ বাড়িয়ে দেওয়ার কথা লিখলেন – এখানে সলিল একজন ওস্তাদ শিল্পী।
“মোর দিবস রজনী হায় গো সজনী ভাবিয়া কাটিয়া যেত,
সবই স্বপ্ন যে মনে হত।
সেই মগন স্বপন সহসা কখন ভাঙিয়া ভাঙিয়া গেল
এই পথ দিয়ে বধূবেশে সেজে যেদিন গেল সে হারিয়ে
সেদিন আমার সজল হৃদয় দুপায়ে গিয়েছে মাড়িয়ে।।
(যাক্, যা গেছে তা যাক্,…)”
এইখানেই আসল ট্রাজেডি। কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের হা-হুতাশের বদলে কবি লিখলেন কি-“যাক্, যা গেছে তা যাক্, যাক্, যা গেছে তা যাক্”। গানটিতে দ্রুতলয়ের সাথে চটুল সুরের ব্যবহার কথার সাথে আপাতদৃষ্টিতে খাপ খায় না, তবে এটাই তো সলিলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত আমরা সঙ্গীতের ভাব, সুর, রাগ, তাল ও লয়ের সমন্বয় নিয়ে যা যা শুনে এসেছি রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত, সবকিছু ধ্যান-ধারণা যেন এক-ঝটকায় বদলে গেল। এটাই সলিল ‘দি অরিজিন্যাল’। সলিল চৌধুরির হাত ধরে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গান যেন সাবালকত্বে পা রাখল।
আলোচনা
বিরহের এই গানটিতে দ্রুতলয়ের সাথে চটুল সুরের ব্যবহার – এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সলিল-বিশেষজ্ঞ তথাগত ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানলাম, শক্তিশালী গীতিকারের (কবি নয়) লেখনীতে সৃষ্ট গানে অনেক সময়েই কথার অতীত কোনো অন্তরাত্মার (spirit) সন্ধান পাওয়া যায়, যা কথাকে অতিক্রম করে যায়। এর সন্ধান পেলে অনেক সময়েই দেখা যায়, তা গানের নিছক কথার অতিরিক্ত কিছু তো বটেই, অনেক সময় গানের কথার আপাত-বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত! সুরকারের প্রতিভা গানের এই অন্তরাত্মাকেই ধরবার চেষ্টা করে – নিছক কথাকে নয়। এক্ষেত্রেও, সুরকার সলিলের অনন্য প্রতিভা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে গীতিকার সলিলের অমর সৃষ্টি এই গানের আসল spirit টিকে – যা কিনা ধরা আছে ওই পাঁচটি শব্দের সমাহারে-“যাক যা গেছে তা যাক!” পুরোনো স্মৃতির অলস রোমান্টিকতা নিয়ে পড়ে থাকা নয়, সামনে দেখো! এই তো ছিল সলিলের জীবনের মূল মন্ত্র। শ্যামল মিত্রেরই গাওয়া সলিলের অপর এক সৃষ্টিতে দেখি,
“স্মৃতি নিয়ে কি হবে আর, মিছে পুতুল খেলার মোর সাধ নাই
মনে রাখো কি না রাখো, মনে মনে ভাবা মোর কাজ নাই.
এ জীবন মোর আঁধারে আঁধারে মিশে আলোয় আলোয় মিলে মিশে থাক।।”
স্মৃতির রোমান্টিকতাকে সার্থক সৃষ্টির প্রেরণায় ব্যবহার কর, কিন্তু সেই স্মৃতিডোর যদি দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করে পেছনে টেনে ধরে, তো তাকে ছিন্ন কর-এই দৃপ্ত পৌরুষই এই গানের, এবং সলিলের অন্যতর বহু গানের, অন্তর্নিহিত সুর, আর সেই সুরই ফুটে উঠেছে “যাক্ যা গেছে তা যাক্ ”এ প্রযুক্ত marching tuneএ। তাই দ্রুতলয় তাঁর মতে ব্যথাময় অতীতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার সুর।
সত্যি এই গানের কথা, ছন্দ, মিল, সুর, লয় আর গায়কী মিলেমিশে অনন্য হয়ে উঠেছিল। ‘সেদিন আমার সজল হৃদয় দুপায়ে গিয়েছে মাড়িয়ে’ কথাগুলি শুনলে মনে হবে যেন বিরহী কবি বা গায়ক সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামছেন আর সমতল পেয়েই যাক্ যা গেছে তা যাক্ নিতান্ত অবজ্ঞাভরে, পাহাড়ি রাস্তার সর্পিল বাঁকগুলো সন্তর্পণে ধাপে ধাপে নেমে এসে সমতল পেয়েই গাড়ি যেমন নিশ্চিন্তে গতি বাড়িয়ে দেয়।
সলিলপ্রেমী বন্ধু ভাস্কর বসুর মতে সলিল চৌধুরি বিরহের গানেও তথাকথিত দুঃখের সুর লাগতে দেন নি। উদাহরণ- “নিশিদিন, নিশিদিন, বাজে স্মরণের দিন” বা “অন্তবিহীন, কাটে না আর যেন বিরহের দিন”। “বৌ কথা কও বলে পাখি আর ডাকিস না” গানেও একটা অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল ঔদাসীন্য কাজ করে। কিম্বা শ্যামলের গাওয়া এই গানটি-
“জীবন বৃন্তের থেকে ঝরে
কত না স্বপ্ন গেছে মরে।
তবুও পথ চলা কবে যে শেষ হবে জানি না”
সেখানে স্মৃতি ভার নয়, অনুপ্রেরণা। “স্মৃতিরা যেন জোনাকির ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি।” ওঁর দর্শনে সম্ভবতঃ দুঃখ পাওয়া মানে হেরে যাওয়া।
কখনও মনে হয় যে এগুলো বুঝি ইচ্ছে করেই করা। সন্দেহ জাগে বিদেশী সুরের আর বাজনার জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার প্রবল আকর্ষণ থেকে সলিল হয়ত বেরোতে পারেন নি। এই গানগুলো গাওয়ার সময় গায়ক-গায়িকার গলায় সামান্যতম দুঃখের পরশ পাই না, যেন বিরহ কত আনন্দের বস্তু!
ভাস্করের কিন্তু অন্য মত। তাঁর মতে বিরহ প্রেমেরই এমন একটা দিক যেটা ছাড়া প্রেমকে ভাবা যায়না। কালিদাসের মেঘদূতের থেকেই হয়ত পরবর্তী কবিরা বিরহের সৃজনশীলতা কে স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ‘নিদ নাহি আঁখিপাতে’- কথাটা খুবই দুঃখের কিন্তু গানে সেই দুঃখের প্রকাশ নেই। তেমনই “আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস”- এই বিরহীর কি অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, সুরেও তা চিহ্নিত। এখানেও মনে হতে পারে – প্রেমিক যেন বিরহেরই প্রতীক্ষাতে। এমনকি মৃত্যুকেও সেইভাবে দেখা হয়নি, বরং ভাবা হয়েছে তা জীবনেরই এক রূপ। কর্মযোগীর দুঃখবিলাস সাজেনা– “মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ/ তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই”। সলিলও ঠিক একভাবে বলছেন- “জীবন বৃন্তের থেকে ঝরে, কত যে স্বপ্ন গেছে মরে/ তবু এ পথচলা কবে যে শেষ হবে জানিনা”!
আজ বুঝি যে কথাটা ঠিক। ‘আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের’ গানটির সুর-লয় শুনে খটকা লাগত, বোঝা মুস্কিল ছিল যে ওটা প্রেম নয়, তার মায়াজাল কাটিয়ে ‘এবার ফেরাও মোরে’র আহ্বান। ‘সাত ভাই চম্পা’র prelude শুনলে মনে হয় একটা রূপকথার গল্প শুনতে চলেছি। ‘না, মন লাগে না’ গানে কিছুটা বিরহের অভিব্যক্তি আছে। হেমন্তের গাওয়া ‘রানার’এর কিছু অংশে, ‘গাঁয়ের বধু’ গানের শেষ অংশে ‘আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো ভাঙ্গা কুটিরের সারি’ সুরে ক্লান্তি আর বেদনার ছাপ স্পষ্ট, জানিনা সলিলের অনুপস্থিতিতে এদের রেকর্ডিং হয়েছিল বলেই কিনা! ‘আজ নয় গুনগুন’ এ যেহেতু আহ্বানটি প্রেমিকার তাই তার মধ্যে আর্তিটাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। আবার পরের অংশটিতে শুনি প্রেমিকের জন্যে প্রেরণা- “তুমি হও একজন তাদেরই কাঁধে আজ তার ভার তুলে নাও”- বলা যেতে পারে দু’টি ভাবের সংমিশ্রণ। মোহিনী চৌধুরীর একটি খুব বিখ্যাত গান ছিল পুরুষকন্ঠে-“পৃথিবী আমারে চায়, রেখোনা বেঁধে আমায়, খুলে দাও প্রিয়, খুলে দাও বাহুডোর”- এখানেও সেই একই ভাব। এর সঙ্গে “প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য” বা “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়” এই দুটি ভাবনাকেও মেলানো হয়েছে বলে মনে হয়।
হালকাভাবেই বলি, প্রেমের বন্ধন অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যদি ‘রাহুর প্রেম’এর প্রেমিক বলে-“রোগের মতন বাঁধিব তোমায় দারুণ আলিঙ্গনে”। তখন সেই যন্ত্রণার থেকে ছাড়া পেতে হয়ত প্রেমিকাকেও বলতে হয়- “ওগো প্রিয় মোর, খোল বাহুডোর, পৃথিবী তোমাকে যে চায়”। এটা তেমনই কোন ঘটনা নয় তো!
কৃতজ্ঞতা স্বীকার- ইন্টারনেটের বিভিন্ন আর্কাইভ, তথাগত ভট্টাচার্য, ভাস্কর বসু, পল্লববরণ পাল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অমিতাভ প্রামাণিক ও ফেসবুক সলিল চৌধুরি ফ্যান-ক্লাব গ্রুপ।
**********************************************************
 পল্লব চট্টোপাধ্যায় পরিচিতিঃ
পল্লব চট্টোপাধ্যায় পরিচিতিঃ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় (বি আই টি সিন্দ্রী) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক। কর্মসূত্রে বিভিন্ন দেশের খনিজ তৈলক্ষেত্রে কাটিয়েছেন সারাজীবন, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত। বিহারের, অধুনা ঝাড়খণ্ড, যে অঞ্চলে তিনি মানুষ সেখানে ‘নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধান’ হলেও একসময় বাংলাভাষা শিক্ষা ও চর্চার আবহ ছিল। সেই শিক্ষা থেকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মায় ও বিগত কয়েক বছরে অবসর, জয়ঢাক, ম্যাজিক-ল্যাম্প, ছুটির ঘন্টা, আদরের নৌকা, ঋতবাক ইত্যাদি নেট-পত্রিকা ও যুগ, ট্রৈনিক, বোম্বে-ডাক ইত্যাদি মুদ্রিত পত্রিকায়, ক্যাফে-টেবল প্রকাশিত শরদিন্দু স্মৃতি-সংখ্যায় লিখে আসছেন। তাঁর প্রকাশিতব্য গল্প সংগ্রহ ‘আড্ডা আনলিমিটেড’ ও ‘বরাহ-নন্দন ও অন্যান্য গল্প’- দুটিই এখন যন্ত্রস্থ।)

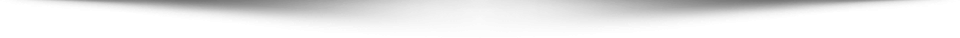
খুব ভালো লাগলো পড়ে।