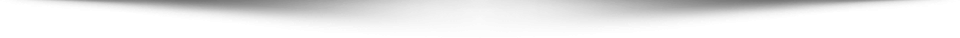বাংলা ও বাঙালির মুড়ি
সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেই ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে হাল আমলের বিশ্বায়নের যুগ অবধি বিদেশি জলখাবারের বাড়বাড়ন্তে চিরাচরিত অনেক বাঙালি জলখাবার হারিয়ে গেছে সত্যি। তবু এখনও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে জলখাবার হিসেবে মুড়ির কদরই আলাদা। এমন নয় যে শুধুমাত্র গ্রাম-মফ:স্বলের লোকজন কিম্বা সস্তায় মেলে বলে গরীব মানুষেরাই মুড়ি খান। অনেক শহুরে অবস্থাপন্ন পরিবারের খাদ্যতালিকাতেও মুড়ি স্বমহিমায় বিরাজিত। তাই তো দেখি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর ‘হাইওয়ে’ কবিতায় লিখেছেন-
“নদী পেরুলে কোলাঘাট,
কোলাঘাট ছাড়ালে দেউলিয়াবাজার।
সেখানে
বাস থেকে নেমে
উইকএন্ডের শৌখিন বাবুরা
গোবিন্দ সামন্তের মালিকের দোকান থেকে
একঠোঙা মুড়ি,
বিটনুন-ছেটানো দু-দুটো আলুর চপ, আর
এক ভাঁড় চা খেয়ে ফের বাসে ওঠে।
তারপর
কেউ ঝাড়গ্রাম, কেউ টাটানগর, কেউ
জুনপুট কি দিঘার দিকে
চলে যায়।”
সঙ্গীতশিল্পী অনুপ ঘোষালের একটি সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় ঘি-চিনি দিয়ে মাখা মুড়ি সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় খাবার ছিল। তাঁর বাবা কবি সুকুমার রায়-ও কি মুড়ি খেতে ভালোবাসতেন? আর তাই কি তাঁর ‘বুড়ীর বাড়ী’ ছড়ার ‘থুর্থুরে বুড়ী’-র ‘গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি’? একই প্রশ্ন মনে জাগে কাজী নজরুল ইসলাম-এর ‘খুকী ও কাঠবেড়ালি’ কবিতায় ‘গুড়-মুড়ি’-র উল্লেখ দেখে। সত্যি কথা বলতে কি শৈশবে এই কবিতা শোনার পর থেকে আমি নিজেও ‘গুড়-মুড়ি’-র ভক্ত হয়ে যাই। এদিকে তখন স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ পড়ছি। তার প্রথম ভাগের পঞ্চম পাঠে কবিগুরু শিখিয়েছেন কত সাদামাটা আয়োজনে চড়ুইভাতি করা যায়। তিনি লিখেছেন – ‘আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশী। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়িভাতি হবে।’ আমরা স্কুলে সহপাঠীরা মিলে প্রায়ই টিফিনবেলায় মুড়ি দিয়ে ‘চড়িভাতি’ করতাম। তবে শুধু নুন নয়। প্রথমে খবরের কাগজ পেতে তার ওপর মুড়ি ঢালা হত। তারপর তার সাথে পরম যত্নে মাখা হত সর্ষের তেল, আলুসেদ্ধ, ছোলাসেদ্ধ, চানাচুর আর কুচোনো শসা-পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা। সবশেষে তাতে একটা বড়সড় পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে বেশ জম্পেশ করে খাওয়া শুরু হতে না হতেই টিফিনশেষের ঘন্টা বেজে যেত। কিন্তু আজও সেই ঝালমুড়ির কথা ভাবলে জিভে জলপ্রপাত নামে। স্কুলজীবনে ঝালমুড়ি খেতাম ছুটির দিনে বাবা-মা-ভাইয়ের সাথে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েও। সেই সময় অর্থাৎ গত শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় আমাদের শহর চন্দননগরের কোথাও ‘ব্র্যান্ডেড’ রেস্তোরাঁ দূরে থাক, সাধারণ রেস্তোরাঁ-ও বিশেষ ছিলনা। দশ পয়সায় প্যাকেট ভর্তি ঝালমুড়ি পেলেই মুখে হাসি ফুটে যেত। সকাল-বিকেলের জলখাবারে আমাদের বাড়িতে চা-মুড়ি, ছাতু-মুড়ি, ঘুঘনি-মুড়ি, দই-মুড়ি ও আম-কলা সহযোগে দুধ-মুড়ি খাওয়ার ব্যাপক চল ছিল। তবে বর্ষার সন্ধ্যায় আম তেল মাখা মুড়ির সাথে মৃত্যুন দা’র দোকানের গরমাগরম ফুলুরি বা পাদ্রীপাড়ার চপ খাওয়া ছিল একেবারে বাধ্যতামূলক। বিজয়া দশমীর সময় অতিথিদের জন্য মা মুড়ির মোয়া বানাতেন। বছরের অন্য দিনে মাকে অনেক সময় মুড়ি-সিঙারা কি মুড়ি-মিষ্টি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করতে দেখেছি। অন্যান্য বাড়িতেও ছবিটা মোটামুটি একইরকম ছিল। আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলে প্রতিবারই তাঁরা আমাদের নারকেল কোরা ও চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়াতেন। এগুলো অবশ্য সবই দোকান থেকে কেনা যন্ত্রে ভাজা মুড়ির কথা। হাতে ভাজা মুড়ি আমাদের জুটত না। ‘সহজ পাঠ’-এর প্রথম ভাগের চতুর্থ পাঠে পড়েছি, ‘ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি / খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি’। আমাদের শহরে এই দৃশ্য দেখার সুযোগ-ও ছিলনা। সুযোগ মিলল মাধ্যমিক পাশ করার পর। আমরা তখন যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সেই বাড়িতে ভাড়া থাকত আর একটি পরিবার। মেদিনীপুর জেলায় ছিল তাঁদের ‘দেশের বাড়ি’। পরিবারটির গৃহকর্ত্রীকে মাসিমা ডাকতাম। প্রথম তাঁকেই দেখি খোলা পেতে মুড়ি ভাজতে। তাঁরা ভুলেও দোকানের মুড়ি খেতেন না। বছরভর ঘরে ভাজা মুড়িই খেতেন। মাসিমার হাতে ভাজা গরম টাটকা মুড়ির স্বাদ পাওয়ার পর থেকে আমারও আর দোকানের মুড়ি মুখে রোচে না। তবে মাসিমাকে দেখে বুঝেছি মুড়ি তৈরি করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং কতখানি দক্ষতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আসলে গ্রামের মেয়ে-বউরা বংশপরম্পরায় এই কঠিন কাজ করার কায়দা-কৌশল রপ্ত করে। প্রসঙ্গত বলি, সব ধানের চালে মুড়ি হয় না। বিশেষ বিশেষ জাতের ধানেই হয়। সেগুলো ‘মুড়ির ধান’ হিসেবে পরিচিত। ‘মৌল ধানের মুড়ি’-র কোনো জুড়ি নেই, প্রচলিত বাংলা ছড়ায় তা পড়েছি। একটা লোকগানে শুনেছি, ‘ও ভাই ঝিঙ্গাশাইলের হুড়ুম ভালা’। বাংলাদেশে মুড়ি-কে ‘হুড়ুম’ বলে। গানের পংক্তিটির অর্থ – ঝিঙেশাল ধানের মুড়ি ভালো। একসময় দুই বাংলাতেই অসংখ্য দেশীয় প্রজাতির মুড়ির ধান পাওয়া যেত। এখন সেসব অনেক ধানই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় কেলাস, ডাহর-নাগরা, নলপাই ও মৌল ধানের চাষ হয়। এগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি মুড়ির উৎপাদন হয়। এছাড়া সুগন্ধী চালের মুড়ি পেতে উত্তরবঙ্গে বিরই, তুলাইপাঞ্জি, কালো নুনিয়া ও নাগেশ্বরী ধানের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে বরিশালের মুড়ির বিশেষ খ্যাতি আছে। বরিশালের অনেক জমিই আধুনিক উচ্চফলনশীল ধান চাষ করার উপযোগী নয়। তাই কতকটা বাধ্য হয়েই সেখানে এখনও অনেক দেশজ ধানের চাষ টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নাখুচি, সাদা মোটা, নারকেল ঝোপা, সাদা পেকরাজ, পারমা, লালগাইচা, করচা মুড়ি, ঘিগজ, দুধরাজ, রঙ্গিখামা, আদুল জরা, লালহাইল, শঙ্করবটি প্রভৃতি ধান থেকে খুব ভালো মুড়ি হয়। তবে মাসিমা কোন ধানের চালে মুড়ি করতেন আজ আর তা মনে নেই। তিনি দেশের বাড়ি থেকে মুড়ির চাল নিয়ে আসতেন। ওনাদের নিজেদের ক্ষেতে মুড়ির ধানের চাষ হত। সেই ধান বিশেষ প্রক্রিয়ায় বার দুয়েক সেদ্ধ করে রোদে শুকোনোর পর ঢেঁকিতে ভেনে চাল তৈরি হত। ঢেঁকি বিলুপ্তপ্রায় বলে এই কাজটা এখন বেশিরভাগ জায়গায় যন্ত্রেই করা হয়। কিন্তু ওনাদের ঢেঁকি ছিল। মুড়ি ভাজার আগে মাসিমা প্রায় দু-তিন কিলো চাল ধুচুনিতে নিয়ে জল দিয়ে ভালোভাবে রগড়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতেন। তারপর সেই চালে আন্দাজমতো নুন মিশিয়ে রোদে রেখে শুকিয়ে ঝরঝরে করে নেওয়ার পর শুরু হত ভাজার পালা। প্রথমে তিনি মাটির উনুনে কাঠের জ্বালে একটা বিরাট কানা উঁচু মাটির পাত্র চাপিয়ে তাতে চালগুলো ঢেলে ‘চাটু’ (একধরনের কাঠের হাতা) দিয়ে অনবরত নাড়তেন। বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার পর মাঝে মাঝে দু’একটা চাল মুখে ফেলে দাঁত দিয়ে ভেঙে পরখ করে দেখতেন ঠিকঠাক ভাজা হল কিনা। মনোমতো ভাজা হওয়ার পর পাত্রটি নামিয়ে রেখে উনুনে ‘খোলা’ (বিশেষ ধরনের মাটির পাত্র) চাপাতেন। এরপর খোলায় কিছুটা বালি গরম করে তাতে একমুঠো ভাজা চাল ফেলে গোছা করে বাঁধা নারকেল পাতার কাঠি দিয়ে একটু নাড়লেই ফটফট শব্দে সেই চাল ফুটে ধবধবে সাদা মুড়ি হয়ে খোলা ভরিয়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গে ওই নারকেলপাতার কাঠির গুচ্ছ দিয়েই তিনি তাঁর হাতের কায়দায় খোলা থেকে সমস্ত মুড়ি টেনে নিয়ে মেঝেতে বিছানো একটা কাপড়ের ওপর ফেলতেন। তাতে কিন্তু বালি একটুও উঠত না। তবুও মুড়ি ভাজা শেষ হলে কাপড়ে জমা হওয়া সব মুড়ি চালুনিতে চেলে মাসিমা টিনে ভরতেন। তবে বাবার মুখে শুনেছি বাংলাদেশে মুড়ি ভাজার পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। সেখানে খোলা থেকে বালিসুদ্ধ মুড়ি একটি মাটির পাত্র বা ‘বালেন’-এর ওপর বসানো ছিদ্রযুক্ত আর একটি মাটির পাত্র বা ‘ঝাঁঝর’-এ ঢেলে মুড়ি থেকে বালিকে আলাদা করা হয়। মুড়িগুলো ঝাঁঝরে থেকে যায়। বালেনে পড়া বালি আবার খোলায় দিয়ে মুড়ি ভাজা চলতে থাকে। বাংলাদেশে এখনও যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান বা পালাপার্বণ উপলক্ষে মুড়ি ভাজা হয়। রমজান মাসে ইফতারির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে হাতে ভাজা মুড়ির চাহিদা বেড়ে যায়। বরিশাল, নাটোর, নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ‘মুড়ির গ্রাম’ বা ‘মুড়ি পল্লী’ নামে প্রসিদ্ধ গ্রামগুলোতে তখন মুড়ি ভাজার ধুম পড়ে যায়। কারখানায় উৎপাদিত মুড়ির চেয়ে হাতে ভাজা মুড়ির বাজারদর তুলনামূলকভাবে বেশি। তবু খেতে সুস্বাদু এবং রাসায়নিক সার ও কেমিক্যাল মুক্ত হওয়ায় অনেক রোজাদার ব্যক্তির কাছেই খাদ্য হিসাবে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। তবে কারখানার প্যাকেটজাত মুড়ি বাজার একরকম দখল করেই ফেলেছে বলা যায়। একসময় দুই বাংলাতেই বহু মহিলা রুটি-রুজির জন্য লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা নিজের বাড়িতেই অন্যের জন্য মুড়ি ভেজে দিয়ে দু’পয়সা রোজগার করতেন। মেদিনীপুরে মাসিমাদের গ্রামে মাঝবয়সী মহিলারা এমনকি বৃদ্ধারাও এই পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। যন্ত্রের দাপটে আজ প্রায় হারিয়েই গেছে সেই জীবিকা। মাসিমার সাথে গল্পে গল্পে আর একটা কথা জেনেছিলাম। মেদিনীপুরের পটুয়ারা নাকি পটচিত্র আঁকতে কালো রঙ সংগ্রহ করেন মুড়ি ভাজার খোলার গায়ে জমা কালি থেকে।
এবার হয়তো কারও কারও মনে একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তা হলে,বাঙালি কবে থেকে মুড়ি খাচ্ছে? এখন এটা সঠিক বলা মুশকিল। অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই বাংলাদেশে ধানকে খাদ্যশস্য হিসেবে উৎপাদন করতে শেখে। তখন থেকেই মৃৎপাত্রে মুড়ি ভেজে খাওয়া শুরু হয়ে থাকতে পারে। কেননা ‘মুড়ি’ শব্দটিই মূলত অস্ট্রিক। অনেকে মনে করেন বৈদিক যুগে দেবতাদের নৈবেদ্যে চালভাজা থাকত। ওই চালভাজাই মুড়ির আদি রূপ। এ প্রসঙ্গে ‘যার নাম চালভাজা তার নাম মুড়ি’ – এই প্রবাদ প্রবচন স্মরণে চলে আসে। কিন্তু খাদ্য হিসেবে স্বনামে মুড়ির উল্লেখ পাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে। ১৬৪৯-১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের ‘মল্লবধ পালা’-য় অনেকগুলো পংক্তিতেই মুড়ির কথা আছে। যেমন – ‘একদন্ডে দশবার চিড়ামুড়ি খায়’, ‘মুড়ি চিড়া সদাই আঁচল ভর্যা দিবে’, পরিপূর্ণ আঁচলে সন্দেশ চিড়া মুড়ি’ ইত্যাদি। ‘জামতি পালা’-য় আছে -‘কর্পূরের আঁচলে সদাই চিড়া মুড়ি’। সেযুগে মুড়ির বিপনন-ও হত। এই পালাতেই পড়ি – ‘মুড়কি সন্দেশ মুড়ি তায় ওষধের গুঁড়ি বার মাস নগরে বিকায়’। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ‘লাউসেনের জন্ম পালা’-য় দোকানির ঘুমোনোর সুযোগ নিয়ে চোরের ‘চিঁড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত’ খাওয়ার সরস বর্ণনা পাই।
বাঙালির মুড়িপ্রীতির কারণে পরবর্তীকালেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই শুধু নয়, লোকগানেও মুড়ি নিয়ে নানা কথার ছড়াছড়ি দেখা যায়। কবিয়াল ভোলা ময়রার রচিত একটি গানে আছে – ‘পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি’। শরৎচন্দ্র পন্ডিত বা দাদাঠাকুরের লেখা একটি গান রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠে জনপ্রিয় হয়েছিল-‘দে মা আমায় রাজা করি/আর কাঙাল হয়ে থাকতে নারি/দন্ত অন্ত হল গো মা/কেমনে চিবোই কলাই মুড়ি।’ রাঢ় বাংলার ভাদু গানে পাই-‘চল চল ভাদু মা মেলায় কিনে দিব রেশমী চুড়ি/আসার পথে খেয়ে আসব লঙ্কা ঘুঘনি মুড়ি।’ টুসু গানেও শুনি -‘আসছে মকর দুদিন সবুর কর/ও তোরা পিঠা মুড়ি জোগাড় কর’। কয়েকটি টুসু গান তো খুব মজার। যেমন-‘আমার টুসু মুড়ি ভাজে,চুড়ি ঝনঝন করে গো/উয়ার টুসু হ্যাংলা মাগি,আঁচল পাইত্যে মাগে গো’ কিম্বা ‘তুদের টুসু মুড়ি ভাজে/খোলা খটখট করে/আরে আমার টুসু মুড়ি ভাজে/বলি,চুড়ি ঝলমল করে গো/ছি ছি! লাজে মরে যাই / টুসু মুড়ি ভাজতে পারে নাই/ছি ছি! লাজে মরে যাই’।
তবে শুধু গানেই নয়,ভাদু ও টুসু পুজোয় ভোগের থালাতেও মুড়ি থাকে। প্রসঙ্গত,পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কোনো বনেদী বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠানে এবং দেব-দেবীর থানে বা মন্দিরেও ভোগ হিসেবে মুড়ি দেওয়া হয়। ছোটোবেলায় আমার মেজ পিসিমাকে দেখেছি কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় নৈবেদ্য হিসাবে মুড়ির মোয়া দিতে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার কাছে রাধানগর গ্রামে রাধা মদন মোহন জিউ মন্দিরে মুড়ির নৈবেদ্য দিয়ে নিত্য পুজোর প্রচলন আছে। বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রামে সেন বাড়ি বা মুন্সি বাড়ির দুশো বছরেরও প্রাচীন দুর্গাপুজোয় মহাষ্টমীর দিন নিম কাঠের দুর্গার ভোগে থাকে হলুদ মুড়ি,আট রকমের কলাইভাজা ও আদা কুচি। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ১ ব্লকের লক্ষ্মীপুরে চৌধুরী পরিবারে কালীপুজোর সময় দেবীকে মুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোলের কাছে শ্যামডিহ গ্রামে ভূতাবুড়ির থানে দেবীকে পুজোর সময় ছোলা,বাদাম ও নানারকম কলাইভাজাসহ মুড়ি নিবেদন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মেড়তলা পঞ্চায়েতের ভট্টাচার্য পরিবারের কালীপুজোয় সর্ষের তেল ও পেঁয়াজ দিয়ে মাখা মুড়ি দেবীকে ভোগ দেওয়া হয়। সাথে পাঁচরকম ভাজা, পুঁইশাক চচ্চড়ির মতো নিরামিষ পদ তো থাকেই। কাঁকড়া ও শোল, বোয়াল ইত্যাদি মাছের পদ-ও থাকে।

PC: ABP Ananda
এগুলো যাঁদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে তাঁরা নিঃসন্দেহে আরও বেশি চমৎকৃত হবেন এটা জানলে যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় গোটা দশেক শতাব্দীপ্রাচীন ‘মুড়ির মেলা’ হয়। হুগলির জিরাট সংলগ্ন মুন্ডুখোলা গ্রামের ধর্মরাজ মন্দির প্রাঙ্গনে মাঘ মাসের অমাবস্যার পরের তিন দিন ধরে মুড়ির মেলা হয়। যা ‘হুড়ুম মেলা’ নামে পরিচিত। এই মেলার বিশেষত্ব হল এখানে শুধু মুড়িই নয়, মুড়ি ভাজার নানান সরঞ্জাম-ও বিক্রি হয়। বাঁকুড়ার জয়পুরের কাছে বৈতল গ্রামে ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ শনিবার ‘মুলো-মুড়ি মেলা’ হয়। সন্তানকামী নারীরা সেই মাসের প্রথম তিনটে শনিবার ধর্মঠাকুরের ব্রত পালনের পর চতুর্থ শনিবার ব্রত উদ্যাপন করে এই মন্দিরে বসেই প্রচলিত নিয়ম মেনে মুলো দিয়ে মুড়ি খান। সেই উপলক্ষেই মেলা হয়। মেলায় মুলো ও মুড়ি বিক্রি হয়। দু’দিন ধরে মেলা চলে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের সর্দারহাটি গ্রামে বনবিবির থানে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বুধবার দেবীর পুজো উপলক্ষে ‘মুড়ির চাকের মেলা’ বসে। সেখানে গুড় ও মুড়ি দিয়ে তৈরি মুড়ির চাক দেদার বিক্রি হয়। তিন দিন ধরে মেলা চলে। মকর সংক্রান্তির পরদিন অর্থাৎ ১ মাঘ মালদার চাঁচলে মহানন্দা নদীর তীরে ‘মুড়ি-আলুরদমের মেলা’ বসে। মেলা চলে পনেরো দিন। তবে মেলার প্রথম দিন মহানন্দার জলে অন্তত তিন ডুব দিয়ে মেলায় বিক্রি হওয়া মুড়ি-আলুরদম খাওয়ার রীতি স্থানীয়ভাবে প্রচলিত। হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের সিংটি গ্রামেও ১ মাঘ ‘মুড়ি-আলুরদমের মেলা’ বসে। এই মেলা ‘ভাই খাঁ পীরের মেলা’ নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির দিন পশ্চিম বর্ধমানে পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন কাঁকসা গ্রামে মুড়ির মেলা হয়। গৈধারা মন্দির ও সংলগ্ন জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই মেলার সূচনা করেছিল গ্রামের রাখালরা। মুড়ি ছাড়াও এই মেলায় গরম গরম তেলেভাজা বিক্রি হয়। পূর্ব বর্ধমানের গলসীর কাছে দামোদর নদের তীরে মকরসংক্রান্তির দিন টুসুর ভাসান উপলক্ষে মুড়ির মেলা বসে। মকর স্নানের পর সবাই দামোদরের ধারে বসেই মেলার দোকান থেকে মুড়ি-তেলেভাজা কিনে খান। বাঁকুড়ার সিমলাপালের পুখুরিয়া গ্রামে লৌকিক দেবী মড়গড়াসিনীর থানে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে চার দিন ধরে মুড়ির মেলা হয়। এই মেলায় দোকানপাট বিশেষ বসে না। প্রতিদিন সকালে নিকটবর্তী গ্রাম ও এলাকার মানুষজন বাড়ি থেকে মুড়ি ও মুড়ি মাখার সামগ্রী নিয়ে এসে এখানে বসে খান। তবে এই সব মেলাকে জনপ্রিয়তায় ছাপিয়ে গেছে প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলা। বাঁকুড়াবাসীর মুখে যা ‘মুড়ি পরব’ নামে পরিচিত। কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদের ধারে অবস্থিত সঞ্জীবনী মাতার আশ্রমমন্দিরে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ মাঘ হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসে। চারদিন ধরে নামগান চলে। শেষ দিন অর্থাৎ ৪ মাঘ সেখানেই দ্বারকেশ্বরের চরে মেলা বসে। বাঁকুড়া ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলা, এমনকি বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশা থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ মেলায় আসেন। পরিবার-পরিজন-বন্ধুবান্ধব মিলে চরের বালিতে গামছা বিছিয়ে তাতে মুড়ি ঢেলে হরেক উপাদেয় উপকরণ সহযোগে চলে খাওয়াদাওয়া। অনেকে আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ে তৈরি করা গর্ত (স্থানীয় ভাষায় ‘চুয়া’)-র জলে মুড়ি ভিজিয়ে খান। কেউ কেউ বাড়ি থেকে পুঁটুলি বেঁধে মুড়ি ও নানা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসেন। কেউ আবার মেলার দোকান থেকে কিনে খান। আশ্রমমন্দিরের পক্ষ থেকে দুপুরে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থাও থাকে। মনে পড়ছে কোনো এক সান্ধ্য আড্ডায় অনেকে মিলে একই পাত্র থেকে মুড়ি খাওয়ার সময় আমার কোনো এক সাথী মন্তব্য করেছিলেন ‘শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমাজে মুড়ি যেন এক সমন্বয়ের প্রতীক’! কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলায় জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আগত অগনিত মানুষের ভিড়ে অন্তত একবার সামিল হতে পারলে অন্তরে এই কথাটির উপলব্ধি হবেই হবে। কামনা একটাই বাঙালি যেন এহেন মুড়িকে বিস্মৃত না হয়।
তথ্যসূত্রঃ
(১) পাগলা ঘন্টি – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; দে’জ পাবলিশিং
(২) সমগ্র শিশুসাহিত্য – সুকুমার রায় ; সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পা.); আনন্দ
(৩) সঞ্চিতা – নজরুল ইসলাম; ডি. এম. লাইব্রেরি
(৪) সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ) – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী
(৫) ধর্মমঙ্গল – রূপরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত; ভারবি
(৬) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল – মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন প্রণীত; শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
(৭) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) – নীহাররঞ্জন রায়; দে’জ পাবলিশিং
(৮) বাংলার কৃষিকাজ ও কৃষিদেবতা – স্বপনকুমার ঠাকুর; খড়ি প্রকাশনী
(৯) Shuvendu, Madhabi & Anup Ghoshal on Foodie Satyajit Ray – youtube.com/watch?v=GgPzHGuUyyc
(১০) ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি
***************************************

সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিতিঃ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘দর্শন’-এ স্নাতকোত্তর সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম আগ্রহের বিষয় লেখালেখি। ‘কালান্তর’, ‘সুস্বাস্থ্য’, ‘উৎস মানুষ’, ‘টপ কোয়ার্ক’, ‘যুক্তিবাদী’, ‘এখন বিসংবাদ’, ‘মানব জমিন’, ‘আবাদভূমি’, ‘সাহিত্য সমাজ’, ‘অভিক্ষেপ’ ইত্যাদি বেশ কিছু পত্রিকা ও সংবাদপত্রে তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত। তাঁর সম্পাদনায় ‘র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন’ প্রকাশন থেকে ড. পবিত্র সরকারের ভূমিকা সহ প্রকাশিত ‘ছোটোদের কুসংস্কার বিরোধী গল্প’-র দুটি খন্ড। তাঁর লেখা ‘ইতিহাসের আলোকে মরণোত্তর দেহদান – আন্দোলন ও উত্তরণ’ বইটি বিশেষভাবে প্রশংসিত। একটি ‘ফেসবুক পেজ’-এ চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী কানন দেবীর জীবনভিত্তিক তাঁর একটি গবেষণামূলক কাজ-ও পাঠকমহলে সমাদৃত। লেখার জগতের বাইরে সংগীতশিল্পী এবং বিজ্ঞান ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত।