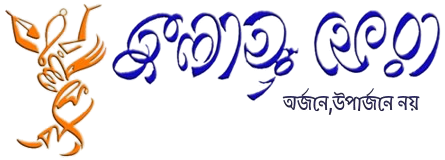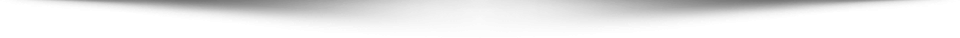গবেষণা
পল্লব চট্টোপাধ্যায়
আরে না না, এটা আমার পি-এইচ-ডির থিসিস নয়। সম্প্রতি এ দেশে গো-জাতি নিয়ে নানাবিধ চর্চা হচ্ছে। গরু আমাদের মাতা এবং গোমাংস ভক্ষণ পাপ হলেও গোমুত্র ইত্যাদি পানে যে সর্বরোগহারিণী সুধা আছে বা গোদুগ্ধে সোনা বা তার কিছু লবণ বর্তমান তাও বিশ্বাস করা হচ্ছে। কোন বিতর্কের মাঝে যাব না, কিন্তু এই দেশে ইদানীং গোভক্তি অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে, নিঃসংশয়ে ভাল কথা, তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকতে গেলে গো-জাতি সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অবশ্য জ্ঞান থাকলেই যে সর্বত্র তার প্রদর্শন করতেই হবে তার কোনও মানে নেই – মাথা তো বাপু একটাই! তাই বলে গরু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভও করতে নেই? ‘গো+এষণা’- সে-ই তো গবেষণা, মানে গরু খোঁজা। অবশ্য রিসার্চের সঙ্গে গরু-খোঁজার কী সম্পর্ক সেটা বলার মত জ্ঞান আমার নেই, আমি বরং যতটুকু জানি, সেটুকুই বলি।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আসি ‘গো’ শব্দটিতে। ‘গো’ সংস্কৃত শব্দ। এটি পুংলিঙ্গ, অর্থ- গরু, পৃথিবী, স্বর্গ। অর্থাৎ গো-মাতা কথাটি সোনার পাথরবাটির মতই অসম্ভব। তবে সংস্কৃতজ্ঞ আর্যজাতির গো-এর স্ত্রী-রূপ গবী বা ধেনুকে মাতা বলা চলে। মূল শব্দটি কিন্তু ‘গো’, যদিও কোন কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ বা ওয়েব-সাইটে প্রায়ই ‘গৌ’ লেখা থাকে। কথাটা আংশিক ঠিক, ‘গো’ শব্দের প্রথমা একবচন আর সম্বোধনে হয় ‘গৌঃ’। তবে জানেন নিশ্চয় যে সন্ধি-সমাস-প্রত্যয় সাধারণতঃ মূল শব্দের সঙ্গে জুড়েই তৈরী হয়, তাই এক্ষেত্রে গো কথাটির ব্যবহার গো-জাতি হিসাবেই হওয়ার কথা।
প্রাচীন ভারতে ষাঁড়ের বেশ একটা মহত্ব ছিল। শিবের বাহন বলে কিনা জানিনা, তবে খালি প্রাচীন ভারত নয়, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়ান সভ্যতাগুলি, যেমন নর্স, আইরিশ ও ইরানীয়ান উপাখ্যানেও পাওয়া যায় গো-জাতির গৌরব গাথা। এদেশের বেদ, প্রাচীন সাহিত্য বা পুরাণেরও আগে ছিল হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আর মহেঞ্জোদারোর সীলে (ছবি দেখুন) ভীমকায় বৃষের ছবি তো বিখ্যাত। তখন ধর্মাধর্ম বলে কিছু ছিলনা, গো-জাতি সিন্ধু-সভ্যতার সময়েই পোষ মানতে শুরু করেছিল। শূকর-ছাগ-ভেড়া-মহিষ-গরু পালন আর চারণ ছিল সে সময়ের দুধ, পশুলোম আর মাংসের উৎস, চাষবাসে গরু বা বলদের ব্যবহারও বোধহয় সেকালেই শুরু হয়। কিন্তু সেসব পদ্ধতি উত্তরকালে আর্যরা তাদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায়নি। তারা নিজেদের মত করেই গো-জাতিকে ব্যবহার করত।
অনেকের ধারণা যে বলদ দিয়ে হলাকর্ষণ-পদ্ধতি আর্যরা এ দেশে নিয়ে আসে। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে আর্যেরা এ দেশে আসে বহুদিন ধরে, তার আগে তারা গবাদি সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে মোটামুটি যাযাবরবৃত্তি করে দিন কাটাচ্ছিল। অনুমান করা যায় যে মধ্যোত্তর এশিয়ার ককেশাস ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে তাদের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার কালে তারা সামান্য কৃষিকাজ জানলেও থিতু হয়ে বসার অব্যবহিত পরে তাদের পক্ষে চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। ফলে গবাদি পশু পশুলোম, দুধ, মাংস আর চামড়ার সরবরাহের কাজেই লাগত। চাষবাস শুরু হলেও লোহার ব্যবহার তখনও ব্যাপক হয়নি বলে কাঠের হল দিয়েই চাষ হত আর এতে বলদের তেমন প্রয়োজন ছিল না। তাই নব্য-আর্য যুগে, ঋক ও সাম বেদে গো-জাতি যজ্ঞাদিতে বলি ছাড়াও সাধারণভাবে খাওয়ার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল একশো চৌষট্টি সূক্তের চল্লিশ নম্বর ঋকে গরুকে ‘অঘ্ন’ অর্থাৎ অবধনীয় বলা হয়েছে। অথচ এই ঋগ্বেদেরই দশম মণ্ডলের ছিয়াশি সূক্তে ইন্দ্র, যিনি ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা, বড়াই করে ইন্দ্রাণীকে বলছেন আমি পনের বা বিশ বৃষের মাংস খেতে পারি। অষ্টম মণ্ডলের একচল্লিশ সূক্তমতে ঋগ্বেদের আর এক মুখ্য দেবতা অগ্নিকে ঘিয়ের সাথে যেসব মাংস আহুতি দেওয়া হতো তার মধ্যে আছে অশ্ব, ঋষভ অর্থাৎ বলদ, উক্ষ্ণ অর্থাৎ ষাঁড়, মেষ এবং ‘ভশা’ মানে বন্ধ্যা বা দুগ্ধবতী নয় এমন গরু। না না, আমি মোটেই এত বিপুল বইপত্র পড়িনি। আমার জ্ঞান সীমিত ভাষাতাত্ত্বিক ডাঃ সুকুমার সেন, বেদজ্ঞা পণ্ডিত সুকুমারী ভট্টাচার্য ও পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত নৃসিংহ ভাদুড়িমশায়ের বিভিন্ন রচনা আর আমেরিকাপ্রবাসী পণ্ডিত-বন্ধু দিলীপ দাসের কিছু লেখা থেকে।
তবে এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা-ধর্ম-সমাজ-অর্থনীতিতে গো-জাতির একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। একটু অনুসন্ধানেই বোঝা যায় যে এ দেশের সনাতন ধর্মে গরু চিরকালই পবিত্র ছিল, তবে অবধ্য বা মাংসভোজন নিষিদ্ধ ছিল না। তাহলে কখন ও কেন এ দেশে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হল?
আমরা স্কুলে গরুর সম্বন্ধে রচনা লেখার শুরুটাই এভাবে করতাম- ‘গরু একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী’। চতুষ্পদ নাহয় বরাবরই ছিল, তবে গৃহপালিতও কি? মানুষ গো-পালন শিখল কবে?
আজ থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগে, সিন্ধু সভ্যতার অনেক অনেক আগে সিন্ধুনদেরই তীরবর্তী মহেন-জো-দারো থেকে কয়েকশো মাইল পশ্চিমে বালুচিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর মাঝে বোলান গিরিবর্ত্মের তরাই অঞ্চলে শুরু হয় মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন ধারা, মেহরগড় সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রায় ছয়টি ক্রমপর্যায় আছে। খ্রীঃপূঃ ৬৫০০ থেকে শুরু হয়ে খ্রীঃপূঃ ৩০০০ নাগাদ এই সভ্যতা বিলীন হবার আগেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে সিন্ধুসভ্যতার উত্থান হয়। তারই মাঝে কোনও একসময় মানুষ গোপালন ও চাষবাস শুরু করে। মেহেরগড়ের গোড়াতে ছিল নিওলিথিক বা নব্য-প্রস্তর যুগ। তারপর আসে চ্যাল্কোলিথিক বা তাম্র-প্রস্তর যুগ। তখনও চাষের কাজে কাঠ বা কাঠের মাঝে পাথরের ফলা বসানো হল দিয়ে জমি কর্ষণ করা হত। এতে বলদের কোনও ভূমিকা ছিল না। তাই গরু-বলদের ব্যবহার বলতে দুধ, চামড়া, মাংস- এই শুধু ছিল। চাকা আবিষ্কারের আগে বলদের ব্যবহার প্রায় ছিল না বললেই চলে। আদি সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, কিন্তু তা সীমিত ছিল অস্ত্রশস্ত্র, গয়না আর বাসনের জন্যে। এর পর খ্রীঃপূঃ ২০০০ নাগাদ আর্যেরা ভারতে আসতে শুরু করে। মতান্তরে তারা এদেশেরই মূল বাসিন্দা- তবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর নগরভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক আর্য-সভ্যতাকে বিবর্তনের দিক থেকে মেলানো বড়ই কঠিন কাজ। আন্দাজ করা যায় যে তারা এদেশে আসার প্রায় ২০০-৩০০ বছর পরে বেদ রচনা শুরু হয়। আদি বেদ ঋকের সময় পর্যন্ত গো-ধন পর্যাপ্ত ছিল, তাই গো-হত্যা আর গোমাংস খাওয়াতেও তেমন নিষেধ ছিল না। দুগ্ধদায়িনী বলে গাভী-হত্যায় নিষেধাজ্ঞা হয় (বলদ দ্বারা চাষের কাজ শুরু হবার পর আর্থ-সামাজিক কারণেই গোমাংস-ভক্ষণ কমে আসে), তবে তা কার্যকরী করার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। যজ্ঞে-উৎসবে এন্তার গরু খাওয়া হত।
মনে করে দেখুন রামায়ণে মিথিলাধিপতি জনক নিজের হাতে হলকর্ষণ করার সময় সীতাকে খুঁজে পান (হলকর্ষণের সময় হলাগ্রে মাটির খাঁজে যে অগভীর রেখা তৈরি হয় তাকেই বলা হয় ‘সীতা’)। তার মানে তখনও হলকর্ষণে বলদের ব্যবহার হয়ত ছিল না। অথচ লৌহযুগ তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে, চাকাও আবিষ্কৃত। আরো পরে বৃষ্ণিবংশীয় যাদবরা লোহার লাঙ্গলে বলদ দিয়ে চাষের প্রবর্তন করেন, সম্ভবতঃ তার উদ্ভাবক ছিলেন রোহিনী-পুত্র বলরাম, যাঁকে হলধরও বলা হয় এই কারণে, হয়ত যাদবদের মধ্যে গোপালন-প্রথারও তা মূল কারণ। ইতিহাস বা বেদ-পুরাণকে মাথায় রেখেই বলি, এই সময় গো-জাতির ব্যবহার হঠাৎ করে এত বেড়ে যায় যে অথর্ব্ববেদের সময়ে রাজা আর ঋষিরা মিলে যজন-হবনের প্রয়োজন ছাড়া গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। হয়ত এই নিষেধাজ্ঞা আরও পরে বলবৎ হয়, আর পরে বেদে সংযোজিত হয়, কারণ বলদেবের জীবন আর অথর্ববেদ রচনার কাল সম্বন্ধে সংশয় আছে।
তবে সার কথা হল যে গো-হত্যা বা গো-মাংস খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ধার্মিক নয়, সম্পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক আর জৈব-প্রয়োজনের কারণে প্রবর্তিত হয়। এর সঙ্গে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। তবে ধর্মের উপর মানুষের আস্থা বা ভক্তির চেয়েও ভয়ের কারণেই বেশি হয়ত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে এই জন্মের কর্মের সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই জুড়ে দেওয়া হয় চিরকাল। তাই নিষেধাজ্ঞা রাজদণ্ডের চেয়ে ধর্মের অনুশাসনের নামে হলে চিরকালই বেশি কার্যকরী হয়, এ ব্যাপারে সংশয় নেই। অবশ্য এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যও আছে। গো-মহিষ-শূকরাদির মাংস দাঁতে ছেঁড়ার বিশেষ শ্বদন্ত মানুষের নেই আর তা হজম করতে মানুষের পাকযন্ত্র ও যকৃৎও সে ভাবে তৈরি নয়, তাই এধরণের মাংস হয় সুপক্ক করে খেতে হয় বা যথেষ্ট পরিশ্রমী মানুষই তা ঠিকভাবে হজম করতে পারে। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসকেরা গো-মাংসকে ‘রেড মীট’ বলে অভিহিত করেন যার মধ্যস্থিত লিপিডোপ্রোটিন বা কোলেস্টেরল নামক পদার্থটি চর্বিরূপে দেহের খাঁজে খাঁজে জমা হয় ও রক্তের সঙ্গে মিশে ধমনীতে রক্ত-চলাচল ব্যাহত করে। তাই মধ্যবয়সের পর গো-শূকরাদি জন্তুর মাংসভোজনে সংযত হওয়াই বিধেয়- এর মধ্যে মানবসৃষ্ট ধর্মের কোনও স্থান নেই।
যাক, অনেক ইতিহাসচর্চা হল, এবার হোক কিঞ্চিৎ ভাষাতাত্বিক গবেষণা। গোজাতির সঙ্গে জড়িত কয়েকটি তৎসম/তদ্ভব বাংলা শব্দ প্রসঙ্গে আসি।
গরু (Cow)– সাধারণ অর্থে গো-জাতি। সং ‘গৌঃ’ থেকে এসেছে।
গাই, গাভী (Cow/she cow)– স্ত্রী-জাতীয় গরু। সংস্কৃত ‘গবী’ থেকে এসেছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে গাভী- গাভীন বা গর্ভিনী গাইরূপে কাব্যে এসেছে- উদাহরণ-
“বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস,
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।” (শক্তি চট্টোপাধ্যায়- এখানে গাভী সম্ভবতঃ আসন্নপ্রসবা গাই-এর মতো ধীরগামী জলভারাবনত মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)
ষাঁড় (Ox)– পুরুষ গরু। সংস্কৃত বৃষ, ঋষভ, ষণ্ড, ঊক্ষ্ণ। তবে বলশালী হলেও সহজে পোষ মানে না বলে প্রজনন ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগেনা। তবে স্পেনের ষণ্ড-যুদ্ধে এদের কাজে লাগানো হয়।
বলদ (Bull)– পুরুষ গরু। সং বলীবর্দ থেকে এসেছে। বলের প্রয়োজন এমন কাজে লাগে যেমন- হাল টানা, গাড়ি টানা, ঘানি ঘোরান। ষাঁড়কে কম বয়সে অণ্ডকোষ বাদ দিয়ে নির্বীর্য করে বলদে পরিণত করা হয়। বয়স্ক ষাঁড়ের মাংস বিস্বাদ, তাই মাংসের জন্যেও বলদের চাহিদা বেশি। প্রাচীন ভারতে বেদোত্তর যুগে গোমাংস-ভক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা লাগু হলেও বলদের মাংস ভক্ষণে তেমন নিষেধ ছিল না, যদিও যজ্ঞে আর পুণ্যকাজে বলদ চলে না।
বাছুর (Calf)– গাভীর সন্তান। সং–গোবৎস। পুরুষ হলে বলা হয় এঁড়ে (অণ্ডকোষী বৎসতর) আর নারী হলে বকনা (সং- বষ্কয়ণী বা বৎসতরী)।
গো-প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রয়োজনীয় শব্দ ও শব্দগুচ্ছ- গো নিয়ে যে শব্দগুলো বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত আছে সেগুলোর প্রসঙ্গে আসি।
– গবাদি পশু (Cattle): চাষের বা দুধের প্রয়োজনে লাগে এধরণের গৃহপালিত তৃণভোজী পশুজাতি, যেমন- গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, ইয়াক, দুম্বা ইত্যাদি।
– গোপাল – গোপালক, গোয়ালা, রাখাল, শ্রীকৃষ্ণ, গরুর পাল।
– গোবলয় (Cow-belt): উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত, মুখ্যতঃ হিন্দিভাষী ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গো-জাতিকে মাতা হিসাবে পূজা করা হয় আর হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ, এমন অঞ্চল। এর মধ্যে আসে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র।
– গোষ্ঠ – গবাদি পশুর একটি যূথের মালিক ও তাঁর দলবলের ঠিকানা ও পশুদের বিচরণভূমি। সব মিলিয়ে একটি গোষ্ঠী। একটি পরিবারের বিস্তৃত রূপকেও গোষ্ঠী বলা হয়। একটি গোষ্ঠির মাথা বা মালিককে গোষ্ঠীপতি বা গোপতি নামে অভিহিত করা হত।
– গভিষ্টি, গব্যু বা গবেষণ- গরু নিয়ে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে লড়াই হত তাকে এই নামে জানা যেত।
– গোজাত- সম্মানার্থে কিছু দেবতাকে এই নামে ডাকা হত। বৃহস্পতিকে বলা হয়েছে গোপতি, মরুৎ-কে বলা হয়েছে গোবন্ধু।
– গোসভ- যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ হলো বেদের অংশ যা মূলত যজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করে। এটি বেদের ভাষ্য হিসাবে বিবেচিত এবং প্রতিটি বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রয়েছে) রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞের একটি অংশ, এটি বেদের ব্রাহ্মণদের দ্বারা পালিত গরুকে উৎসর্গ করার আচারকে বোঝায়।
– গোপথ- অথর্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ। এতে ‘সমিতর’ অর্থাৎ যিনি গো-ইত্যাদি পশু বলি দেন, তিনি কিভাবে ছত্রিশ ভাগে পশুটি কাটবেন তার নির্দেশ আছে।
– গোময়-গোচনা- গরুর মল ও মূত্র, হিন্দুশাস্ত্রমতে দুটিই পবিত্র।
– গব্যঘৃত- গরুর দুধের ঘি।
– পঞ্চগব্য- গো-শরীরজাত পাঁচটি বস্তু যা পূজা ও যজ্ঞাদি পবিত্র কাজে ব্যবহার্য – গোময়, গোচনা, গোদুগ্ধ, দধি আর গব্যঘৃত।
– গবেষণা- গো+এষণা= গরু খোঁজা? না, বিশেষভাবে অনুসন্ধান।
– গবাক্ষ- গো+অক্ষ (নিপাতনে)- গরুর চোখ? না, জানালা।
– গোগ্রাস- প্রায়শ্চিত্তের পর গরুর মুখে মন্ত্রপূত ঘাস-দান, আধুনিক প্রয়োগে- বড় বড় গ্রাসে গেলা।
– গোধন- গাভীরূপ সম্পদ। পুরাকালে গবাদি পশুর মালিকের সম্পত্তির হিসেবের মধ্যে গরুর সংখ্যা ধনের তুল্যমূল্য ধরা হত, তা-ই গোধন।
– গোত্র- বংশ, কুল। এর সঙ্গে গরুর যোগাযোগ আছে কিনা জানি না। হয়ত এককালে ছিল। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের পরিচয় তাঁর পূর্বজের গুরু ঋষির নামে হত। অনেকের মতে গোত্র বংশপ্রবর্তক ঋষির সন্তান, ভৃত্য বা অনুগামী পরম্পরা, যেমন ভারদ্বজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ।
– গোত্র- পৃথিবীর শীর্ষ (পর্বত)। গোত্রপ্রধান- হিমালয়। গোত্রভিদ্- পর্বত-ভেদকারী (ইন্দ্র)।
– গোকুল- গো-বংশ, গরুর পাল, বৃন্দাবনের কাছে গোপদের গ্রামবিশেষ, যেখানে গোপালকদের রাজা নন্দ থাকতেন, কৃষ্ণ-বলরাম এখানে পালিত হয়েছিলেন।
– গোক্ষুর- গরুর ক্ষুর, মাথায় গরুর ক্ষুরের চিহ্নধারী (গোখরো) বিষধর সাপ, একধরনের কাঁটাগাছ।
– গোসাপ, গোধা, গোধিকা- গরুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এমন সরীসৃপ প্রাণী।
– গোচর- ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ (গো-সম্পর্কহীন?)
– গোকর্ণ- না গরুর কান নয়। অঙ্গুষ্ঠ থেকে অনামিকা বিস্তার করলে যে মাপটুকু হয় (বিত্তা), জানিনা তা গরুর কানের সমান কিনা! গণ্ডূষ। কর্ণাটকের সাগরতটে এক তীর্থস্থান গোকর্ণ। তবে বলা কঠিন তার নামের উৎপত্তি সরাসরি গরু থেকে না সেখানকার বিখ্যাত ‘ওম বীচ’- যা কিনা ওঙ্কার, মতান্তরে গরুর কানের আকৃতির বলে।
– গোষ্পদ- গরুর পা নয়। গরুর পায়ের ছাপের গর্ত, জল জমে থাকলে পরিণত হয় এক অতিক্ষুদ্র জলাশয়ে।
– গোধুলি- সময়বিশেষ (গরুর পায়ের ধুলো নয়)- সন্ধ্যাকাল, যে সময় গরুর দল চারণভূমি থেকে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে গোঠে বা গোশালায় ফেরে।
– গোমুখ- গরুর মুখের আকৃতির বাদ্যযন্ত্র, জপমালার ঝুলি।
– গোমুখী- গরুর মুখের হাঁ-এর মত গহ্বর যেখা থেকে গঙ্গার মূলধারা প্রবাহিত হয়েছে।
– গোঘ্ন- গোহত্যাকারী।
– গোমুর্খ- গরুর ন্যায় মুর্খ। আমাদের গোমাতাকে আমরা কি তাই মনে করি!
– গোস্তনী- আঙুরের গুচ্ছ (গরুর স্তনের মত একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে ঝুলে থাকার সাথে তুলনীয়)।
– গোলোক- এখানে ‘গো’ স্বর্গ। বিষ্ণুর বাসস্থান।
পরিশেষে বলি, বন্ধুগণ, দয়া করে (রস)’গো’ল্লা, ‘গো’রস্থান বা ‘গো’লাপফুলকে গরুর সঙ্গে জুড়বেন না। যতদূর জানি ‘গৌ’রবের সঙ্গে গরুর হাম্বা-রবের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব গরুর মৃতদেহের কথা ভেবে ‘গো’মড়া হয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই, এখনও এ দেশে হাসির উপর জি-এস-টি বসেনি।
******************************

পল্লব চট্টোপাধ্যায় পরিচিতিঃ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক। কর্মসূত্রে বিভিন্ন দেশের খনিজ তৈলক্ষেত্রে কাটিয়েছেন সারাজীবন,সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত। বিহারের,অধুনা ঝাড়খণ্ড,যে অঞ্চলে তিনি মানুষ সেখানে ‘নানা ভাষা,নানা জাতি,নানা পরিধান’ হলেও একসময় বাংলাভাষা শিক্ষা ও চর্চার আবহ ছিল। সেই শিক্ষা থেকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মায় ও বিগত কয়েক বছরে অবসর,জয়ঢাক,ম্যাজিক-ল্যাম্প,ছুটির ঘন্টা,আদরের নৌকা,ঋতবাক ইত্যাদি নেট-পত্রিকা ও যুগ,ট্রৈনিক,বোম্বে-ডাক ইত্যাদি মুদ্রিত পত্রিকায়,ক্যাফে-টেবল প্রকাশিত শরদিন্দু স্মৃতি-সংখ্যায় লিখে আসছেন। তাঁর প্রকাশিতব্য গল্প সংগ্রহ ‘আড্ডা আনলিমিটেড’ ও ‘বরাহ-নন্দন ও অন্যান্য গল্প’-দুটিই এখন যন্ত্রস্থ।